এমএমআর
জালাল
পর্ব এক :
রবীন্দ্রনাথ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জমিদার পরিবারের সন্তান।
ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথকেও জমিদারগিরি করতে হয়েছিল। এখানে একটি তবে আছে? সেটা হল অধিকাংশ সময়কালটাই বাবার হয়ে--পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের হয়ে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এর জন্য তিনি নিয়মিত বেতন পেয়েছেন।
১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩১ বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের বেতনভোগী হিসাবে জমিদারি দেখেছেন। এই জমিদারির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সর্বমোট ৫০ বছর। তিনি প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন।
এই জমিদারগিরি নিয়েই একটি রবীন্দ্রবিরোধিতা দীর্ঘকাল থেকে নানা কায়দায় চলে আসছে। জমিদাররা যেহেতু শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি--সুতরাং তারা কোনোভাবেই ব্যতিক্রমী হতে পারেন না-- ভাল হতে পারেন না। তারা যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন প্রজানিপীড়ন করে থাকেন। এইরকম একটি সাধারণ সমীকরণ থেকে বলা যেতে পারে, জমিদার রবীন্দ্রনাথও প্রজানিপীড়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই নানাধরনের বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বিরোধিরা তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে বিরোধিতা করে জুঁত করতে পারেনি--তখন তারা চোখ বুজে গৎবাঁধা আওয়াজটি দিয়েছেন--বাবু রবীন্দ্রনাথ প্রজানিপীড়ন করেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের এই প্রজানিপীড়ন বিষয়ে সম্প্রতি একটি ব্লগে নতুন করে অভিযোগ করা হয়েছে। সে কারণে এই সিরিজে অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে--'রবীন্দ্রনাথের জমিদারগিরি—জমিদারের রবীন্দ্রগিরি' কেমন ছিল। বোঝার চেষ্টা করা হবে-- প্রজানিপীড়নের অভিযোগটির ভাঁড়ার ঘরে কি আছে।
ঠাকুরদের জমিদারীর একটু খতিয়ান—
---------------------------------------------------
ডিহি শাহজাদপুর (সদর শাহজাদপুর), বিরাহিমপুর ( যার সদর কাছারি ছিল শিলাইদহে), কালিগ্রাম পরগণা (সদর পতিসর) এবং উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া ও বালিয়া তালুক। এছাড়াও নূরনগর পরগণা, হুগলির মৌজা আয়মা হরিপুর, (মণ্ডলঘাট) পাবনার পত্তনী তালুক তরফ চাপড়ি, রংপুরের স্বরূপপুর, যশোরের মহম্মদশাহী ইত্যাদি এলাকাও। গবেষক অমিতাভ চৌধুরীর তথ্যমতে নদীয়া (কুষ্টিয়া)ও ঠাকুর এস্টেটের অধীনে ছিল। তবে প্রধানত বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, শাহজাদপুর ও ওড়িশার কটকের জমিদারি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারি ঠাকুরদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ অবশ্য জানা যায় না।
কিভাবে জমিদারিটা ঠাকুর পরিবারে পেলেন--নীলমণি থেকে দ্বারকানাথ
--------------------------------------------------------------------------------------
জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুর ছিলেন ব্যবসায়ী। তার পুত্র রামলোচন ঠাকুর বিরাহিমপুর পরগনা (যার সদর কাছারি ছিল শিলাইদহে) জমিদারী কিনেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। জমিদারী কিনে পীরালী ঠাকুরদের মধ্যে তিনি কিছুটা আভিজাত্য অর্জন করেছিলেন।
রামলোচন ঠাকুর মৃত্যুর আগে তার দত্তকপুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৮০৭ সালে এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বছর। তার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পত্তি রামলোচন ঠাকুরের স্ত্রী অলকা দেবী ও দ্বারকানাথের বড় ভাই রাধানাথ দেখাশুনা করতেন। সে সময় শিলাইদহ এলাকাটির সুনাম ছিল না। প্রজারা ‘দুর্বৃত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ’ ছিল। এ জন্য জমিদারী পরিচালনার আইন-কানুন সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার ফার্গুসনের কাছে ভাল করে জেনে নেন।
আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে ১৮১৮ সালে তিনি চব্বিশ পরগনার কালেক্টরের শেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। ১৮২৮ সালে শুল্ক ও আফিং বোর্ডের দেওয়ান হন।
১৮৩০ সালে কালীগ্রাম পরগণা কিনেছিলেন। এ ছাড়া উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া ও বালিয়া তালুক তাঁর ছিল। ১৮৩৩ সালে বিরাহিদপুরের কুমারখালি মৌজায় অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠিটি তিনি কিনে নিলেন। ১৮৩৪ সালে সাহাজাদপুর কেনেন।
সাজাদপুরের জমিদারিটি কিনেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রানী ভবানীর নাটোরের জমিদারির নীলাম থেকে। দাম পড়েছিল ১৩ টাকা ১৩ আনা।
অথ জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাচার
---------------------------------------------
১৮৪৬ সালে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে তাঁদের হাউসের দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা। ৩০ লক্ষ টাকার খবর নাই। ঠাকুর পরিবার গরীব হয়ে গিয়েছিল। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন—যাঁহার পিতার ডিনার তিনশত টাকার কমে হইত না, তিনি চারি আনা মূল্যের ডিনার খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। সেসময় ১৮৫৫ সালে ঋণের দায়ে দেবেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হওয়ার পথে। তিনি সংকল্প করলেন দেনা তিনি শোধ করবেন। দেউলিয়া ঘোষিত হবেন না। ছয়মাসের মধ্যেই অবস্থা সামলে ওঠেন। তাঁদের কোনো ব্যবসা বানিজ্য রইল না। শুধু জমিদারীটি টিকে ছিল। তিনি গরীব হওয়ার কারণে বিষয় সম্পত্তিতে মনোযোগী হলেন।
দ্বারকানাথ তাঁর উইলে তিন ছেলের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দিলেও মৃত্যুর পরে জমিদারি এসে পড়েছে তার বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথের উপর। শিলাইদহে গিয়ে নিজেই জমিদারী পরিচালনা করা শুরু করলেন। গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়েছিল শাহজাদপুর পরগণা।
দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটো দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অংশের জমিদারি পরিচালনাও এক সঙ্গে করতেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করেন। দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে গিরীন্দ্রনাথ ব্যবসা দেখতেন। তিনি ভাল ব্যবসা বুঝতেন। দ্বারকানাথের অধিকাংশ ঋণই গিরীন্দ্রনাথের সুযোগ্য পরিচালনায় ব্যবসার আয় থেকে শোধ করা হয়। গিরীন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সালে মারা যান।
দ্বারকানাথের ছোটো ছেলে নগেন্দ্রনাথ বিলাসী ছিলেন। তিনি সেই পারিবারিক ঋণগ্রস্থ অবস্থায়ও বিপুল পরিমাণ ঋণ করেন। এটা নিয়ে বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিমান করে ছোটো ভাই নগেন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে বহুদূরে চলে যান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। তার কোনো সন্তান ছিল না। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে দ্বারকানাথের এই বিপুল জমিদারি দেবেন্দ্রনাথের একার উপরই পড়ে।
গিরীন্দ্রনাথের দুই ছেলে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান। গণেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসা বিষয়ে তার উপরে নির্ভর করতেন। তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে কলেরা রোগে মারা যান। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে গিরীন্দ্রনাথের ছোটো ছেলে গুণেন্দ্রনাথও মারা যান। গুণেন্দ্রনাথের নাবালক তিন ছেলের গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের জমিদারী অংশও দেবেন্দ্রনাথকে পরিচালনা করতে হয়। তিনি তাঁদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিতেন।
পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে সরাসরি জমিদারি পরিচালনা করা ছেড়ে দেন। ব্রাহ্ম ধর্ম পালন ও প্রচারে সময় ব্যয় করেন। দেবেন্দ্রনাথ জমিদরি ছেড়ে দিলে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এই জমিদারিগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেছেন বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড় জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও মেজো ছেলে অরুনেন্দ্রনাথ, সারদাপ্রসাদের ছেলে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তখন আয়ের উৎস দাঁড়িয়েছিল শুধুমাত্র প্রজাপ্রদত্ত খাজনা ও অন্যান্য আদায়। বাড়ির পুরুষরা প্রায় কেউই জমিদারী পরিচালনায় অংশ নেন না, কালে ভদ্রে মহালে যান। সেখান থেকে অর্থ আসে। তাঁরা ছিলেন জমিতে অনুপস্থিত জমিদার। পরিবারের সদস্যদের অনেকে সে সব অঞ্চল চোখে পর্যন্ত দেখেন নি। তাঁরা বিলাসী জীবন আর নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। তবে দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে জমিদারী দেখতে গেছেন। সমীর সেনগুপ্ত লিখছেন—দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে দার্শনিকতা ও বৈষয়িকতার অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী সহাবস্থান ছিল। সব কিছু থেকে দূরে থেকেও তিনি তাঁর জমিদারী, আদি ব্রাহ্মসমাজ ও পরিবারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন।
রবীন্দ্রনাথের জমিদারির শুরুর আগে--
-----------------------------------------
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে বক্সার থেকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্যভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে উপকার কিছুই হইবে না।
শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগ করেছিলেন জমিদারী পরিদর্শক হিসাবে। সেটা ১৮৮৯ সালের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র বিয়ে করেছেন।
অই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারের দ্বায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন ঘরজামাই। যে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাস থেকে পত্র লিখে তাঁকেই নির্দেশ দিয়েছেন বলে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের রাত্রে ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। আকস্মিকভাবে শিলাইদহে তাঁর মৃত্যু হয়। সংবাদটি এসে জোড়াসাঁকোয় পৌছায় পরের দিন। শোকের আঘাতে সমস্ত আনন্দঅনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।
সারদাপ্রসাদের মৃত্যু, কয়েকমাস পরে কাদম্বরী দেবী ও দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের দেহত্যাগ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী ব্যবসা ইত্যাদিতে শৃঙ্খলায় জমিদারি ও আর্থিক বিলিব্যবস্থার ভার নির্দিষ্ট কারো উপরে দিতে ভরসা পাননি। এর আগে দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম ছেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখতেন। ১২৯১ (১৮৮৪) সাল থেকে জোড়াসাকোর হিসাবপত্র বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখতেন। তিনি এই কাজটি পছন্দ করতেন না। মাত্র দেড় মাস পরে তাই তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
দ্বিপেন্দ্রনাথ ২৩ আগস্ট ১৮৮৪ তারিখ থেকে ঠাকুরপরিবারের জমিদারির হিসেবপত্র পরীক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিপেন্দ্রনাথ পাঁচ বছর এই কাজ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথের ছোটো ছেলে রবীন্দ্রনাথের উপর এই দায়িত্ব এসে বর্তায়। সে সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চার ফাঁকে ফাঁকে কাছারিতে নিয়মিত বসে জমিদারির কাজকর্ম শিখতেন।
২ আষাঢ়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন জোড়াসাকোর কাছারির হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব। ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ তারিখে পেয়েছিলেন জমিদারি পরিদর্শনে অধিকার (নভেম্বর, ১৮৯০)।. এতদিন অবসর মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শন করেছিলেন। (১১ অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার) ২৫, ১৮৮৯ সালে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবী, একজন সহচরী, মেয়ে মাধুরীলতা (বেলা) ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহে যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জমিদারি কাজে কোলকাতায় নহে, শিলাইদহে --
------------------------------------------------------
রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে প্রথমবার গেছেন বাল্যকালে বাবা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ১৮৭৫ সালে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে। তৃতীয়বার গেলেন জমিদারি পরিদর্শনের কাজে। সঙ্গে পরিবার।
তারা তখন শিলাইদহে একটি বোটে থাকা শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে জানাচ্ছেন—শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কোলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদ্য় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।
২৮ নভেম্বর বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃণালিনী দেবী, বেলা, সহচরীসহ চরে বালিহাঁস দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজে ব্যস্ত। তিনি সঙ্গে আসেননি। বলেন্দ্রনাথরা চরে ফেরার পথ খুজে পাচ্ছেন না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় দেখা যাচ্ছে, মৃণালিনী দেবী ভালই হাঁটতে পারছেন। কিন্তু সহচরী অমলা দাশ হাঁটতে পারছেন না। ভয়ে তার গা হিম হয়ে আসছে। মাটি ফুঁড়ে যে কোনো সময় ডাকাতদল বের হয়ে আসতে পারে। শেষে উঁচু জমিতে উঠতে একদল মেছোদের দেখা পেলেন। তারা ফেরার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, সকালে মৌলভী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসেছেন। তারা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের অভাব অভিযোগ প্রার্থনা জানাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ শুনে তার প্রতিকার করছেন।
সে সময় বোট গ্রাম্য গাইয়েদের আগমণ ঘটত। তার মধ্যে দুজন মার্কামারা হয়ে গিয়েছিল। একজন বৈষ্ণব—সে কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান গাইত, আরেকজন সুনা-উল্লাহ। এক-একদিনের পালায় দুআনা করে পয়সা বরাদ্দ ছিল। নিয়মিত বরাদ্দ ছাড়াও মৃণালিনী শাড়ি, সাংসারিক টুকিটাকি ওদেরকে দিতেন। বলেন্দ্রোনাথ এ সময় সুনা-ওল্লাহর মুখ থেকে শোনা ১২টি গান খাতায় লিখে রেখেছেন। এর মধ্যে ২ সংখ্যক গানের রচয়িতা গগণ মণ্ডল। তিনি গগণ হরকরা নামে পরিচিত। গানটির নাম আমি কোথায় পাব তারে। রবীন্দ্রনাথ সেগুলো শুনছেন। তাদের সঙ্গে আসরে বসছেন। পল্লীগানের সংকলন তৈরি হচ্ছে তার নির্দেশনায়।
পরিদর্শক থেকে আমমোক্তার জমিদার রবীন্দ্রনাথ
-----------------------------------------------------------
রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮৯৬ সালে ৮ আগস্ট বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পক্ষে জমিদারি পরিচালনার জন্য পাওয়ার অব এটর্নি করে দেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এই আমমোক্তারনামা দলিলে দেবেন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেন।Tagore Family Papers, Doc. No.68—এর উপরে লেখা আছে—Power of Attorney from Debendranath Tagore to Rabindranath Tagore on 8th August 1896 in the presence of Mohini Mohan Chatterjee, Solicitor, Cal./Presented between the hours 10 to 11 on on the 8th august 1896. এই দলিলের বলে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিচালনা করেছেন। তখনো বেতন পাচ্ছেন।
আমমোক্তারনামা নিয়ে বাবা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিচালনা করেছেন। তারপর নিজে জমিদারির মালিকানা পেয়েছেন ১৯২০ সালের ৮ মে।।
এইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারগিরি শুরু হয়েছে।
পর্ব দুই...
জমিদারির খোঁজে
----------------
কলিমখানের :
জন্মসূত্র--জমিপুত্র--
বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষে
৩৮৯ পৃষ্ঠায় কলিম খান রবি চক্রবর্তী লিখেছেন : জমি--(জমিদার, জমী, জমীন, জমীনদান)
জমি শব্দটি এসেছে জম
থেকে। জম অর্থ—গতিশীল যাহাতে।
জমি—পৃথিবী,
ভূতল, মাটি, কৃষিক্ষেত্র,
চাষের ভূঁই, কাপড়ের পিঠ (Surface)
বা বুননি (Texture), চিত্রপটের তলদেশ (Ground)।
জমিদার—ভূস্বামী,
রাজা। Land—অর্থে জমি এবং Landlord-অর্থে
জমিদার শব্দটি প্রচলিত।
যতদূর বোঝা যায়, ভূতলের অংশ বা
কৃষিক্ষেত্রের লেনদেন শুরু শুরু হওয়ার পরেই জমি ও জায়গা শব্দদুটির সৃষ্টি
হয়েছিল। কারণ, দুটি শব্দের ভিতরেই ‘ই’ বা গতিশীলতা
রয়েছে। জমি-তে ই-কার রয়েছে সরাসির, জায়গাতে ই রয়েছে ‘য়’—এর ভিতরে। কিন্তু কলিম খানের
প্রশ্ন হল—জমিজায়গা গতি পায় কিভাবে?
তিনি বলছেন, জমিজায়গা
হেঁটে-চলে বেড়ায় না। একবস্তা ধান কাউকে দিয়ে দেওয়ার মতো জমিজায়গা কাউকে হাতে
তুলে দেওয়া যায় না, কেউ তা কাঁধে করে স্থানান্তরে নিয়ে
যেতেও পারে না। অথচ একালের মানুষ মাত্রেই জানেন, জমিজায়গা
দিয়ে দেওয়া যায়, দান করা যায়, বিক্রি করা যায় এবং অন্যে তা নিয়েও নিতে পারে। কী করে তা সম্ভব হয়?
কার্যত জমিদান, জমিক্রয়
ইত্যাদি ব্যাপার মানবসভ্যতার একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। বিষয়টিকে বুঝবার জন্য কলিম
খান বলেন, সর্বাগ্রে জানা চাই, ভূতলের কি কোনো অধিকারী বা মালিক হয়? হ্যা,
হয়। ভূতল যাদের অস্তিত্বের ভিত্তি, তেমন
সমস্ত জড় ও জীবই ভূতলের প্রতিটি বিন্দুর অধিকারী। জড় থেকে জীবের
আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্রমান্বয়ে উচ্চতর উত্তরণের সমস্ত ধাপে পেরিয়ে এই ভূতল মানুষের
সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে এই পার্থিব জগৎ হল অস্তিত্বের মাতা, মানুষ হল তার শ্রেষ্ঠ সন্তান; তার সর্বাধিক
আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম বুদ্ধিমান ছেলে; অন্যেরা তুলনায় কম
আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম। যে নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে অন্যের সাহায্যে সাহায্য স্বভাবতই করতে পারে না। মানুষই একমাত্র
পারে এই বিশ্বের সকল জীব ও জড়কে রক্ষা করে সবাইকে নিয়ে চলতে। ফলত, ভূতলকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে তার
সিন্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জন্মে যায়। ফলত, বিশ্বের সমস্ত
মানুষ সমগ্র ভূতলের প্রতিটি বিন্দুর মালিক হয়ে যায়। আর, এই মালিকানার ধারণা চলে আদিম যুগ থেকে মহেঞ্জোদাড়োর যুগ পর্যন্ত। এই
সময় পর্যন্ত ভূতল হাঁটা-চলা করতে পারেনি, গতিশীল হয়নি।
কিন্তু সুবিধাবাদিতার
পাল্লায় পড়ে সেই মানুষ একদিন আত্মকলহে জড়িয়ে পড়ে। পরমাপ্রকৃতি তাকে
সাধারণভাবে ‘শিবতার’ এবং প্রয়োজনে ‘দক্ষতার’ ব্যবহার করবার
যোগ্যতা দিয়েছিল। নিজের নাবালকত্বের কারণে সে অপ্রয়োজনেও দক্ষতার ব্যবহার শুরু
করে দেয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ মানবসমাজে মৌলবিবাদের জন্ম হয়ে যায়। সৃষ্টি হয়
সম্প্রদায় ও সম্প্রদায় পরিচালক মহর্ষিদের বা জ্ঞানীমানুষদের। সেই সম্প্রদায়
সৃষ্টির কালে আদি জ্ঞানীগণকে বা কশ্যপকে পৃথিবী দান করে দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে যায়;
আদিম যৌথসমাজের প্রতিটি মানুষ তাদের তিনটি অধিকার জ্ঞানীগণকে দান
করে দেয়; যার তৃতীয়টি ছিল ভূতলের উপর প্রত্যেক মানূষের
নিজ নিজ অধিকার। ভূতলের অংশ বা জমির হাঁটা-চলার সূত্রপাত হয়ে যায় সেই থেকে। এই
অবস্থাতেই কেটে আরও হাজার বছর।
তারপর একদিন মহর্ষি
(জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, মন্দির-চার্চ-মঠ-মন্দিরের অধিকারী)
তাঁর অধিকারের ভূমির দেখভাল করার জন্য রাজা নিয়োগ করেন, অর্থাৎ
রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। রাজা ও রাজার সাগরেদ রূপে সামন্তগণ জমির দেখভালের
দায়িত্বও পেয়ে যান, কিন্তু তারা তো আর চাষ করেন না।
অতএব তারা সে অধিকার দিয়ে দেন রায়তদের। এরপর এক রাজা আরেক রাজাকে সরিয়ে
ক্ষমতায় বসে, দেখভালের কাঁধবদল হতে থাকে; যদিও গোড়ায় থেকে যায় আদি জ্ঞানজীবী মন্দির-মঠ-চার্চ-মসজিদ এবং শেষ
সীমায় থেকে যায় একই রায়ত। এর মাঝে জমির যে লেনদেন চলতে থাকে, তা কেবলমাত্র দেখভালের-চাষাবাদের অধিকারের লেনদেন।
মুগলদের জমিদারি
বেত্তান্ত---
মুগল আমলে জমিদার বলতে
প্রকৃত চাষির ঊর্ধ্বে সকল খাজনা গ্রাহককে বোঝানো হতো। প্রকৃত চাষি জমিদার নয়, কারণ সে কখনও
তার জমি খাজনা বা ভাড়ায় অন্য কাউকে প্রদান করে না। জমিদাররা শুধু খাজনা আদায়ের
স্বত্বাধিকারী, জমির স্বত্বাধিকারী নয়। পক্ষান্তরে,
জমির মালিকদের বলা হতো রায়ত বা চাষি যাদের নামে জমাবন্দি বা রেন্ট-রোল তৈরি হতো। এই ধারণায়
জমিদারগণ রাজস্বের চাষি ছিল মাত্র। এরা ছিল সরকার এবং হুজুরি(স্বতন্ত্র) তালুকদার ব্যতীত নিম্নস্তরের রাজস্ব চাষিদের মধ্যস্থ পক্ষ। হুজুরি তালুকদারগণ
খালসায় (খাজাঞ্চি খানায়) সরাসরি রাজস্ব প্রদান করত।
জমিদার এই পদবি বা
শব্দটি ভূঁইয়া বা ভূপতি নামে যে দেশীয়
পারিভাষিক শব্দটি প্রচলিত আছে তার সরাসরি প্রতিশব্দ বলা যায়। এই ভূঁইয়া বা ভূপতিরা ছিল ভারতের প্রাক্-মুগল আমলের বংশানুক্রমিক
উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিক। মুগলগণ তৎকালে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে তাদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের
জন্য একটি নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তর করে। অবশ্য চিরাচরিত ক্ষমতা ও উৎপাদনের
উপায়গুলি তেমন বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি।
টোডর মল্লর বন্দোবস্ত
(১৫৮২) যা দূরবর্তী বাংলা সুবায় একদিন জমিদারি পদ্ধতির সূচনা করেছিল, তা ১৬৫৮ সন
পর্যন্ত বজায় থাকে। এই সময়ে বাংলার সুবাহদার শাহ সুজার (১৬৫৭) রাজস্ব বন্দোবস্তের
মাধ্যমে জমিদারি ব্যবস্থায় কিছুটা বল সঞ্চার হয়। এরপর ১৭২২ সনে সুবাহদার মুর্শিদ
কুলির মালজমিনি (ভূমি রাজস্ব) পদ্ধতি প্রচলিত হয়। সরকারি রাজস্ব সর্বাধিক করা ও
রাজস্বের নিয়মিত পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য মুর্শিদ কুলি বাংলা প্রদেশকে
পূর্ববর্তী চৌত্রিশটি সরকারের পরিবর্তে তেরটি চাকলায় (প্রশাসনিক বিভাগ) ভাগ করেন।
আর সেসঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারদের চাকলাদারের এখতিয়ারাধীন করেন। এই
চাকলাদারগণ মনোনীত হন বৃহৎ জমিদারবর্গ থেকে আর তারা জমির মালিক হিসেবে নয়
অধস্তনদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তাদের কাজ ছিল দক্ষতার
সঙ্গে রাজস্বের আদায় ও সংগ্রহ নিশ্চিত করা। তবে প্রধান জমিদারগণকে রাজস্বের
রাজকীয় অংশের জন্য খালসা বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কাছে জবাবদিহি করার ফলে তাদের
সনাতন ক্ষমতা ও মর্যাদাগত অবস্থান আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও প্রতিভাবান জমিদারগণকে
বিভিন্ন সরকারি পদে নিযুক্তির যে প্রস্তাব দেওয়া হয় তার ফলে রাজদরবারে তাদের
অবস্থানগত মর্যাদা বৃদ্ধি ও সেসঙ্গে তাদের নিজ স্বার্থকে আরও এগিয়ে নেবার
সম্ভাবনা অনেক দূর প্রসারিত হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপকের ভূমিকা থেকে জমিদারে
রূপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সম্পূর্ণ হয়।
সময়ের চিত্র : ফ্রম
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শাহজাদা দারাশুকো থেকে---
কোটচাঁদপুর সরকার
যশোহরের একটি মহাল। মোট পরিমাণ ফল ৮৩২০ বিঘা। আকবর বাদশার আমলে স্থির হয়েছিল—লড়াই-হামলার সময়—মহাল কোটচাঁদপুর আগ্রাকে দেবে ২০০
ঘোড়সওয়ার আর ১০১ জন পদাতী। .ঘোড়সওয়ার বা পদাতী দিতে না পারলেও মহান কোটচাঁদপুর
শাহী খাজনা-খানায় পুরো মুল্য ধরে দিত—ফৌজদারের হাদ দিয়ে।
কড়ায়-ক্রান্তিতে। আশরাফিতে—মোহরে।
লেখাটিতে
একজন পথিককে দেখা যাচ্ছে। তিনি পায়ে হেঁটে আসছেন কোটচাঁদপুরের দিকে। হাঁটতে
হাঁটতে এক সময় পথিক দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার পায়ের ফাঁক দিয়ে দুটি বনমোরগ ছুটে
পালাল। দূরে বনশুয়োরের ঘোত ঘোত। পথিক এক একই বলে উঠলেন, আগে
এখানে একটা গাঁ ছিল। এখন নেই। মুছে গেছে। বসতি মুছে যাওয়ার পরে এখানে বোধ হয়
কোনওখানে মানুষজন মানত করতে আসে। তাদের মানত করা মুরগিগুলো এখন বনমোরগ হয়ে ঘুরে
বেড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে বনজঙ্গল বেড়ে যাওয়ায় বনশুয়োর এসে জুটেছে।
পথিক জানেন, কোটচাঁদপুরে
রাত জেগে থাকত। তাঁতীরা খটখট করত। নেই। শুন্য। ভিটেমাটি। জঙ্গল। গ্রামটি মুছে
গিয়েছিল—মগদের লুটপাটের কারণে। পথিকের চার
ভাইপোকে মগরা ধরে নিয়েছিল। আর নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির কিশোরী মেয়েটিকে। এদেরকে
দাস হিসেবে বেঁচে দেওয়া হয়েছে সেসময়ে। সে সময়ের শাসকবর্গ মগ দস্যুদের দমনের
জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রজারা বাঁচল কি মরল এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল
না। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রজাদের কাছ থকে খাজনা আদায় করা।
সে সময় মুর্শিদ কুলি
খাঁ বলছিলেন, বাদশার পাওনা হল-বিঘা পিছু চার মণ গম, চার মণ
যব, আড়াই মণ সরষে, সাড়ে তিনমন
ছোলা বা মটর আর ছমন কলাই। কিন্তু জমিতে যদি পেঁয়াজ, লেবু,
শাকসবজি ফলে—তাহলে নগদ তনখায় খাজনা দিতে হবে।
এছাড়াও নীল, পান, তেতুল, গাজা,
চুবড়া আলু, শাকালু, লাউ, কুমড়ো ফলানের নগদে খাজনা চাই। এসব হিসেব
করার জন্য কানুনগোরা গ্রামে গ্রামে যায়। গরু মোষ রক্ষায় গোসেমারি খাজনা চালু কর
হয়েছিল। ফলবান গাছের উপর খাজনা, সরদবক্তি, শান্তি রাখতে দারোখানা খাজনা, সরাফি, হাসিলবাজার—সব রকম খাজনার পাশাপাশি গাঁজা, কম্বল,
তেল, কাঁচা চামড়ার উপরেও কর বসেছে
প্রয়োজনে।
১৭৫৭ সালে সিরাজউদদৌলা
ইংরেজ বণিকদের হাতে পরাজিত হওয়া পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার এবং
ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করে ১৭৬৫ সালে। এই সময় থেকে আরম্ভ করে কিছুকাল একই সঙ্গে
চলতে থাকে নবাব এবং কোম্পানীর দ্বৈতশাসন।
ইরানী
ভাগ্যান্বেষী রেজা খানকে নবাবের নায়েমে নাজিম করে শাসন ব্যবস্থা চালানো হয়। তাকে
দেশীয় আইন-কানুন ও প্রথা অনুযায়ী দেশ শাসন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।
এই ব্যবস্থাটি ১৭৬৭ সন অবধি ভালভাবেই কার্যকর ছিল। ঐ বছরেই ক্লাইভ এদেশ থেকে চূড়ান্তভাবে
বিদায় নেন। ক্লাইভের সমর্থনে রেজা খান দক্ষতার সাথেই কোম্পানির রাজ্য শাসনে সক্ষম
হন। তবে পৃষ্ঠপোষক ক্লাইভ-এর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রেজা খানকে ফোর্ট উইলিয়ামের উচ্চাভিলাষী
কর্মকর্তাদের চরম বিরোধিতা মোকাবেলা করতে হয়। ফোর্ট উইলিয়ামের এসব কর্মকর্তা
রাতারাতি ধনী হবার বাসনায় রেজা খানের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসে বদ্ধপরিকর হয়ে
ওঠেন। তারা পর্যায়ক্রমে রেজা খানের হাত থেকে প্রশাসন নিজেদের হাতে তুলে নেন।
তাদের এ হস্তক্ষেপের বিষয় প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিভিন্ন জেলায় ইউরোপীয়
তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মাধ্যমে। রেজা খান অভিযোগ করতে থাকেন যে এই নবনিযুক্ত
কর্মকর্তারা পল্লী অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছেন। অভ্যন্তরীণ
ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে কোম্পানি কর্মকর্তারা দেশের পল্লী জনপদগুলিতে লুটপাট
চালাচ্ছে।
এর ফলে রাজস্বের দাবি
রাতারাতি বেড়ে যায়। ১৭৬৪ সালে যেখানে ভূমি রাজস্ব ছিল মাত্র ৮১ লাখ টাকা, সেখানে পরের
বছর তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৪৮ লাখে। আর সাত বছর পরে ১৭৭৩
সালে এই রাজস্ব ধার্য হয় ৩ কোটি টাকা। এই অতিরিক্ত রাজস্বের দাবিতে বাংলার কৃষি
ব্যবস্থা য় রীতিমত বিপর্যয় ঘটে। এ সময় একটি অসাধারণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।
দুর্ভিক্ষটির নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই ছিয়াত্তর বাংলা সন ১১৭৬, ইংএরজি হিসেবে ১৭৭০ সালের প্রথম দিকে। এই দুর্ভিক্ষে চাষীদের অর্ধেকই
মারা গিয়েছিল। আর মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগই প্রাণ হারান। অতিরিক্ত
রাজস্বের দাবিতে জমিদাররা অত্যাচার শুরু করেন। তাতে অতিষ্ট হয়ে অধিকাংশ চাষী
অন্যত্র পালিয়ে যান। বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ফসলি জমি লোকের অভাবে ঝোপ-জঙ্গলময়
হয়ে ওঠে।
১৭৮১
সালের একটি পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, একমাত্র
রংপুরের উর্বর জমি ছেড়ে ৩০ হাজার পরিবার কোচবিচার চলে গিয়েছিল। এভাবে চাষীরা
অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ায় এবং মারা যাওয়ায় জমিও হয়ে পড়েছিল অনাবাদি। ফলে
রাজস্ব আদায়ে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল।
কোম্পানির পরিচালক
সভার নির্দেশের (২৮ই আগস্ট, ১৭৭১) আওতায় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম
কাউন্সিল দেওয়ানি প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিজেকেই সুবা বাংলার জন্য সর্বোচ্চ সরকার
ঘোষণা করে। নায়েব দেওয়ান রেজা খানকে পদচ্যুত করে দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে কারারুদ্ধ করা হয়।
পর্ব তিন.....
বাকী রাখা খাজনা
মোটে ভাল কাজ না।।
( --হীরক রাজার
দেশ/ সত্যজিৎ রায়)
খাজনা আদারের কাছারি:
মুগল বাদশা জমির
মালিক। তার কাছ থেকে কৃষক বা রায়তরা জমির সাময়িক মালিকানা নিয়ে চাষবাস করত। এর
মধ্যে এই প্রজা বা রায়তদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায়ের জন্য মুগল বাদশা
মধ্যবর্তী লোক হিসাবে জমিদার নিয়োগ দিতেন। জমিদার জমির মালিক ছিলেন না। খাজনা
আদায়কারী মাত্র। জমিদাররা খাজনা আদায়ের কাজটি ভালমতো করতে পারলে বাদশার
তরফ থেকে খিলাত বা উপাধী জুটত। এই খিলাত দিয়ে ক্ষুদে জমিদারী থেকে বড়ো জমিদারি
পেতে সুবিধা হত। চোর থেকে ডাকাত হতে কাজে লাগত। তবে কিভাবে—কোন প্রক্রিয়ায় সেই খাজনা আদায় করা হত—সেটা নির্মম কী ভয়ঙ্কর ছিল, তা বিবেচনা করার কোনো দরকার ছিল না বাদশার। এই
তনখা পাওয়াটাই ছিল শাহীর জন্য আল্লার নেয়ামত।
তাহলে খাজনা—দেখি তোমার সাজনা:
জমিদাররা তিন ধরনের
খাজনা আদায় করে বাদশার খালসা বা কোষাগারে জমা দিত।
এক. খাজনা মানে মাল :
আবাদি ফসলী জমি ও
অফসলী জমি যেমন, ফলজ-বনজ গাছপালা, বনজঙ্গল, জলাভূমি ও পুকুর থেকে যে খাজনা আদায় করা হত, তার
নাম ছিল মাল। (এখান থেকেই টাকা পয়সাকে মাল বলা হয়। বলা হয়—মাল-কড়ি কেমন কামাচ্ছেন ভাই?)
দুই. সেইর খাজনা :
নদীপথে যেসব নৌযান
চলাচল করত, যেসব হাঁট-বাজার বসত গ্রামে গঞ্জে তাদের কাছ থেকে সেইর খাজনাটি
আদায় করা হত। এছাড়া যারা বিভিন্ন ধরনের কাজকারবার করত—সেইসব পেশাজীবী বা কর্মজীবীদের কাছ থেকে আদায় করা হত বেশ মোটা
অঙ্কের খাজনা। এটার নামও ছিল সেইর খাজনা।
তিন. বাজে জমা খাজনা :
বিভিন্ন ধরনের জরিমানা, প্রতারণা ও
বিয়েশাদি থেকে এই ধরনের জরিমানা আদায় করা হত।
খাজনা কি করে ধার্য
হত:
এই খাজনা আদায়ের জন্য
জমিজিরেতের সঠিক জরিপ ছিল না। একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে খাজনা ধার্য করা
হত। একে বলা হত আসনাসাক। জমিদারের কাজ ছিল বাদশাহী থেকে ধার্যকৃতএই
খাজনা আদায় করে দেওয়া।
ধার্যকৃত খাজনার টাকা
বিভাজন করে জমিদাররা প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তবে মুগল আমলে জমিদাররা
প্রজারাদের বেশি খেপিয়ে তুলত না। বেশী ঝামেলা সৃষ্টি হলেই বাদশা জমিদার পাল্টে
দিতেন। ফলে জমিদারী টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই প্রজাদের অনুগত রাখার দরকার হত।
জমিদাররা প্রজাদের খুশি রাখতে তাদের কিছু দাবীদাওয়া মেনে নিতেন। তাদের
দেখভালের কিছু কাজ করতেন।
সকলপ্রকার জমিদারদের পুলিশ, বিচার ও
সৈন্যসামন্তর দায়দায়িত্বও বহন করতে হত। জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য পাইক
বরকন্দাজ থাকত। এরা খাজনা আদায়ের কাজে সহযোগিতা করত। আবার স্থানীয় চুরি ডাকাতি
দস্যুদের উৎপাত থামানোর কাজ করত। বড় জমিদারদের আওতায় থানা ছিল। সেখানে নিয়মিত
পুলিশ থাকত। থানা অধিনে একাধিক চৌকি বা পাহারাস্থল ছিল। এদের কর্মীদের নাম ছিল
চৌকিদার। থানার প্রধান ছিল ফৌজদার। ফৌজদাররা বাদশার লোক হলেও তারা জমিদারদের
অধিনেই কাজ করত। এসবই ছিল খাজনা আদায়ের নানাবাহিনী।
মুগলদের নিয়মিত
সেনাবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের জন্য, বিদ্রোহদমনের সময়, বা
পররাজ্য দখলের কাজে বাদশাহীতে সৈন্যসামন্ত, ঘোড়া-হাতি
এগুলোর যোগান দিতে হত জমিদারদের। এই উপলক্ষ্যে প্রজাদের ঘাড়ে বাড়তি কিছু খাজনা
চাপিয়ে দেওয়া হত।
জমিদাররা ছোটোখাটো
বিচারআচারও করতেন। তাদের ছিল জমিদারী আদালত। এই আদালতে যেসব বিচার সম্ভব হত না—তা পাঠিয়ে দেওয়া হত থানাদার বা কাজির কাছে। সাধারণত রায়ত বা
প্রজাদের পক্ষে রায় যাওয়াটা ছিল দৈবদুর্ঘটনা। বাদশার স্বার্থ-জমিদারের
স্বার্থরক্ষা করে যেটুকু বিচার করা সম্ভব—সেখানে তা-ই করা হত।
সে সময়ের লোকছড়ায়
এই খাজনার ভয়াবহতা ধরা পড়েছে--
খোকা ঘুমোলো পাড়া
জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।
ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানীর আমল : পাঁচশালা বন্দোবস্ত—
সে সময়ে কোম্পানী বেশ
খারাপ অবস্থায় পড়ে যায়। তাদের আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এই সমস্যা
মোকাবেলায় কোম্পানী তরফ থেকে ১৭৭২ সালে নিলামের মাধ্যমে জমিদারিগুলো পাঁচবছরের
মেয়াদে ইজারা দেওয়া হয়। এই পাঁচসালা বন্দোবস্ত স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হয় গভর্নর ও কাউন্সিলের চার সদস্যের
নেতৃত্বে এক সার্কিট কমিটিকে। এই কমিটির আরও দায়িত্ব ছিল ইজারাদারদের কাছ
(চাষীদের) থেকে রাজস্ব আদায় করা। দেশীয় জেলা কর্মকর্তা তথা ফৌজদার, কানুনগো আর আমলাদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলো ব্রিটিশ কালেক্টর বা রাজস্ব আদায়কর্তা।
কানুনগোদের কাছে প্রজাদের জমিজিরতের—খাজনাপাতির
হিসেবপত্র-দলিলদস্তাবেজ থাকত। তাদের বাতিল করার ফলে নতুন করে যে যে কোনো হারে
খাজনা বসাতে কোনো অসুবিধে থাকল না।
ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের
দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এরা ‘জেলা কালেক্টর’ হিসেবে অভিহিত হন। জেলা কালেক্টর জমিদারদের কাজনা আদায়েরকাজ
তত্ত্বাবধান করত। কমিটি অব সার্কিট বন্দোবস্তের কাজ ১৭৭২ সালের মধ্যে শেষ করে।
নতুন ইজারাদার বা
জমিদাররা চড়া হারে খাজনা আদায় করতে মনোযোগী হয়। যারা চড়া দামে নিলামে
এইসব ইজারা নিয়েছিলেন,
তারা যে-পরিমাণ রাজস্ব আদায় করবেন বলে আশা করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা করতে পারেননি। ইজারাদাররা কোম্পানীকে নির্দিষ্ট
অঙ্কের খাজনা আদায় করে দিতে পারেনি। তাদের জমিদারি নিলামে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত
স্থাবর অস্থাবর সকল সহায় সম্পত্তিও কেড়ে নেয়। এরপরও এই পুরনো জমিদারদের
কয়েদখানায় ঢোকানো হয়। নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়।
পুরনো জমিদারদের কাছ
থেকে নিলামে জমি কিনে নতুন জমিদার হয়ে বসে নবাবের চাকুরেরা, ব্যবসায়ীরা,
সুদখোর মহাজনেরা-- জমিদারদের দুর্নীতিবাজ নায়েব ধরনের আমলারা।
ফলে তারা খাজনা আদায়ের বেলায় পুরনো জমিদারদের রেকর্ড ভেঙে ফেলে। প্রজাদের
দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। লোকজন জায়গা জমি পালাতে থাকে। সে সময়ে লোকসংখ্যার
তুলনায় অনাবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে বেড়ে যায়। বকেয়া খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়।
আর তারাও কোম্পানীকে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব দিতে না পারলে তাদের ভাগ্যেও
পুরনো জমিদারদের মতো সব হারিয়ে কয়েদখানায় যেতে হত।
এই সমস্যা নিরসনকল্প
কোম্পানী দশশালা বন্দোবস্ত করে।
দশশালা বন্দোবস্ত
জমি নিয়ন্ত্রণের
ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারভিত্তিক জমিদারদের একটা সামাজিক স্বার্থ জড়িত ছিল যা
অস্থায়ী ইজারাদারদের বেলায় ছিল না। তাই ধরে নেওয়া হয় যে, জমিদারদের
তাদের পুরানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিলে ও তালুকের সম্পদ অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য করা হলে
একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় সহজতর হবে অপরদিকে তা কৃষককুলকেও ইজারাদারের অত্যাচার
থেকে রেহাই দেবে। কিন্তু পাঁচসালা বন্দোবস্তের শর্তাবলীর কারণে এক্ষেত্রে সরকারের
হাত বাঁধা ছিল। ১৭৮৯-১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিন জমিদারদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত
করেন। এর ফলে জমিদার ও তালুকদাররাই জমির প্রকৃত
মালিক বলে বিবেচিত হন। তারা সরকারের কোনো অনুমতি ছাড়াই তাঁদের জমি দান বা বিক্রি
করতে সক্ষম বা বন্ধক দিতে পারবেন। এমন কি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন করতে পারবেন।
আর কোম্পানীকে ধার্যকৃত রাজস্ব দিতে না পারলে তাদের জমিদাইর নিলামে দেওয়া হত।
কিন্তু পাঁচশালা বন্দোবস্তের মত তাদেরকে কয়েদ করা হত না।
রাজস্ব শাসনের দক্ষতা
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গোটা দেশকে অনেকগুলি জেলায় বিভক্ত করা হয়। জেলা কালেক্টরকে
জেলার সর্বেসর্বা প্রশাসকে পরিণত করা হয়। কালেক্টরকে সকল নির্বাহী ও বিচারবিভাগীয়
ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রায়ন ও হস্তক্ষেপের প্রতীক রাজস্ব কমিটিকে বিলুপ্ত
করে স্থাপন করা হয় রাজস্ব বোর্ড, যার দায়িত্ব হলো রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়াবলির
সাধারণ বা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ। জমিদারগণকে তাদের জমির ন্যায্য রাজস্ব নির্ধারণের
জন্য এই কালেক্টরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। রাজস্ব বোর্ডও রাষ্ট্রের রাজস্বের জন্য
কালেক্টরের ওপর নির্ভরশীল হয়। ১৭৮৬ সনের সংস্কার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত
প্রশাসনিক বুনিয়াদ রচনা করে। সরকার তখন থেকে আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি
আত্মবিশ্বাস ও দৃঢতার সঙ্গে জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
দশশালা বন্দোবস্তের
সাফল্যের কারণে ১৭৯৩ সালে একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানীকে ধার্যকৃত রাজস্ব প্রদানের পরেও বেশ মোটা
অঙ্কের অর্থ জমিদারদের হাতে রয়ে যেত। তারা প্রজাদের দফায় দফায় খাজনা বাড়িয়ে
দিত। তারা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি, অনাবাদি জমি নতুন করে বন্দোবস্ত দিত প্রজাদের
কাছে। নতুন খাজনা ধার্য করত। এভাবে তাদের আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটা
কোম্পানী এবং জমিদারদের জন্য একটি সুবিধাজনক বন্দোবস্তে পরিণত হয়। আর প্রজারা
নতুন শোষণের জাতাকলে পড়ে।
কেন এই চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত
এ সময় কোম্পানীর
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দরকার ছিল বিপুল
অর্থ। তারা চেয়েছিল ভারতে তাদের ব্যবসাবানিজ্য বিনা মুলধনেই করবে। তারা প্রজাদের
কাছ থেকে অর্থ লুটপাট করে সেই অর্থ দিয়েই ভারতে ব্যবসাবানিজ্য চালাবে। সোজা কথায়
বিনা পূঁজিতে মুনাফা কামানোর ধান্ধা। কিন্তু তাদের নিয়োগকৃত নাইবে নাজিম
রেজাখানের দু:শাসন, দুর্ভিক্ষ, কোম্পানী লোকজনের উশঙ্খল আচরণ
কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের কিছুটা হতাশ করেছিল। যত
তাড়াতাড়ি পারা যায় বিপুল অর্থ কামাইয়ের ইচ্ছে ছিল তাদের। দুর্ভিক্ষের কারণে
বাংলায় তখন এত জনসংখ্যা ছিল না। এই অল্প মানুষকে সহজে সুলভে শোষণ করে খাজনা
আদায়ে জন্যই কোম্পানী জমিদারী প্রথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল।
ইংরেজরা কুটির শিল্প, হস্ত শিল্পকে
শেষ করে দিয়েছিল। তখন কেবল আয় বলতে জমির খাজনাই ছিল প্রধান। জমিদার পাল্টাতো
কিন্তু শোষিত প্রজারা পাল্টাতো না। বাবার বকেয়া খাজনা ছেলের কাঁধে বর্তাতো। ছেলের
বকেয়া তার ছেলের কাধেঁ পড়ত। এভাবে বংশপরম্পরায় বকেয়া খাজনা প্রদানের দায় বহন
করে যেত।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
মানে চিরস্থায়ী প্রজাশোষণ--
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
হওয়ার ফলে প্রজাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে গেল। যো লোকটি জমি চাষ করছে, এতকাল জেনে
এসেছে জমিটি তার—তার ইচ্ছেমত ফসল চাষ করছে, ছেলেপেলেদের
জমি হস্তান্তর করতে পারছে, প্রয়োজনে বিক্রি করতে পারছে,
জমি বন্দক দিয়ে ঋণ নিতে পারছে—এসবই এক খোঁচায় বন্ধ হয়ে গেল চিরস্থাযী বন্দোবস্তের কারণে।
সবকিছু্রই মালিক হয়ে গেল জমিদার। জমিদার খাজনা আদায় ছাড়া আর কোনো বিনিয়োগই
করছে না ফসলী জমিতে—না শ্রম, না পূঁজি—বিনা মূলধনেই কৃষককের ফসলের সিংহভাগই তারা নিয়ে যাচ্ছে। চাষী কোনো
গাছপালা লাগাতে পারে না। কোনো গাছপালা কাটারও ক্ষমতা তার নেই। যেখানে সে
থাকে, সেখানে যেনতেন প্রকারে ঘর বেঁধে থাকবে—কোনো পাকা ঘর তুলতে চাষীরা পারবে না। জমাজুতোও পরতে পারবে না।
মেয়ের বিয়েতে খাজনা দিতে হবে। বাপমা মারা গেলে তার শ্রাদ্ধশান্তিতে খাজনা ছাড়া
করা যাবে না। চাষীর ছেলে হলেও জমিদারকে খাজনা দাও। এমনকি কোনো ঊৎসব-পার্বনও খাজনা
ছাড়া প্রজারা করতে পারবে না। রায়ত বা প্রজারা এক ধরনের শেকলেবন্দী শ্রমিক
জীবনের অধিকারী হল পাঁচশালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে।
এই শেকল আরও শক্ত হয়ে
যেত মহাজনদের ফাঁদে পড়লে। সাধারণত দেশে তখন বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী লেগেই
থাকত। আর এই মেয়ের বিয়ে, বাপের শ্রাদ্ধ আর ছেলের জন্মের কারণে খাজনা
দেওয়ার উপায় থাকত না। ফলে চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হার সুদে ঋণ নিতে
হত। এই ঋণ কখনো ফেরত দেওয়া কখনো ফুরাতো না। বাপের ঋণ শুধতে হত ছেলেকে। ছেলের ঋণ
নাতিকে। এইভাবে মহাজানের ঋণের শেকড় বংশপরম্পরায় বহন করতে হত। আবার চাষী যদি
অক্ষরজ্ঞানহীন মুর্খ কিসিমের হত, তাহলে কায়দা করে একই
ঋণের টাকা পয়সা দুই-তিনবারও আদায় করা হত।
এই মহাজনদের বড় বড়
ব্যবসাপাতিও ছিল। তারা ফসল ওঠার সময়ে জমি থেকেই তাদের ঋণের টাকা আদায় করত। সেই
সময়ে ফসলের বাজার মূল্য কম থাকত। ফলে মহাজনরা কম টাকায় বেশি ফসল পেয়ে যেত।
চাষীরা আরও বেশি ঠকত। কখনো এই সুদের কারবারীরা হত বড় কৃষক। তাদের বলা হত জোতদার।
তারা সব সময়ই হা করে থাকত ক্ষুদে কৃষকের জমিজিরতের গিলে খাওয়ার জন্য।
জমিদাররা খালসা বা রাজ
কোষাগারে আদায়কৃত খাজনার ধার্যকৃত অংশ জমা দেওয়ার পরেও তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ
অর্থ সম্পদ থেকে যেত। এই অর্থ সম্পদ দিয়ে তারা এক ধরনের আয়েসী জীবন যাপন
শুরু করে। তারা তাদের জমিদারিকে ছোটো ছোটো অংশ ভাগ করে পত্তনিদার বা
তালুকদারদের কাছে ইজারা দিতেন। এই পত্তনীদাররা বা তালুকদাররা আসলে জমিদারের আমলা।
জমিদাররা তাদের উপর জমিদারির ভার দিয়ে কোলকাতায় বসবাস করত। তালুকদাররা তখন
প্রজাদের লুটে পুটে খেত। আদায় করত ইচ্ছেমত খাজনা। দখল করত সহায় সম্পত্তি।
প্রজারা এর প্রতিকার কারও কাছে পেত না। আসল জমিদারের কাছে প্রজারা পৌঁছুতেই পারত
না। আর যদি কেউ আদালতে যেত—তাহলে সেখানে উকিল নামের কুমীরের
খপ্পরে পড়ত। এই জমিদারীকাল ছিল প্রজাদের জন্য দোজখ।
পর্ব চার.......
প্যাগোডা ট্রি ওরফে
টাকার গাছের কাহিনী
ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানীর আমলে ইংলণ্ড থেকে যে সব ইংরেজরা ভারতে আসত তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র, ছিচকে,
গুণ্ডা, মারকুটে ছিন্নমূল, আশিক্ষিত, অভদ্র। এদের অনেকের বাপদাদার ঠিক
ঠিকানা ছিল না। এরা কলকাতায় এলে কিছুদিন ঘুরে বেড়াত ফ্যা ফ্যা করে। তারপর জুটে
যেত কোম্পানীর চাকরী। বেতন বার্ষিক মাত্র পাঁচ
পাউন্ড। সবশেষে বার্ষিক চল্লিশ পাউন্ড। এই বেতনে মেসের ভাড়াই হত না। এরা
কোনোক্রমে সই করতে জানত, অথবা সামান্য লেখাপড়া—কিছু সহজ সরল অংক জানত। এরা লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের মালিক হয়েছে কয়েক
বছরের মধ্যেই। এই ধনলাভের কাহিনী বাংলার মানুষকে লুটপাটেরই ইতিহাস। তারা আঙ্গুল
ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। কলাগাছ থেকে বটগাছ। তারপর পুরো বন। ১৭৫৭ সালে
সিরাজউদ্দৌলার পতনের পরে বাংলাকে ইংরেজ বেনিয়ারা প্যাগোডা ট্রি বা টাকার গাছে
পরিণত করেছিল।
এই ইংরেজরা বাংলাকে
শোষণ করে ছিবড়ে করে ফেলে হয়েছিল নবাব। নবাব মানে খুব ধনশালী ব্যক্তি। এরা ভারতে
প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করে ইংলন্ডে ফরে যায়। বিত্তশালী জীবন যাপন করে।
সিরাজউদ্দৌলার পতনের
পরে মীর জাফরের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল বিপুল অঙ্কের টাকা পয়সা এইসব ভাগ্যবান
ইংরেজরা। লর্ড ক্লাইভ ট্রেজারি লুট করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে নিয়েছিলেন দেড়
মিলিয়ন স্টারলিং মূল্যের নগদ টাকা, সোনা, রূপা, গহনাপাতি, এবং বহু মুল্যবান জিনিসপত্রাদি। মীর
জাফরকে নবাব করা হলে তিনি ক্লাইভকে যা খুশি সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।
ক্লাইভ নিয়েছিলেন এক লক্ষ ষাট হাজার পাউন্ড। তিনি অর্ধ মিলিয়ন বিলিয়েছিলেন তার
অধীনস্ত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে। এরা
কোম্পানীর বাহিনী।
আর যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীর লোকদের প্রত্যেককে দেওয়া
হয়েছিল ২৪০০০ পাউন্ড।
মীর জাফর কর্তৃক
পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের তালিকা—
গভর্নর ড্রেক—৩১,৫০০ পাউন্ড, লর্ড ক্লাইভ—২,১১, ৫০০ পাউন্ড, মিঃ
ওয়াটসন—১,১৭,০০০ পাউন্ড, কিল প্যাট্রিক—৬০,৭৫০ পাউন্ড, মিঃ ম্যানিংহাম—২৭,০০০ পাউন্ড, মিঃ বিচার—২৭,০০০ পাউন্ড, মিঃ বোডম—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ ম্যাকেট—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ আ্যামিয়েট—১১,৩৬৬ পাউন্ড, মিঃ পার্কেস—১১,৩৬৬ পাউন্ড, মিঃ ওয়ালশ—৫৬,২৫০ পাউন্ড, মিঃ স্ক্রাপটন—২২,৫০০ পাউন্ড, মিঃ ল্যাসংটন—৫৬২৫ পাউন্ড, মেজর গ্রান্ট—১১২৫০ পাউন্ড।
ইংরেজের বিজয়
উপলক্ষ্যে কিছু বাঙালিবাবুও পুরস্কৃত হয়েছিলেন। একে পুরস্কার না বলে ক্ষতিপূরণ
নাম দেওয়া হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ নীলমণি ঠাকুর পেয়েছিলেন
মীরজাফরের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ হিসাবে—১৩,০০০ টাকা। সেই টাকা দিয়ে কোলকাতা
গ্রামের পাথুরিয়াঘাটা পাড়ার জমি কিনে ভিটে তোলেন। সেখানে পরবর্তি সময়ে একঘর
পাথুরিঘাটের জমিদারদের পত্তন হয়।
মীর জাফরকে সরিয়ে
মীরকাশেমকে ১৭৬০ সালে পুতুল নবাব হিসেবে কোম্পানী বাংলার গদিতে বসায়। সে
উপলক্ষ্যেও বিস্তর পুরস্কার জুটেছিল এই পরদেশী লুটেরাদের। পুরস্কারপ্রাপ্তদের
তালিকা—গভর্নর ভ্যানসিটার্ট—৫৮,৩৩৩ পাউন্ড, মিঃ হলওয়েল—৩০,৯৩৭ পাউন্ড, মিঃ সুমনার—২৮০০০ পাউন্ড, জেনারেল
কাইলাইড—২২ম৯২৬ পাউন্ড, মিঃ ম্যাকগুইরি—২২,৯১৬ পাউন্ড, মিঃ স্মিথ—১৫, ৩৫৪ পাউন্ড, মিঃ ইয়র্ক—১৫, ৩৫৪ পাউন্ড।
১৯৬৪-৬৫ সালে
মীরকাশেমকে সরিয়ে নরমপন্থী নিজামউদ্দৌলাকে গদিতে বসানে হলে আবারও পুরস্কার পায়
মেজর মনরো—১৩০০০ পাউন্ড, তার অধীনস্ত সাহবরা পেল আরও ৩০০০ পাউন্ড করে
পুরস্কার। আরও অনেকে পেয়েছে। দাগি মুদ্রারাক্ষস লর্ড ক্লাইভ পেয়েছিলেন—৫৮,৬৬৬ পাউন্ড।
মুর্শিদাবাদের নবাবদের
কাছ থেকে এই পুরস্কার আদায়ের টাকাটা আসমান থেকে আসেনি। এই টাকাটা বাংলার
প্রজাদেরই টাকা। অভাবী ভুখা নাঙ্গা প্রজাদের কাছ থেকেই আদায় করা হয়েছিল।
তাদের রক্ত শোষণ করে অর্জন করেছিল জমিদার, তালুকদার, গাত্তিদাররা। তারা জমা দিয়েছিলেন রাজকোষে। সেখান থেকে ইংরেজরা
নিয়েছে।
Prosperous Britis India নামে একটি বই লিখেছিলেন মিঃ ডিগবি। তিনি লিখেছেন—পলাশী এবং ওয়ার্টারলুর যুদ্ধের মধ্যবর্তি সময়ে ভারত থেকে ইংলন্ডে
অন্তত ১০ কেটি পাউন্ড নগদ অর্থ চলে গিয়েছিল। The Law of Civilization and Decay নামে আরেকটি বই লিখেছেন ব্রুকস এডামস। তিনি বলেছেন— শিল্পবিপ্লব কার্যত শুরু হয় ১৭৬০ সালে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ
অর্থ ও সোনা-রূপা ইংলন্ডে পৌঁছানোর পরে।
আর সে সময়ে বাংলায়
দুর্ভিক্ষে মানুষ গরু-জরু বেঁচে দিচ্ছে। গাছের পাতা-ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা
করছে। না খেতে পেয়ে তিনভাগের এক ভাগ মানুষ মারা যাচ্ছে। তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ
খাজনা দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে বাঘের পেটে যাচ্ছে। বাকীদের পিঠের
চামড়া তুলে খাজনা আদায় করে এইসব ইংরেজ লুটেরাদের পকেটে ভরে দেওয়া হচ্ছে।
১৭৮২ সালে ইংলন্ডে
পৌঁছে মেজর জন স্কট ওয়ারেন হেস্টংইসকে একটি চিঠিতে লিখছেন—আমাদের ব্যবসার হয়তো মন্দা দেখা দিয়েছে, কিন্তু আজকের
মতো এমন বিপুল বৈভব বোধহয় এই রাজ্যে কখনো ছিল না। আমি ২০০ সোনার মোহর গলাতে
দিয়েছিলাম একজনকে, তিনি জানালেন গত বারো বছর তিনি অন্তত
দেড় টন সোনার মোহর এবং প্যাগোডা গলিয়ে ‘বার’ তেরি করে দিয়েছেন। তার মানে প্রতি বছর গড়ে ইংলন্ডে মজুত
হয়েছে ১৫০ হাজার পাউন্ড।
কেউ কেউ আবার সে সময়
বাংলা থেকে ইংলন্ডে হীরেও নিয়ে যেত। হীরের আমদানি এত বেড়ে গিয়েছিল যে তখন
ইউরোপের বাজারে হীরার দাম পড়ে গিয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসপত্নী কোনো পার্টিতে
তিরিশ হাজার পাউন্ডের গহনা পরে যেতেন। এই টাকা বাংলার মানুষের টাকা।
১৭৬৯ সালে বাংলাকে
কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা
হয়। এই পদটিই ১৭৭২ সালে কালেক্টারে রূপান্তরিত করা হয়। এই
জেলার কালেক্টারদের প্রধান কাজই ছিল দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া।
কেউ কেউ এরা সুদের ব্যবসা করতেন। কেই কেউ দুনম্বরী ব্যবসাবানিজ্য। জন বাথো নামে
বর্ধমানের এক কালেক্টার দেশী একজন জমিদারকে লবণের ব্যবসা পাইয়ে দেন বার্ষিক আটাশ
হাজার পাউন্ড ঘুষের বিনিময়ে। শ্রীহট্টের কালেক্টার কোম্পানীর কাছে হাতির ব্যবসা
করে অনেক টাকা রোজগার করেছেন।
ক্লাইভ আঠার বছর বয়সে
ভারতে এসেছিলেন। তিনি চাকরী পেয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে একজন রাইটার বা
কেরানী হিসেবে। পরে প্রতিভাবলে কোম্পানীর উচ্চপদে চলে যান। হয়েছিলেন
গভর্নর জেনারেল। সিরাজউদ্দৌলাকে হারানোর পরে ১৭৬০ সালে ক্লাইভ যখন ইংলন্ডে ফিরে
যান তখন সঙ্গে নিয়েছিলেন তিন লক্ষ পাউন্ড। ভারত থেকে তার জমি সম্পত্তির আয় থেকে
বার্ষিক আয় ছিল ২৭০০০ পাউন্ড। সে সময়ে তার বার্ষিক আয় ছিল ৪০০০০ পাউন্ড।
এই ইংরেজরা তখন হয়েছিলেন
নবাব। এইরকম একজন নবাবের নাম হল---মিঃ হিকি। উইলিয়াম ম্যাকিনটস হিকির দৈনন্দিন
জীবন সম্পর্কে লিখেছেন-- সকাল সাতটা নাগাদ দারোয়ান নবাববাহাদুরের গেট খুলে দিল। নিমেষে
বারান্দাটি সলিসিটার, রাইটার, সরকার,
পিওন, হরকরা, চোপদার,
হুক-বরদার ইত্যাদিতে ভরে গেল। বেলা আটটায় হেড বেয়ারা এবং
জমাদার প্রভুর শোয়ার ঘরে প্রবেশ করবে। একটি মহিলাকে তখন শয্যাত্যাগ করে একান্তে
প্রাইভেট সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে দেখা যাবে,--অথবা বাড়ির
অঙ্গন পরিত্যাগ। নবাব বাহাদুর খাট থেকে মাটিতে পা রাখামাত্র অপেক্ষমান ভৃত্যবহর
তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে পড়বে। তারা আনত মাথায় পিঠ বাঁকিয়ে প্রত্যেকে তিনবার তাঁকে
সেলাম জানাবে। ওদের হাতের একদিক তখন কপাল স্পর্শ করবে, উল্টো
দিকটা থাকবে মেঝেতে। তিনি মাথা নেড়ে অথবা
দৃষ্টিদানে তাদের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি জানাবেন।
পারসিভাল স্পিয়ার
একটি বই লিখেছেন—The Nababs নামে।
বইটিতে কয়েকজন মৃত লুটেরা নবাব সাহেবের রেখে
যাওয়া অস্থাবর সম্পত্তির বিববরণ আছে। তার মধ্যে
নিকোলাসের ঘরে পাওয়া যায় রাশি রাশি দামি আসবাব। বেশ কিছু ঘড়ি, আয়না, লণ্ঠন, রকমারি
পালকি, বিপুল সংখ্যক বাসনপত্র, চা,
কফি, পান, তামাকের
বিবিধ সরঞ্জাম, বিভিন্ন মদের বোতল এবং আরও অনেক কিছু। তার
মালসামানের জন্য ছিল পাঁচটি গুদাম। বারওয়েল নামের একজন নবাবের খাওয়ার সময়
উপস্থিত থাকত প্রাতঃরাসের সময় তিরিশজন, মধ্যাহ্ণভোজের
সময় পঞ্চাশজন এবং রাত্রির খাওয়ার সময়ে অগণিত। খেয়ে দেয়ে মধ্যরাত্র অবধি নাচের
আসর হত। ভোর পর্যন্ত মদ্যপান।
হিকি নামে একজন নবাব
১৭৯৬ সালে গভর্নরের বাড়ির পাশেই পার্কের গা ঘেষে নদী পড়ে একটি প্রাসাদতুল্য
বাংলো তৈরি করেছিলেন মাত্র ছয়মাসের মধ্যে। তার আর্কিটেক্ট আর মিস্ত্রিরা ছিল
পশ্চিমি। কলকাতার চূঁচুড়ার এই বাংলোটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন তার রক্ষিতা এক
জমাদারনিকে। তার খরচ পড়েছিল চল্লিশ হাজার টাকা। হিকির বউ শার্লট যখন মারা গেল তখন
হিকির জন্য কাজ করত তেষট্টিজন ভৃত্য।
এরকম রাশি রাশি নবাব
তখন কোলকাতায় ছিলেন। তারা বাংলাকে লুটপাট করেছেন। এদের লুটপাটের অর্থের অন্যতম
যোগানদাতা ছিলেন স্থানীয় বাবুশ্রেণী, জমিদার।
এই নবাবদের ইংলন্ডের
সমাজে ভাল চোখে দেখ হত না। তাদের মন্তব্য হল-- এরা সবাই হয়
দারোয়ান-তনয় অথবা দাসীপুত্র। হৃদয়হীন এই পাষণ্ডের দল প্রত্যেকই হাজার হাজার
নেটিভের হত্যাকারী। হিন্দুস্থানে তাঁদের কেউ একশো নিরীহ মানুষ খুন করে এসেছেন—কেউ বা পঞ্চাশ হাজার। এদের দিকে তাকানোও পাপ।
তারা বাংলা থেকে
লুটপাট করা অর্থ দিয়ে ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন বিলাসবহুল জীবন। টাকা পয়সা দিয়ে ১৭৬০
থেকে ১৭৮৪ সালে এরকম ৩০জন নবাব পার্লামেন্টের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এদের সম্পর্কে
একজন লিখেছেন—লজ্জার কথা সেদিন জনৈক নবাব এক ভদ্রসম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি
সঙ্গে নিয়েছিলেন একজন রূপোজীবিনীকে। অন্য একজন লিখেছেন—সাবধান,
কোনও ভদ্রমহিলা যেন ভুলেও কখনও কোনও নবাবের সঙ্গে না নাচেন।
তাদের নবাব তখন দাস-ব্যবসায়ী. ওয়েস্ট ইন্ডিজের খামার মালিকের চেয়েও ঘৃণ্য এক
অসামাজিক জীব। তারা ভালো বাড়ি কেনে, ভালো খায়, যত খায় তার চেয়ে বেশি অপচয় করে, ছড়ায়।
তারা ডুয়েল লড়ে, জুয়া খেলে,--মাত্রাহীন
বিলাসে গা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করে।
পর্ব পাঁচ.....
একটু ইংরেজদের গেড়ে
বসার আদিকাণ্ড--
সপ্তদশ শতকের প্রথম
দিকে মুগল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বানিজ্যের উদ্দেশ্যে সুরাটে
একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। কয়েক বছর পরে তারা দক্ষিণ ভারতে একখণ্ড জমি
কিনে মাদ্রাজ শহর পত্তন করে। ১৬৬২ সালে ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পোর্তুগালের
কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি বিয়ের যৌতুক হিসেবে লাভ করেন। তিনি কোম্পানীর কাছে এই
দ্বীপটি হস্তান্তরিত করেন। ১৬৯০ সালে কোলকাতা শহর জোব চার্নক নামে এক ইংরেজ
প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরেজ
তারা আস্তানা গাড়ে। সমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি ঘাঁটি বসায়। ক্রমে ক্রমে তারা দেশের
প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরে বিস্তির্ণ
ভূখণ্ড ইংরেজদের দখলে আসে। কয়েক বছরের মধ্যে তারা বাংলা, বিহার ও
উড়িশ্যা দখল করে বসে। এবং সমগ্র পূর্ব-উপকূলে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।
এর চল্লিশ বছর পর, উনবিংশ শতকের
গোড়ার দিকে তারা একবারে দিল্লীর তোরণদ্বারে হানা দেয়। ১৮১৮ সালে মারাঠাদের
পরাজিত করে। ১৮৪৯ সালে শিখ-যুদ্ধের পর ইংরেজ সারা ভারতবর্ষে কায়েম হয়ে বসে।
মধ্যবিত্তের উত্থান
ইংরেজ শাসনে জমিদারদের
প্রজাশোষণে লোকজন অনাহারে অত্যাচারে মারা গিয়েছে। অনেকে সব ছেড়ে ছুড়ে অন্য
জমিদারের পরগণায় আশ্রয় নিয়েছে। আর যারা বনেজঙ্গলে পালিয়েছে তারা বাঘের আর
কুমিরের পেটে গিয়েছে। অনেক নতুন নতুন জমিদার পুরনো জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারী
কিনে নতুন খাজনার হার ধার্য করেছে। এর মধ্যে অনেক প্রজা কখনো কখনো রুখেও
দাড়িয়েছে। ১৮৭৩ সালে পাবনাতে নাটরের জমিদারি ভেঙে পাঁচজন
ধনী লোক জমিদার কিনে যখন খাজনা বাড়াতে চেয়েছিল তখন প্রজাদের সঙ্গে জমিদারদের বড়
ধরনের রায়ট হয়েছিল।
চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের ২০ বছরের
মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারার জন্য তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি পুরনো
জমিদাররা জমিদারী খুইয়েছিলেন। এসব জমিদারি এসেছে নব্য ধনীদের মধ্যে। তখন ব্যবসার
চেয়ে জমিদারদের সামাজিক মর্যাদা বেশি ছিল। কিন্তু এইসব জমিদাররা নিজেরা কখনো
জমিদারি পরিচালনা করেননি। তারা অন্য লোকদের দিয়ে জমিদারি পরিচালনা করেছেন। তারা
হয়েছেন অনুপস্থিত জমিদার।
হেস্টিংসের আমলে
গোড়ার দিকে জমিদারের সংখ্যা মাত্র শ খানেক, সেখানে ১৮৭২-৭৩ সালে এই সংখ্যা দাড়ায় ১ লাখ
৫৪ হাজার ২ শোতে। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৭ হাজার জমিদারের সম্পত্তি ছিল মাথা পিছু ৫০০
একরেরও কম।
জমিদার এবং
মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রজাদের খাজনা দিতে হয়েছে বেশি। ১৭৭২
সালে রাজস্ব আদায় হয়েছিল তিন কোটি টাকা, কিন্তু একশো বছর পরে ১৮৭২ সালে জমিদার এবং
মধ্যস্বত্বভোগীরা রাজস্ব আদায় করতেন ১৭-১৮ কোটি টাকা।
বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যই
ছিল ভারতে জমিদার, তালুকদার, জোদ্দার,
ধনী কৃষক সৃষ্টি করে একটি অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা। তাদের শোষণে
যদি কখনো প্রজাবিদ্রোহ হয়, তাহলে এই অনুগত বাহিনীই
প্রজাদের বিদ্রোহ থেকে তাদের বাঁচাবে। তাদের ব্যবসা-বানিজ্য-শোষণ কৌশল টিকে থাকবে।
এদের পাশাপাশি বিশেষভাবে রাজভক্ত বা অনুগত প্রজাদেরও তাদের কোম্পানীতে,
ব্যবসাবানিজ্যে, জমিদারী-সেরেস্তায়
কিছু দায়িত্বজনক পদ দিয়ে জমিদারি পরিচালনার কাজ পাইয়ে দেয়। এভাবে কিছু ধনীক
শ্রেণীও ইংরেজরা তৈরি করল।দেশে পরজীবী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হল ইংরেজ
আমলে।
বেহাল কৃষি ব্যবস্থা
ইংরেজদের আগমণের আগে
বাংলার শুধুমাত্র অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ছিল না। দেশে শিল্পী দক্ষ কারিগরী পেশায় লোকের
সংখ্যা ছিল প্রচুর। সে সময় মানুষের বড় ধরনের শিল্প না থাকলেও ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র
শিল্প-কুটির শিল্প ছিল। সেখানে কাজ করতে করতে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজন সেই কাজে
খুব দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারা পরিচিত হয়েছিল—তাঁতী বা জোলা, কামার,
কুমোর, সুতোর ইত্যাদি নামে। চাষীরাও সে
সময় চাষের অবসরে বা ফাঁকে ফাঁকে এইসব কুটির শিল্পে কাজ পেত এবং বাড়তি আয়ের
সুযোগ ঘটত তাদের। ফলে দেশে মানুষের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না।
এই গ্রামবাংলার ঘরে
উৎপাদিত মসলিন কাপড়ের খ্যাতি তখন শুধু দেশেই নয় সারা বিশ্বজোড়া। বিদেশীরা মসলিন
কিনতে ভারতে আসত। বাংলা থেকে তা কিনে উচ্চদামে ইউরোপে বিক্রি করত। তারা খুঁজে বের
করত কোথায় এই মসলিন উৎপাদিত হয়। শোনা যায় কলম্বাসও এই মসলিনের খোজেই ভারত
আবিষ্কারের জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন।
ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানী ভারতে আসার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য, শাল, মসলিনজাতীয় বস্ত্র ও নানাবিধ মসলা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ থেকে
পাশ্চাত্যে চালান করা। সে সময়ে ইউরোপে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল। বাংলায় যখন
কোম্পানীর শাসন জেঁকে বসেছে—লুটপাটের টাকায় ইংলণ্ডে
শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে তখন ইংলন্ডের একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা দাবী করে বসে
ইংলন্ডের শিল্পবাজার প্রসারের জন্য ভারত থেকে পণ্য আমদানী বন্ধ করে দিতে হবে।
বৃটিশ পার্লামেন্ট সে দাবী মেনে নেয়।
তখন ভারতের
বহির্বানিজ্য সম্পূর্ণভাবে কোম্পানী নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভারত থেকে পণ্য ইউরোপের
অন্য দেশেও প্রবেশাধিকারের সুযোগ হারাল। ইংলণ্ডে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভারতে
একচেটিয়াভাবে আসা শুরু করল। একই সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের পণ্যের উপরে কোম্পানী
চড়া কর বসিয়ে দিল। ফলে ইংলণ্ডের পণ্য কম দামে বাজারে পাওয়া যেতে লাগল। এইভাবে
দেশী পণ্যের বাজার পড়ে গেল। দেশী পণ্য একই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী বাজার হারাল। ফলে
দেশের শিল্প খাতটি সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। জহর লাল নেহেরু বলেছেন—উনিশ শতকের ভারত ইতিহাস হল ধ্বংসপর্বের ইতিহাস--পুরাতন শিল্পাদি
নিশ্চিহ্ণ করার ইতিহাস। জাহাজী কারবার কাজ, বস্ত্র শিল্প, ধাতব
পদার্থের কাজ, কাঁচ তৈরির কাজ, কাগজ
তৈরির কাজ—আরও অনেক শিল্প মৃত্যুমুখে পতিত
হল।
ভারতের শিল্পোন্নতি
যাতে না হয়, যাতে শিল্পের দিক থেকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ অবনতিলাভ করে—সেদিকেই ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল বেশি। যন্ত্রপাতি ভারতে যাতে না আসতে
পারে তার জন্য নিয়ম করা হল। বাজারে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হল যে বৃটিশ পণ্য
না হলে যেন ভারতের না চলে। ইংলন্ড দ্রুত তার শিল্পোন্নতির দিকে এগিয়ে চলল, ভারত হয়ে গেল
কৃষিনির্ভর দেশ। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শতকরা পঞ্চান্ন লোক এদেশে কৃষিদ্বরা
জীবিকানির্বাহ করত। ইংরেজদের এই শিল্পধ্বংসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃষিজীবিীর সংক্যা
বেড়ে দাড়িয়েছির শতকরা চুয়াত্তর জন। এদেশ
থেকে সস্তায় কাঁচা মাল ইংরন্ডের কারখানায় চলে গেল এবং বিলেতের কারখানাজাত
শিল্পসম্ভার এই দেশের বাজারই চড়া মূল্য বিক্রি হতে লাগল। ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র
বাংলা হওয়ায় বাংলার অবস্থাই সবচেয়ে করুণ হয়ে পড়ল।
ভারত-ইতাহাসের যুগ্ম
লেখক এডওয়ার্ড টমসন ও জি.টি. গ্যারেট লিখেছেন, ইংরেজদের ঐশ্বর্য্যলিপ্সা একটা
যেন রোগের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ-বিষয়ে তারা কোর্টেস ও পিৎসারোর আমলের
স্প্যানিশদের পর্যন্ত হার মানিয়েছিল। একেবারে নিঃশেষে শোষিত না হওয়া পর্যন্ত এই
বাংলাদেশের আর শান্তি ছিল না।
ভূমিহীন ও বর্গাচাষীর
বেত্তান্ত
ইংরেজরা বাংলার
ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুকৌশলে বাংলার এই কুটির শিল্পকে পুরোপুরি ধ্বংশ
করে দেয়। ফলে এই কুটির শিল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। লক্ষ
লক্ষ শিল্পী ও কারিগররা আত্মহত্যা করে-- মরে যায়। ১৮৩৪ সালে বড়লাট লর্ড বেন্টিংক
তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন—ব্যবসা বানিজ্যের ইতিহাসে এই রকম
দুরাবস্থার তুলনা খুবই কম মেলে। সমগ্র ভারত ভূখণ্ড তাঁতি জোলা সম্প্রদায়ের
অস্থি-কঙ্কালে পরিকীর্ণ হয়ে আছে।
এদের কাজ ছিল না, উপজীবিকা ছিল
না, বহু বংশপরম্পরায় অর্জিত দক্ষতা বা
শিল্পকুশলতাও কাজের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। বেঁচে থাকার জন্য তারা তখন
কৃষিকাজের দিকে ছুটে আসে। ফলে এরা জমির উপর বিরাট ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। তারা
পরিণত হয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে। কেউ কেউ হল বর্গা চাষী। এদের জীবন ছিল মানবেতর।
সভ্যজগতে যাকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা বলে তার বহু নিচের স্তরে লোকে কোনোমতে
প্রাণধারণ করতে লাগল। এরা পরের জমিতে কাজ করে—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু ফসলের উপরে তাদের
অধিকার নেই। তাদের আয় খুবই কম। বর্গচাষীদেরকে জমির মালিকরা ভয়ঙ্কর জটিল
পদ্ধতিতে জমি ভাড়া দেওয়া শুরু করে। মালিকরা জমি ভাড়া দেওয়া ছাড়া জমিতে আর
কোনো পূঁজি বিনিয়োগ না করেই বর্গাচাষীর কাছ থেকে ফসলের বড় ভাগ পায়।
ভূমিহীন ক্ষেতমজুর আর
বর্গাচাষীরা হয়ে উঠে দাসশ্রমিকের মত। তার সঙ্গে মহাজনদের কবলে পড়ে এই দাসজীবনের
পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। প্রজাদের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যেতে লাগল।
এইভাবে হাত বদলানোয়
জমিগুলি দিন দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোয় পরিণত হয়ে এক অদ্ভুত
অবস্থার সৃষ্টি করল। কৃষকরা ঋণের ফাঁদে পড়ে
মহাজনদের কাছে বেঁচে দিতে বাধ্য হল। ক্ষুদ্র কৃসকদের জমি গিলে নতুন নতুন ভূস্বামী
সৃষ্ট হল। পরিচিত হল বাবুতে। ভূমিহীন শ্রমজীবীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বেড়ে উঠল।
ক্ষুদ্র কৃষক-ভূমিহীন
ক্ষেতমজুরদের জন্য তৎকালীন সরকারও কিছু করে নাই। পরবর্তিতে যখন রাজনীতিবিদদের
উত্থান হল—তারাও তাদের জন্য কিছু ভাবে নাই।
জমির আয় খুব লাভজনক ও
সম্মানজনক বলে তখন শিক্ষিতবাবুরা এবং ব্যবসায়ীরা জমি কিনে ভাড়া দিতে শুরু করল।
এইসব জমির মালিকরা
পরজীবী শ্রেণী সমাজে নতুন করে শোষক
হিসেবে আর্বিভূত হয়।
পর্ব ছয়...
বাবুরাম সাপুড়ে
কোথা যাস বাপুরে।।
নববাবুবিলাস সম্বাদ
১৮৭২ সালে প্রথম যখন
আদম শুমারী হয়। সেখানে দেখা যায়—সত্তরের মন্বন্তরের ক্ষতি পূরণ
হতে প্রায় একশ বছর সময় লেগেছিল। দুই তৃতীয়াংশ লোকই হয় মরে গিয়েছিল—নয় পালিয়ে গিয়েছিল, ফলে প্রথম দিকে জমির পরিমাণ ছিল প্রচুর। কিন্তু
চাষের লোক ছিল খুবই কম। যারা ছিল তারা জমিদারের শোষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের
কারণে শস্যচাষে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। ইংরেজরা বাংলা দখল করার পরে দেশে অসংখ্য
ক্ষুদে সামন্ত বা জমিদার এবং বরগা চাষীর সৃষ্টি হয়। এর আগে মধ্যবিত্ত বলে কোনো
সম্প্রদায় ছিল না।
তখন দেশটি পুরোপুরি
বৃটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। মাত্র ১০-১৫ জন বৃটিশ লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের উপর
ছড়ি ঘোরাত। এই ছড়ি ঘোরানোর কাজটি করা হত স্থানীয় অনুগত শ্রেণীর লোকদের
সহায়তায়। এই অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করার জন্য ইংরেজরা ইংরেজি শিক্ষা চালু করে।
বাঙ্গালী বাবুরাই ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে আসে। তারা ইংরেজি শিখে সাহেবদের দোভাষী, মুনশি,
দেওয়ান ইত্যাদি কাজে ভিড়ে যেত। তাদের এই ভিড়ে যাওয়াকে বলা
হয় সাহেব ধরা। সাহেবরা চাকরী, দুর্নীতি, ব্যবস্যা-বানিজ্য, জমিদারি, নবাবীর নামে যেসব লুণ্ঠন করত এইসব বাঙ্গালী বাবুরা তাদের সহযোগী হিসাবে
বেশ বড় অঙ্কের বেতন পেত—বখরা পেত। এভাবে দেশে তখন নতুন
ধরনের শিক্ষিত ধনীক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা এইসব টাকা পয়সা দিয়ে নানা ধরনের
ব্যবসা-বানিজ্য করেছে। জমিদারীও কিনেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার এক
দশকের মধ্যেই কোলকাতায় থেকে নতুন ধরনের শোষক বাবু শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।
এরাই পুরনো জমিদারদের হটিয়ে আরও হৃদয়হীন জমিদারে পরিণত হয়েছে।
এই শিক্ষিত বাবুরা
একটু ইংরেজি শিখেই সাহেব ধরতে শিখত। বাবুরা কোলকাতায় বনবাস করত। কোলকাতা শুরুতে
ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পন্য আমদান-রপ্তানীর কেন্দ্র। ইংরেজ শাসন কায়েম
হওয়ার পরপরই কোলকাতাকে সারা ভারতের রাজধানী করা হয়। হয়ে ওঠে বৈদেশিক বানিজ্যের
প্রধান কেন্দ্র। ইংলল্ড থেকে তখন ভাগ্যান্বেষণে ইংরেজরা কোলকাতায় আসত। এই
ইংরেজরা বাংলা ভাষা জানত না। এই মধ্যবিত্ত বাবুরা
তাদেরকে জাহাজঘাটা থেকেই পাকড়াও করত। তারা সাহেবদের কেরানীর চাকরী করত। আবার কিছু
কিছু বাঙালিরা ইংরেজী জানত না। কিন্তু দেখে দেখে কোম্পানীর দলিলপত্রাদি না বুঝেই
হুবহু নকল করতে পারত। এদের নাম ছিল মুনশী। এরাই আবার প্রমোশন পেয়ে দেওয়ান হত।
এরা নানা কায়দায় বেতনসহ নজরানা দস্তুরী আদায় করত ইংরেজদের কাছ থেকে। এভাবে তারা
বেশ অর্থসম্পদের মালিক হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসা বানিজ্য খুলেছিল। কেউ কেউ জমিদারও
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ জয়রাম ছিলেন
ইংরেজদের এ ধরনের ঠিকাদার। হয়েছিলেন হুইলার সাহেবের দেওয়ান। রামমোহন রায়ও ছিলেন
কোম্পানীর সেরেস্তাদার—পরে দেওয়ান।
ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানীর আদি সহযোগীর অন্যতম ছিলেন শোভারাম বসাক। ১৭৮০ সালে তার মৃত্যু হয়।
ইংরেজদের সঙ্গে ওঠাবসা করে তার সম্পত্তির পরিমাণ—কোলকাতার বগবাজার
এলাকায় ৩৭টি বাড়ি,
কৌরকাতার বিভিন্ন এলাকায় ৩টি বাগান ও পুকুর। মারা যাওয়ার পরে
তার গুদামে ছিল নানা ধরনের বিপুল পরিমাণ কাপড়, ৫ মন
রকমারি মশলা, ১৮ মন আফিং, এবং
পরিমাণমত চন্দনকাঠ, তামা, সিসা,
লবঙ্গ, ফিটকিরি ইত্যাদি। সিন্দুকে ছিল
৮৯১টি মুক্তা—এর মধ্যে ৬১টি আবার আকারে বেশ বড়, ৪১৩টি হিরা,
৩৫টি পদ্মরাগ মণি। তাছাড়া অনেক মোহর, সোনার
ছড়া ইত্যাদি। সাহেবদেরও তিনি টাকা সুদে ধার দিতেন। তাদের কাছে তার পাওনা ছিল ৫
লক্ষ ২৭ হাজার ১১২ টাকা। দেশীয় লোকদের কাছে পাওনা ৫৩ হাজার ৮৩ টাকা। সুয়েজ,
বোম্বাই এবং বসরার বণিকদের কাছে পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৭৫ হাজার
৭৫১ টাকা। এ ছাড়াও মালদা, কাশিমবাজার, হরিয়াল, ক্সীরপাই ও ঘাটালে শোভারাম বসাকের
নিজস্ব আড়ং ছিল।
লুণ্ঠনপর্বের শুরুতেই
ইংরেজ কোম্পানী জাহাজে করে এদেশ থেকে মালপত্র ইংলন্ডে নিয়ে যেত। ফেরার পথে খালি
জাহাজ নিয়ে আসার কিছু সমস্যা ছিল। ঝড়ের কবলে পড়লে জাহাজ ডুবির আশঙ্কা ছিল।
সেকারণে তারা সে সময়ে খুবই সস্তা লবণ জাহাজ ভরে নিয়ে আসত। যাত্রা শেষে সে সব নুন
সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আবার জাহাজ খালি করত। ইংরেজদের ব্যবসাবুদ্ধি ছিল অতি প্রখর।
তারা স্থানীয় কিছু অনুগত বাঙ্গালীকে ধরে এই লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করে। তখন এদেশে
লবণের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু কোম্পানী বাজারে প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় লবণ
বিক্রি থামিয়ে দিয়ে বিলেতি লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল। সেই লবণের টাকায় অনেক
বাঙ্গালী বিপুল অর্থসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। তারা হয়েছিল দেওয়ান, উপদেওয়ান।
কেউ কেউ হয়েছিলেন একদম নিঃস্ব থেকে উচ্চবিত্ত—মধ্যবিত্ত।
পদ্মলোচন নামে এক
ভদ্রলোকবাবুর খবর জানতে পারা যায় হুতুম প্যাঁচার নকশায়। পদ্মলোচন খুব গরীব ঘরের
সন্তান। গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে গৃহভৃত্যের কাজ নেয়। কিন্তু কায়দা করে
টাকাপয়সা আয় করে একজন বড় মানুষে পরিণত হয়েছিলে। হুতুম প্যাচার নকশায় লেখা
হয়েছে —
‘’ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন কত্তে লাগলেন, অবস্থা উপযোগী
একটি নতুন বাড়ি কিনলেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল
জিনিসপত্র উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবরা
সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পূরণ করে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্সে) একটি রাঁঢ়ও রাখলেন।‘’
আরেকজন বাবুর নাম জানা
যায়—নাম বিশ্বনাথ মতিলাল। তিনি শেষ বয়সে এসে গান-বাজনা, হাফ-আখড়াই আর
শখের যাত্রা নিয়ে খুব মেতেছিলেন। তার অগাধ সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন তার
ছেলেপেলেদের মধ্যে। কোলকাতার তার এক ছেলের বউয়ের নামেই একটি বাজার বসিয়েছিলেন।
সে বাজারটির নাম বউবাজার। এই বউবাজরটিতে সে সমযের বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য বারবণিতাদের
সবচেয়ে পল্লী গড়ে উঠেছিল। এখানে এই বড় বড় বাবুরা ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার
লুটপাটের টাকা পয়সা দিয়ে, জমিদারী প্রজাশোষণের টাকা
দিয়ে তাদের রক্ষিতা রাঢ়দের জন্য বাড়ি করে দিতেন। ভাগ্যান্বষণে অনেক মুসলমান ও
পশ্চিমা বাঈজিরাও এখানে আসর বসাত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল নিকি বাঈ। তাকে
তার বাবু প্রতিমাসে সে সময়ে এক হাজার টাকা দিয়ে পুষতেন। পাইকার, ব্যাপারী আর ইজারাদারদের রাত্রিবাসের জন্য অনেক টোটেল গড়ে উঠেছিল।
সেখানে রাতকাটানোর জন্য বারবণিতাদের সহজে পাওয়া যেত। তাদের জন্য তখন সৌখিন পোষাক
আষাক আর গহনার দোকানপাটেরও রমরমা ছিল।
পূর্ব বাংলা থেকে
আসতেন বাঙ্গাল জমিদার,
তালুকদার আর ইজারাদাররা। তারা আসতেন বজরায় করে। তাদের পাণ্ডারা
ধরে বারবণিতাদের কাছে নিয়ে যেত। আর কিছুদিন ফূর্তিফার্তা করে সর্বস্ব খুইয়ে দেশে
ফিরে যেত। আবার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কোলকাতায় ফিরে আসত।
ঠিক সে সময়েই গ্রামের
মানুষ না খেয়ে মরছে। সে সময়ে পথে ঘাটে, মন্দিরচত্বরে খ্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে অনেক
মা তাদের শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতেন। পালিয়ে গিয়ে এদের উঠতে হত এইসব
বউবাজারের মত বারবণিতা পল্লীতে।
১৮২০ সালে ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুবিলাস নামে একটি বই লেখেন। সেখানে বাবু বলতে তরুণ
নব্যধনীদের কথা বুঝিয়েছেন। ইংরেজরা বাবু শব্দটিকে ইংরেজিজানা বাঙালি
কেরানীকে বুঝত। তারা ১৭৮২ সালে এই বাবু শব্দটিকে দলিলপত্রাদিতে ব্যবহার করা শুরু
করে। আর বাঙালিদের কাছে বাবু মানে মনিব।
উনিশ
শতকের গোড়ার দিকে যারা জমিদারি কিনে অথবা ব্যবসা বানিজ্য করে কৌলকাতায় নব্যধনী
হয়েছিলেন--তারাই বাবু হিসেবে পরিচিত হতেন সে সময়ে। ১৮৫০ সালের দিকে বাবু বলতে
সংবাদপত্রে জমিদার, ব্যবসায়অর সঙ্গে ধনী পরিবারের অলস
তরুণদের বোঝানো হত। এরা ছিলেন আলালের ঘরের দুলাল। ১৮৬০ সালের দিকে বাবু শব্দটি আরও
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তখন চাকরীজীবীদের মধ্যে বড়বাবু, ছোটো বাবু ইত্যাদি শব্দ এসে যায়। এমনকি পরিবারের বড়ো ভাইকে বড় বাবু,
মেজো ভাইকে মেজো বাবু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। বাবুদের
গিন্নীদের বলা গত বিবি। ভাবানীচরণ এইসব বিবিদের নিয়ে নববিবিবিলাস নামে আরেকখানি
বই লিখেছেন। মুসলমানদের মধ্যে বাবু শব্দটির বদলে সাহেব শব্দটিই বেছে নেওয়া হত।
এ ধরনের বাবু রাজা
রামমোহন রায়ের বাড়ির একটি উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায় ফেনি পার্কসের
ভ্রমণকাহিনীতে। ভ্রমণকাহিনীর নাম Wanderings of a Pilgrim in search of Picturesque ।
তিনি
১৮২৩ সালে কলকাতায় রামোহনেরবাড়িতে নাচের আসরে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন—
একদিন এক ধনিক
সম্ভ্রান্ত বাঙালিবাবুর বাড়ি ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবুর নাম
রামমোহন রায়। বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে তার বাড়ি; ভোজের দিন নানা বর্ণের আলো দিয়ে
সাজানো হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজির খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তার
বাড়ি।
বাড়িতে বড় বড় ঘর
এবং একাধিক ঘরে বাইজি ও নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। বাইজিদের পরনে ছিল ঘাঘরা, সাদা ও রঙিন
মসলিনের ফ্রিল দেওয়া, তার উপর সোনারূপার জরির কাজ করা।
শাটিনের ঢিলে পায়জামা পা পর্যন্ত ঢাকা। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, পোষাকে ও আলোয় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়েতে অলঙ্কার ছিল নানারকমের।
...বাইজিদের একজনের নাম নিকি, শুনেছি সারা প্রাচ্যের
বাইজিদের মধ্যে মহারানি সে, তার নাচগান শুনতে পাওয়া
ভাগ্যের কথা।
ভদ্রলোক : ভদ্র
হইলেও লোক বটে
উনিশ শতকের শেষদিক
থেকে বিশ শতকের প্রথমদিকে বাবুদের মধ্যে থেকে ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা কিছু
দেশোদ্ধারের কাজকর্মে জড়িত থাকতেন। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে আধুনিক
জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত হয়ে বাঙালি মানসে এ সময়কালে একটি জাগরণের ফলে বাবু থেকে
ভদ্রলোকে রূপান্তর এসেছিল। তার কিছু পল ভাল হয়েছিল—কিছু খারাপ হয়েছিল। ১৮৭২ সালে ভদ্রলোক অর্থটি ভদ্র যে
লোক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন হুতুম প্যাঁচার নকশা বইয়ে।
বঙ্কিমচন্দ্র ঠাট্টা
করে এই ইংরেজি জানা শিক্ষিত বাবুর একটি চিত্র এঁকেছেন—চসমা-অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী।
এরা নিজের ভাষাকে ঘৃণা করেন, পরের ভাষায় পারদর্শী।
মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ। এঁরা বিনা উদ্দেশ্য সঞ্চয় করেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করেন, আপার্জনের জন্যে
বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রশ্নপত্র চুরি করেন।
এঁদের বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ এবং কার্যকালে এরা
অদৃশ্য। এঁদের বুদ্ধি বাল্যে বইয়ের পাতায়, যৌবণে বোতলের
মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর আঁচলে। আরও মজা করে বঙ্কিম
লিখেছেন—বাড়িয়ে এরা জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে
গালি খান এবং মুনিব সাহেবের কাছে গলাধাক্কা খান।
সোম প্রকাশ পত্রিকায়
১৮৬২ সালে একটি নিবন্ধে লেখা হয়—ভদ্রলোক, এ ব্যক্তি
আপনার পরিবারকে খাইতে দয় না, বাটী যায় না, যেখানে পায় সেইখানে আহার ও শয়ন করে।
১৮৮৩ সালে সোমপ্রকাশ
লেখে—কৃষিকার্য করা ভদ্রলোকের কর্ম নহে, তাহাতে লোকে চাষা বলিবে।
পর্ব সাত.....
বাংলায় বামুন
আর্যরা ভারতে আসার
অনেক পরে বাংলায় তাদের সংস্কৃতির স্পর্শ পায় অনেক পরে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে
এই দেশকে আর্যরা খুব ভালো চোখে দেখেনি। বাংলা ছিল নিম্নবর্গের মানুষের জায়গা।
দস্যুদের এলাকা। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর বেশিরভাগ সময়েও এদেশে ব্রাহ্মণ্য
আচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণেই তৎকালীন
মহারজ আদিশুর কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়েছিলেন। তারা
বেদবিহিত পূজাঅর্চনা প্রচলন করেন। আধুনিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ এই পঞ্চ
ব্রাহ্মণ। তারা জাতপাতের বিভেদের প্রাচীর তুলে সমাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।
নিম্নবর্গের মানুষ শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নয়—ধর্মব্যবস্থায়ও নতুন
নতুন নিপীড়নের শিকার হয়ে পড়ে।
বাংলায় ইসলাম
পাশাপাশি ত্রয়োদশ
শতাব্দীতে ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ ঘটে। তখন বাংলায় সমাজব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন
ঘটে। কোথাও মুসলমান সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে কোথাওবা বা শাসক সম্প্রদায়ের
ধর্মান্তকরণে প্রদত্ত সুযোগসুবিধার ফলে বা
রাজানুগ্রহ পাওয়ার আকাঙ্খায় বা জাতে উঠার আকাঙ্খায়ও অনেক উচ্চবর্গের হিন্দু
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পাশাপাশি নিম্নবর্গের হিন্দুরা ইসলামের উদার নীতির কারণে
আকৃষ্ট হয়। সে সময়ে দরবেশ-ফকিররাও ক্ষেতের আলে আলে নাচতে নাচতে—গাইতে গাইতে দিগন্তে পিঠ রেখে দেখা দিয়ে আসছেন। ঈশ্বরের কথা—আল্লার কথা তাঁদের গান হয়ে সন্ধ্যার শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে
দীর্ঘকাল ধরে বাংলার আকাশে বাতাসে জনপদে মিশে গেছে। সাধারণ মানুষজন অনেকেই উদার
ইসলাম গ্রহণ করেছে।
জাতের বামুন থেকে
অজাতের পিরালী বামুন
ঘটনাটা পঞ্চদশ
শতাব্দীর। তখন যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণায় এক ঘর জমিদার ছিল। তার পদবী ছিল
গুড়। তবে খাতা পত্রে এই গুড়দের রায়চৌধুরী বলা হত। সেখানকার জমিদার দক্ষিণানাথ
গুড় বা রায়চৌধুরীর চার ছেলে—কামদেব, জয়দেব,
রতিদেব ও শুকদেব। সে সময়ে স্থানীয় এক মোগল শাসক ছিলেন মামুদ
তাহির বা পীর আলি। এই পীর আলীর কৌশলে বা প্রলোভনে পড়ে বা আকৃষ্ট হয়ে কামদেব এবং
জয়দেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে আরও একটি মত পাওয়া যায়-- পীর আলী এই দুইভাইকে
কৌশলে গোমাংস ভক্ষণ করান। এই ঘটনা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন পীর আলী। তখন তাদের
মুসলমান হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাদের ছোটো দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেব
মুসলমান হয়নি। কিন্তু তাদের ভাই মুসলমান হয়েছে শুধু এই কারণে হিন্দুসমাজ তাদেরকে
সমাজচ্যুত করে। তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। তাদের
সঙ্গে কেউ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ছেলেমেয়ে বিয়ে দেওয়াও এই নিষেধাজ্ঞার
অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। এদের নাম হয় পিরালী বামুন বা পিরালী থাক। জাতে ছোটো।
অছ্যুৎ।
অথচ
মহাভারতে উল্লেখ আছে প্রাচীন সমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকলেরই
প্রচুর মাংসাহার করতেন। ভদ্রসমাজেও সুরাপান চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞের বহু
উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। রাজশেখর বসু মহাভারতের ভূমিকায় আরও জানাচ্ছেন, সেকালে অস্পৃশ্যতা কম ছিল—দাসদাসীরাও অন্ন পরিবেশ করত।
কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণতন্ত্র কঠিনভাবে সমাজে কায়েম হয়ে পড়লে হিন্দু সমাজের
এই উদারনীতি অনেকাংশেই পরিত্যাক্ত হয়।
এই সমাজচ্যূতির ফলে
স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিয়েশাদী বন্ধ হয়ে গেলে তারা ভিন্ন কৌশল করেন।
তারা ছেলেমেয়েদের বিয়ের জন্য কৌশল ও প্রলোভনের জাল বিস্তার করেন। সাধারণত তারা
টার্গেট করতেন গরীব ব্রাহ্মণদের। তাদেরকে টাকা পয়সা, জমিজিরেত ও
ঘরজামাই করে মেয়ে গছাতেন। আর ছেলে বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের বাড়ির লোড়ির লোকজনকে
আর্থিকভাবে দাড় করানোর দায়িত্ব নিতেন।
ঘরজামাই থেকে জমিদারি
এ সময়কালেই বর্ধমান
জেলার কুশগ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। তারা কুশগ্রামের নামঅনুসারে কুশারী
পদবী ব্যবহার করতেন। তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সে গ্রামের
জগন্নাথ কুশারী পিঠাভোগ নামের এক স্থানের জমিদার ছিলেন। তাঁর জীবৎকাল ছিল ষোড়শ শতাব্দীর
প্রথম দিকে। তখন মোগল শাসন ছিল।
বর্ধমানের পিঠাভোগের
জগন্নাথ কুশারীকেও এইরকম কোনো একটি কৌশলে পিলারী বামুন শুকদেব গুড় কায়দা করে তার
মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ফলে জগন্নাথ কুশারীকে তার ভাইবেরাদার-আত্মীয়স্বজন
পরিত্যাগ করে। সম্ভবত ছিন্নমূল হয়ে জগন্নাথ কুশারী যশোহরে শ্বশুরবাড়ি চলে আসেন।
এবং ঘরজামাই হয়ে গেলেন। নরেন্দ্রপুরের উত্তরপশ্চিমকোণে উত্তরপাড়া গ্রামের সঙ্গে
সংলগ্ন বারোপাড়া গ্রামে ঘর বাঁধেন। তিনিও পিরালী থাকের অন্তর্ভুক্ত অছ্যুৎ হয়ে
গেলেন। শ্বশুর শুকদেব গুড় তাঁকে উত্তরপাড়া গ্রামটি দান করেন। এই গ্রামের আয়
থেকেই তাঁর সংসার চলে। তাঁর চার ছেলে—প্রিয়ঙ্কর, পুরুষোত্তম,
জগন্নাথ কুশারীই রবীন্দ্রনাথদের ঠাকুরবংশের
আদিপুরুষ।
আজব শহর কোলকেত্তা
আগমন
রবীন্দ্রনাথের
উর্দ্ধতম নবম পুরুষ। তার জীবৎকাল ছিল সপ্তদশ শতাদ্বীর দ্বিতীয়ার্ধে। সে সময়ে জোব
চার্নক কোলকাতা শহর পত্তন করছিল। তার ছেলে মহেশ বা মহেশ্বর যশোরের উত্তরপাড়া থেকে
ভাগ্যান্বেষণে কোলকাতা আসেন। আরেকটি মত আছে মহেশ নয় তার ছেলে পঞ্চানন কুশারী
জ্ঞাতী কলহে ভিটা ত্যাগ করে কোলকাতায় চলে যান। সময়টা প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর
শেষভাগ।
জোব চার্নকের জন্ম
১৬৩০ সালে ইংলন্ডের ল্যাঙ্ক শায়ারে। ১৬৫৬ সালে এক ব্রিটিশ বানিজ্যিক সংস্থায় কাজ
নিয়ে ভারতে আসনে। এর বছর খানেক পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠিতে
বার্ষিক কুড়ি পাউন্ড বেতনে এক কর্মি হিসাবে যোগ দেন। ১৬৮৬ সালে প্রতিভাবলে ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার এজেন্ট নিযুক্ত হন। সে সময়ে সুবেদার শায়েস্তা খাঁর
সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ বাড়ছিল। ঐ বছরের অক্টোবরে জোব চার্নক হুগলির মুগল সুবেদারের
আড়তে গোলাগুলি চালিয়ে আগুণ লাগিয়ে দিলেন। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম মুগলদের
বিরুদ্ধে ইংরেজদের অস্ত্র ধারণ।
জোব চার্নক মুগলদের
ভয়ে তল্পতল্লা গুটিয়ে হুগলি ছেড়ে বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন। সে সময়ে হঠাৎ
করে হুগলীর পূর্ব পাড়ে নির্জন এক গ্রাম তার চোখে পড়ল। ঘাঁটি গাড়লেন সেখানেই।
গ্রামটির নাম সুতানটি। এই সুতানটি গ্রামে এর আগে আর কোনো ইংরেজের পা পড়েনি।
সেখানে ছোটো একটা দুটো খড়ের চালা ঘর তৈরি করে বসবাসের উদ্যোগ নেন। কিন্তু মুগলদের
বিরুদ্ধে আবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সুতানটি ছেড়ে চলে যান।
ইংরেজদের সঙ্গে এই
বিরোধের জেরে মুগলদের রাজকোষে অর্থ আসা বন্ধ হয়ে গেল। এবং শায়েস্তা খাঁ
ব্যক্তিগতভাবেও কিছু ঘুষ পেতেন। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল । ফলে শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের
আবার সুতানটিতে ডেকে আনলেন। কিন্তু আবার গন্ডগোল হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামে চলে যান।
সেখানে সুবিধা করতে না পেরে মাদ্রাজে পলে যেতে হয়।
সে সমযে মুগল সম্রাট
ছিলেন আওরঙ্গজেব। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে পাঠালেন বাংলার সুবেদার করে। সম্রাটের আদেশে
তিনি ইংরেজদের আবার আমন্ত্রণ জানালেন বাংলায় ব্যবসা করার জন্য। ১৬৯০ সালের ২৩
এপ্রিল আওরঙ্গজেব এক আদেশনামায় বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্কের বিনিময়ে ইংরেজদের
বাংলায় বাণিজ্য করবার অনুমতি দিলেন। ১৬৯০ সালের ২৪ জুলাই এক বৃষ্টিমুখর দিনে
জলকাদা মাড়িয়ে জোব চার্নক এসে নামলেন সুতানটির ঘাটে।
পঞ্চদশ শতাব্দীর
শেষভাগে লিখিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে
এই অঞ্চলের একটি প্রামাণ্য ভৌগোলিক বিবরণী পাওয়া যায়। ব্যান্ডেল ও ত্রিবেণীরমধ্যবর্তী স্থানে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ ছিল একটি বিরাট বন্দর। নদীর ভাটিতে একই পাড়ে বেতড় গ্রামটি
ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পথিকেরা কেনাকাটা করত ও দেবী চণ্ডীর পূজা দিত। চিৎপুর ও কলিকাতা গ্রাম
ছিল বেতরের নিকটবর্তী গ্রাম। সেই যুগে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব ছিল না। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বাংলায় পর্তুগিজদের যাতায়াত শুরু হয়।
এই যুগে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম বন্দরদুটি ছিল বাংলার দুটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। পর্তুগিজরা
চট্টগ্রামকে বলত "Porto Grande" বা "মহা
পোতাশ্রয়" ("Great Haven") ও সপ্তগ্রামকে
বলত "Porto Piqueno" বা "ছোটো
পোতাশ্রয়" ("Little Haven")। সেযুগে টালির নালা বা আদিগঙ্গা ছিল সমুদ্রে যাতায়াতের পথ। সমুদ্রগামী বড়ো বড়ো জাহাজগুলি এখন যেখানে
গার্ডেনরিচ, সেই অঞ্চলে নোঙর ফেলত। কেবল মাত্র দেশি ছোটো
নৌকাগুলিই হুগলি নদীর আরো উজানের দিকে চলাচল করত। সম্ভবত,
সরস্বতী নদী ছিল এই সময়কার আরও একটি জলপথ। এই নদী ষোড়শ
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ১৫৮০ সালে হুগলি-চুঁচুড়াতে পর্তুগিজরা একটি নতুন
বন্দর স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রামের দেশীয় বণিকেরা নতুন একটি
বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাঁদের অধিকাংশই হুগলিতে বসতি
স্থাপন করলেন। কিন্তু চারটি বসাক পরিবার ও একটি শেঠ
পরিবার বেতরের বাণিজ্যিক
সমৃদ্ধির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে নদীর পূর্বতীরে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন। ডিহি কলিকাতা গ্রামের উত্তরাংশে বস্ত্রাদি ক্রয়বিক্রয়ের একটি কেন্দ্র
গড়ে ওঠে। ১৫৯৬ সালে আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরিগ্রন্থে এই অঞ্চলটিকে সাতগাঁও পরগনার একটি জেলা হিসেবে উল্লেখ করেন।
পর্তুগিজদের পর এই অঞ্চলে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা পদার্পণ করে।
অবস্থানগত নিরাপত্তার
কারণে জব চার্নক সুতানুটিকে বসতি স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। সেই যুগে
সুতানুটি পশ্চিমে হুগলি নদী এবং পূর্বে ও দক্ষিণে দুর্গম জলাভূমির দ্বারা বেষ্টিত
ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব অংশে প্রহরার প্রয়োজন হত।
সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা
ও গোবিন্দপুর ছিল মুঘল সম্রাটের খাসমহল অর্থাৎ সম্রাটের নিজস্ব জায়গির বা ভূসম্পত্তি। এই অঞ্চলের জমিদারির দায়িত্ব ছিল বড়িশারসাবর্ণ
রায়চৌধুরী পরিবারের উপর। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর জব
চার্নকের উত্তরসূরি তথা জামাতা চার্লস আয়ার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের থেকে এই
তিনটি গ্রামের জমিদারির অধিকার কিনে নেন। এরপরই কলকাতা মহানগর দ্রুত বিকাশ লাভ
করে। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানি নিয়মিত এই অঞ্চলের রাজস্ব মুঘল সম্রাটকে
দিয়ে এসেছিল
কোলকাতা শহরের প্রকৃত
নগরায়ণ আরম্ভ হয় ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর
হাতে বাংলার শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রধান
বানিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে কোলকাতা। বাংলার তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন
এখানে আসতে আরম্ভ করে জীবিকার তাগিদে। গ্রামগুলি মিলেমিশে ক্রমে রূপান্তরিত হয়
কোলকাতা শহরে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ মহেশ্বর বা পঞ্চানন কুশারী এভাবেই এখানে
রুটি রুটির রোজগারে চলে এলেন। তখনো তারা ঠাকুর হননি।
পর্ব আট.....
কুশারী থেকে ঠাকুর :
ঠাকুর থেকে টেগোর
পঞ্চানন কুশারী ভাগ্য
পরিবর্তনের আশায় কোলকাতায় এলেন। সঙ্গে ছোটো ভাই শুকদেব। বসতি স্থাপন করলেন
কোলকাতা গ্রামের দক্ষিণে,
গোবিন্দপুর আদিগঙ্গার ধারে। তখন এখানে জেলেদের বাস ছিল। অছ্যুত
জেলেদের মধ্যে দুভাই ব্রাহ্মণ এসে পড়ায় তারা বেশ খুশী হল। তাদের
পূজাপার্বনের দুশ্চিন্তা কাটল। তাদের বসবাসের বন্দোবস্ত
করে দিল। তাদের পূজাপার্বনের দায়িত্ব পালন করে
দিতেন। দুভাই শিব পূজার জোগাড় যন্ত্র করে তাদের পুরুতঠাকুর হয়ে বসলেন।
এখানে তখন অনেক বিদেশী
জাহাজ আসত। এইসব জাহাজে তারা নানাবিধ মালামাল সরবরাহ করা শুরু করলেন। এভাবে কিছু
টাকা পয়সাও জমে গেল। পঞ্চানন ও শুকদেব গোবিন্দপুরে গঙ্গার ধারে কিছু জমি কিনে
ফেললেন। বসতবাটি আর শিবমন্দির স্থাপন করলেন। জেলেদের দেখাদেখি সাহেবরাও এই
দুইভাইকে ঠাকুর বলে ডাকা শুরু করল। তারা ঠাকুর বলতে পারত না। তারা বলত টেগোর। এই
পঞ্চানন থেকেই কোলকাতার পাথুরীঘাটা, জোঁড়াসাঁকোতে পঞ্চানন ঠাকুরের বংশধারা এবং
চোরাবাগানে শুকদেবের বংশাধারা ঠাকুর পরিবার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।
পঞ্চানন কুশারীর
দুছেলে জয়রাম কুশারী ও রামসন্তোষ কুশারী কিছু কিছু ইংরেজী ও ফারসী শিখেছিলেন।
ভাষার জোরে তারা সহজের বিদেশী বনিকদের নেক নজরে পড়ে গেলেন। এই দুই ভাষা জানার
কারণে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি মালামাল সরবরাহের কাজ পেতে লাগলেন। করিৎকর্মা
পঞ্চাননকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাস্টারের প্রধান সহকারী হিসাবে কাজ দিল।
ইংরেজদের অধীনে
কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর আসার পরে ১৭৪২ সালে এই অঞ্চলে প্রথম জরীপ কাজ
শুরু হয়। কোলকাতার কালেক্টর র্যালফ সেলডন পঞ্চানন ও শুকদেবকে আমিন হিসাবে নিয়োগ
দেয়। এই কাজে দুভাই বেশ বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে
ছিল কোলকাতার আশেপাশের জমি । তিনি দুভাইকে দিয়ে এই জমিগুলোর জরীপ করান। এইভাবে রাজা
কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জয়রাম তার বাড়িতে
রাধাকান্তর বিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্র খুশী হয়ে দেবসেবার জন্য ৩৩ বিঘা জমি
জয়রামকে দান করেন।
বর্গী এলো দেশে
সেসময়ে বাংলায়
প্রতিবছরই মারাঠা বগীর্দের খুব হামলা হত। তারা ঘোড়ায় চড়ে আকস্মিকভাবে আসত।
আক্রমণ করে সব লুটেপুটে কেটে পড়ত। নওয়াবের সেপাইরা তাদের ঘোড়ার পিছনে ছুটে ধরতে
পারত না। তাদের দমন করতে নবাবকে খুব ঝামেলা পোহাতে হত। মানুষের জন্য সেটা ছিল
এক দুর্বিসহ অবস্থা। একটা ছড়া এই মারাঠা বর্গীদের অত্যাচার বিষয়ে মানুষের মুখে
মুখে আজও ফেরে—
খোকা ঘুমালো পাড়া
জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।
বর্গীদের হামলা আর
নওয়াব-জমিদারদের খাজনা-প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্যুদস্ত মানুষের হাহকারের সামাজিক
ইতিহাসটা এই ছড়ায় আছে।
গঙ্গা আর ভাগীরথী নদী
একটা বাঁধা হিসাবে কাজ করত। এটা পাড়ি দিয়ে তাদের অনুপ্রবেশ করারটা অত সহজ ছিল
না। তাই এই দিক দিয়ে তারা খুবই কম আসা যাওয়া করত। ১৭৫১ সালে নবাব ও মারাঠাদের
একটি সন্ধি হয়। তারপর থেকে আর বাংলায় বর্গি আক্রমণ হয়নি। বর্গীদের স্থলপথের
আক্রমণ ঠেকাতে কোলকাতার উত্তর দিকে নালা কাটা হয়।
বর্গিদের আক্রমণের
সময়কালে নবাব খুব প্রতাপশালী ছিলেন। আর ইংরেজরা তখন তাদের ব্যবসা বানিজ্য
সম্প্রসারণে ব্যস্ত। এদের হামলা রুখতে কোলকাতাকে রক্ষা করার জন্য চারিদিকে মারাঠা ডিচ চ্যানেল বা নালা খনন করে ইংরেজরা। মূলত তাদের বানিজ্যের
সম্পদাদি রক্ষা করার জন্যই নবাবের অনুমতি নিয়ে মারাঠা ডিচ তৈরি করেছিল।
কিন্তু বর্গীদের আক্রমণ আশঙ্কা থেমে গেল তখন অবশিষ্ট নালা আর খনন করা হয়নি। উত্তর
কোলকাতার একমাত্র পথটিকে কেটে নালার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। সরাসরি ঘোড়া
নিয়ে কোলকাতায় ঢোকা যেত না। নালাটি পার হওয়ার দরকার হত। নালাটি সাত মাইল লম্বা
করার পরিকল্পনা ছিল। ছয় মাসে মাত্র তিন মাইল কাটা হয়েছিল। এই নালা খননের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা
পয়সা এদেশীয় লোকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল।
১৭৫৬ সালে
সিরাজউদ্দৌলা যখন কোলকাতা আক্রমণ করেছিলেন, তার সঙ্গে ছিল ৩০, ০০০
সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। অধিকাংশ সৈন্যই এই নালাটি পার হয়ে কোলকাতায় প্রবেশ
করেছিল। সেই যুদ্ধে সিরাজউদ্দোলা জয়লাভ করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে
আবর্জনার ভরে উঠেছিল নালাটিটি। এটার কোনো দরকারই ছিল না। ১৭৯৯ সালে এই মারাঠা নালাটি ভরে দেওয়া হয়। ওখানে সার্কুলার রোড তৈরী
করা হয়। এই মারাঠা পনালা খননের কাজটিতে জয়রাম কুশারী একজন ইন্সপেক্টর
হিসাবে কাজ করেছিলেন। ধান সায়রে তিনি জমি কিনে রাতারাতি বসতবাড়ি স্থাপন করেন।
ধানসায়রের বর্তমান কোলকাতার ধর্মতলা।
জয়রাম ঠাকুরের বড়
ছেলে আনন্দীরাম খুব ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে সে সময়ে তার চেয়ে
ভালো ইংরেজি আর কেউ জানতেন। তবে বাবা জয়রামের কোনো অপ্রিয় কাজ করার ফলে
তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। জয়রাম বেঁচে থাকতেই তিনি মারা যান।
নীলমণি ঠাকুর :
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পত্তন
জয়রাম ঠাকুরের মেজো
ছেলে নীলমণি ও সেজো ছেলে দর্পনারায়ণ ধানসায়রের জমি সম্পত্তি বেঁচে দেন। তাদের
বাড়িটি ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের সময় মুর্শিদাবাদের
নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কোলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গে গোলা বর্ষণ করেন, তখন
নীলমণি ঠাকুরদের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তী নবাব মীর
জাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা তাদের নিজেদের জন্য এবং তাদের মিত্রদের জন্য ক্ষতিপুরণ
আদায় করেন। জয়রাম ঠাকুরও সে সময় ১৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ
পান। এই টাকার একটি অংশ দিয়ে কোলকাতা তিনি কোলকাতা গ্রামের পাথুরিয়া ঘাটা
পাড়ায় জমি কিনে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। ইংরেজদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে
জয়রাম ঠাকুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার বা কাগজও কিনেছিলেন। শেয়ার তাদের
গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিইয়ের নামে করেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট কোম্পানী
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। তখন তারা জয়রাম ঠাকুরকে উড়িষ্যার
কালেক্টরের দেওয়ান বা সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। এই কাজে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ
উপার্জন করেন।
জয়রামের তৃতীয়
ছেলে দর্পনারায়ণ হুইলার কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ করেন। সে সময়ে ইংরেজরা জাহাজ
থেকে জলের মধ্য লবণ ফেলে দিত। পরে তুখোড় ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজরা সেই লবণ
ফেলে না দিয়ে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বিক্রি করত। এজন্য স্থানীয় লবণ
শিল্পকে তারা ধ্বংস করে দেয়। এদেশীয়দের বাধ্য করে ইংরেজদের লবণ কিনতে।
দর্পনারায়ণ এই লবণের ব্যবসা শুরু করেন। এখান থেকে তিনি বিস্তর লাভ করতে
থাকেন। তিনি স্থানীয় লবণ বাজারের ইজারাদারী করেন। এ ছাড়াও জমিদারির
পত্তনিদারি ও অন্যান্য ব্যবসা থেকে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের মালিক হন। নীলমণি ঠাকুর
উড়িষ্যা থেকে দেওয়ানী থেকে আয়কৃত টাকা দর্পনারায়ণের কাছে কোলকাতায় পাঠাতে
থাকেন।
এই সময়কালে বাংলায়
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দ্বিতীয় বর্ষে করাল মূর্তি ধারণ করে। না খেতে পেয়ে, রোগে ভুগে
বাংলায় তিনভাগের এক ভাগ মানুষ মারা যায়। একভাগ লোক পালিয়ে বনে জঙ্গলে চলে যায়।
অন্যান্য বছরের তুলনায় এ সমযকালেই বাংলায় রেকর্ড পরিমাণ খাজনা আদায় করে ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানী রেজা খানের পরিচালনায়। এই ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জমিদার
তালুকদার, পত্তনীদাররা খাজনা আদায়ে মুল ভূমিকা পালন করে।
পুরনো জমিদারদের চেয়ে ব্যবসা থেকে আসা নুতন জমিদাররা খাজনা আদায়ে বেশী দক্ষতা
দেখাতে সক্ষম হন। ফলে কোম্পানীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। পুরনো নরম
আলস দুর্বল জমিদারদের অনেকেই খাজনার আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়ে
জমিদারী হারায়। এইসব জমিদারীই এইসব নব্য ব্যবসায়ী ও জমিদাররা কোম্পানীর কাছ থেকে
ইজারা নেন। তারা বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হন। এরা সবাই ছিলেন অনুপস্থিত
জমিদার। তারা নায়েব গোমস্তাদের মাধ্যমেই জমিদারী পরিচালনা করতেন।
নীলমণি ও
দর্পনারায়ণের ছোটো ভাই গোবিন্দরাম নিঃসন্তান ছিলেন। ১৭৭১ সালে তার মৃত্যু হয়।
এই বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ঠাকুর পরিবারে নীলমণি ও দর্পনারায়ণের
সঙ্গে গোবিন্দরামের বিধবা স্ত্রীর এই সময় গৃহবিবাদ শুরু হয়। বিধবা স্ত্রী
রামপ্রিয়া দেবী ১৭৮২ সালে সুপ্রীয় কোর্টে মামলা করেন। এই মামলার ফলে সম্পত্তি
তিনভাগে ভাগে হয়। রামপ্রিয়া রাধাবাজার ও জ্যাকসন ঘাটে দুটি বাড়ি পান। দর্পনারায়ণ
পাথুরিয়া ঘাটের বাড়ি ও অপর গৃহদেবতা রাধাকান্ত জিউর সেবার ভার পান। তার বংশধারা
পাথুরিয়া ঘাটের ঠাকুর বংশ নামে পরিচিত হন। আর নীলমণি তার নিজস্ব উপার্জিত বিপুল
অর্থ, এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণসহ গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শিলার ভার নেন।
জোড়া বাগানের বৈষ্ণব শেঠের কাছ থেকে লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে মেছুয়াবাজার
এলাকায় এক বিঘা জমি কেনেন। সেখানে আটচালা বেঁধে বসবাসকরতে শুরু করেন। মেছুয়া
বাজারের নামই পরে জোড়াসাঁকো হয়। এইভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন
নীলমণি ঠাকুর ১৭৮৪ সালে। নীলমণি ঠাকুর ১৭৯১ সালে মারা যান।
পর্ব নয়...
ঠাকুরবাড়ির জমিদারি
শুরু
নীলমণি ঠাকুরের বড়
ছেলে রামলোচন ঠাকুর প্রখর বিষয়বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি বিরাহিমপুর পরগণা কিনে
জোড়াসাঁকো পরিবারের আনুষ্ঠানিক জমিদারগিরির সূচনা করেন। বিরাহিমপুর পরগণার সদর
কাঁছারি ছিল শিলাইদহে।
তিনি বিপুল বিষয়সম্পত্তি কিনে ঠাকুরপরিবারকে কোলকাতায় অভিজাত
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর আগে ঠাকুর পরিবারের পরিচয় ছিল-- পিরালী ব্রাহ্মণ এবং
ব্যবসায়ী বাবু। তারা পাত্তা পাওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। সমাজে অছ্যুত।
জমিদারি করার সঙ্গে
সঙ্গে পারিবারিক কিছু সৌখিন আভিজাত্য গড়ে তোলেন রামলোচন ঠাকুর। বিকেলে তিনি
হাওয়া খাওয়ার প্রচলন তিনি প্রচলন করেন। এছাড়া খেয়াল বা কালোয়াতি গান ও
কবিয়াওয়ালাদের আসর জোঁড়াসাঁকোর বাড়িতে বসাতেন। সেসব অনুষ্ঠানে ইয়ারবন্ধুদের
আমন্ত্রণ করা শুরু করেন। সেখানে বিস্তর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হত। বিভিন্ন জেলায়
তিনি জমিদারি কেনেন। কোলকাতা শহরে দশটি বাড়ি কিনেছিলেন।
রামলোচন ঠাকুর আর তাই
ভাই রামমণি ঠাকুর দুজনে দুবোনকে বিয়ে করেন। রামলোচনের স্ত্রী অলকা দেবীর
শিবসুন্দরী নামে একটি মেয়ে হলেও শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান
ছিল না। রামমণির স্ত্রী মেনকার গর্ভে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে হয়েছিল। ছেলে দুটির
নাম রাধানাথ (১৭৯০-১৮৩০) ও দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)।. মেয়ে
দুটির নাম জাহ্ণবী ও রাসবিলাসী। সবার ছোটো দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের বয়স এক বছর
পূর্ণ হওয়ার আগেই তার মা মেনকার মৃত্যু হয়। এরপর রামমণি ঠাকুর দুর্গামণি দেবীকে
বিয়ে করেন। দুর্গামণির একটি ছেলে রমানাথ (১৮০০-১৮৭৭) এবং একটি মেয়ে দ্রবময়ীর
জন্ম হয়।
ছোটো বোন মেনকার
মৃত্যুর পরে দুধের শিশু দ্বারকানাথের লালন পালনের ভার তুলে নেন অলকা দেবী। তিনি
তাকে স্তন্যপানও করান। সে সময় অলকাদেবীর পরামর্শে অপুত্রক রামলোচন দ্বারকানাথকে
দত্তক নেন। এই দত্তক নেওয়াটা একই পরিবারের মধ্যে ঘটেছিল। দ্বারকানাথের
বাবা-জ্যাঠা সহোদর দুভাই। মা-মাসি সহোদর দুবোন।
১৮০৭ সালে
ডিসেম্বর মাসে রামলোচন উইল করে দ্বারকানাথকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান।
উইলে লেখা হয়--
এখনও তুমি নাবালক
একারণ এবং এই জমিদারি ওগায়রহ জে কিছু বিসয় তোমাকে দিলাম ইহার কর্ম্মকার্য্য জাবত
আমি বর্ত্তমান থাকিব অর্থাৎ আমিই করিব আমার অবর্ত্তমানে জাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না
হও তাবৎ পরগণাদিগর এ সকল বিষয়রের কর্ম্মকার্য্য ও সহী দস্তখত বা বন্দবস্ত ও
হুকুমহাকাম সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্তবয়স হইলে জমিদারিদিগর আপন নামে
হুজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়া জমিদারির ও সংসারের কর্ম্মকার্য্য ও
জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ওগায়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবা
এবং জাবৎ তোমার মাতা বর্ত্তমান থাকিবেন তাবৎ পরগণার মুনাফা ওগায়রহ জে কিছু আমদানির
তহবিল তোমার নিকট জেমন আমি রাখিতাম তুমিও সেইরূপ রাখিবা।
রামলোচন ঠাকুর এইভাবে
নিজের স্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক কর্ত্রিত্বশক্তির
প্রতি সম্মানও দেখিয়েছেন।
এই উইল করার কয়েকদিন
পরেই রামলোচর ঠাকুর ১৮০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর মারা যান। দ্বারকানাথের বয়স তখন তের।
তিনচার বছর সম্পত্তি দেখাশুনা করেন তার মা অলকা দেবী ও দ্বারকানাথের আপন বড় ভাই
রাধানাথ। এর পরে দ্বারকানাথ নিজেই সব নিজেই পরিচালনা করতে শুরু করেন। তখন তাঁর
বয়স ১৬/১৭ বছর।
দ্বারকানাথ ঠাকুর—বাঙালি প্রিন্স বলিয়া ইংরেজরা আদর করিত
বাল্যকালে প্রথামতো
কিছুদিন দ্বারকানাথ পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। পরে মৌলবীর কাছে ফার্সি ও আরবী ভাষা
শেখেন। সে সময়ে মুগলদের অনুসরণে ফার্সি ভাষা রাজভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। ইংরেজরা
প্রথমদিকে এদেশের শিক্ষা নিয়ে ভাবিত ছিল না। তখন কিছু ইংরেজ ইংরেজি শেখার স্কুল
খুলেছিলেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। কিছু মিশনারীগণও কোম্পানীরকে পাশ কাটিয়ে স্কুল
করেছিলেন। সে রকম একটি স্কুল খুলেছিলেন শেরবোর্ন সাহেব কোলকাতার চিৎপুরে। সেখানে
দ্বারকানাথ ইংরেজি শেখেন। এছাড়াও পরে রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম, ডিজে গর্ডন,
জেমস কলরড প্রমুখের কাছেও ইংরেজি ভাষার তালিম নেন। সেকালে ইংরেজি
ভাষা শেখা ছাড়া বিত্তবৈভব অর্জন করা সম্ভব ছিল না। যারা ধনী হয়েছিলেন তারা
সবাই-ইংরেজির শেখার গুণে ইংরেজদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ধনী হয়েছিলেন। দ্বারকানাথও
এই ঘরাণার উন্নত সংস্করণ। ইংরেজদের দেওয়ান রাজা রামমোহন রায় তাঁর পাইওনিয়ার।
তারা দুজনেই ধনীদের প্রতিনিধি। গরীবপ্রজাদের নয়।
রামলোচন ঠাকুরের
জমিদারি ছিল উড়িষ্যার কটকে ও পূর্ববঙ্গের বিরাহিমপুর মহলে। বছরে এই দুটি মহল থেকে
তাঁর আয় হত তিরিশ হাজার টাকা। দ্বারকানাথ ১৬/১৭ বছরে জমিদারির দায়িত্ব নিয়েই
সন্তুষ্ঠ ছিলেন না। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রতিভাবলে
উপার্জনের নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়ে কলাগাছ থেকে বটগাছ এবং বটগাছ থেকে
তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হয়েছিলেন। সেটা ইতিহাস। এই ইতিহাসের পেছনে কাজ
করেছে তাঁর সহজে আয়ত্ত্বাধীন ইংরেজিভাষা আর বহুমুখী উদ্যোগ।
একটি দলিলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার
বিরাহিমপুরের প্রজারা ‘দুর্বত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল’।. এই জটিলতাপূর্ণ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে দ্বারকানাথ আটঘাট বেঁধে
জমিদারি আইনকানুনগুলো ভালোভাবে শিখে নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি এত কুশলতা অর্জন
করেছিলেন যে অন্যান্য জমিদারগণ তাঁকে জমিদারির নানা সমস্যা নিরসনে ও
আইনকানুন বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ করতেন। পরে সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার
ফার্গুসনের নিকট থেকে তিনি আইন বিষয়ে গভীর পাঠ গ্রহণ করেন। এভাবে স্বাধীন আইন
পরামর্শক হিসাবে তাঁর উপার্জন বেশ ভালো ছিল।
রাজা রামমোহন রায়ের
বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম ও ডিজে গর্ডন বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটস এন্ড
কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। তাদের সহায়তায় দ্বারকানাথ ম্যাকনটস কোম্পানীর গোমস্তা
পদে যোগ দিয়ে রেশম ও নীল কিনতে তাদের সাহায্য করেন। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে
তিনি নিজেও রেশম ও নীল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন।
১৮১৮ সালে
চব্বিশপরগণার কালেক্টর অফিসে সেরেস্তাদার পড়ে তাঁর চাকরী হয়। এই চাকরীটি আগে
রাজা রামমোহন রায়ের সুপারিশে তিনি পান। রামমোহন রায় নিজেও ইংরেজদের সেরেস্তাদার
ছিলেন। দ্বারকানাথ আপন প্রতিভাবলে ১৮২২ সালে ২৪ পরগণা কালেক্টর ও নিমক মহলের
অধ্যক্ষ প্লাইডেনের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮২৮ সালে শুল্ক ও আফিম বোর্ডের দেওয়ান
পদে উন্নীত হন। ভালো আয় করা সত্ত্বেও তিনি ১৮৩৪ সালে কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে
নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন।
১৮২৮ সালে ম্যাকিনটস
কোম্পানীর ইংরেজ বন্ধুরা তাকে কোম্পানীর অংশীদার করে নেয়। এই কোম্পানীর
কমার্শিয়াল ব্যাংকের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পরের বছর ১৮২৯ সালে১৬ লাখ টাকা মূলধন
নিয়ে তিনি ইউনিয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য ব্যবসা দেখার জন্য বাংকের
কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন তার ছোটো ভাই রমানাথকে। ১৮৩০ সালে তিনি কালীগ্রাম ও ১৮৩৪
সালে সাহাজাদপুরের জমিদারী কেনেন।
এই সময় উইলিয়াম কার
নামে এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে কার-ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানীর
সাহায্যে দ্বারকানাথ চীন থেকে রেশম আমদানী করেন। এছাড়া বহুবিধ ব্যবসাবানিজ্যের
মধ্যে অন্যতম হল—ক্যালকাটা স্টিম টাগ
অ্যাসোসিয়েশন, দ ফ্লোটিং ব্রিজ প্রজেক্ট, দ বেঙ্গল বন্ডেড
ওয়্যারহাউজ অ্যাসোসিয়েশন, দ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানী,
দ বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী, দ স্টিম ফেরি
ব্রিজ কোম্পানী, দ বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েশন, দ বেক্ষল কোল কোম্পানী, এবং ইন্ডিয়া জেনারেল
নেভিগেশন কোম্পানী। রেললাইন বানিয়ে রেল কোম্পানীরও পত্তন করার চেষ্টা করেছিলেন
তিনি। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে থামিয়ে দেয়। কার এন্ড টেগর কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়।
ইউনিয়ন ব্যাংকেরও পতন ঘটে।
১৮৩৩ সালে ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ হারায়। তার কিছু সুবিধা ভোগ করেন
দ্বারকানাথ। তার জমিদারি বিরাহিমপুরের কুমারখালি মৌজায় অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানীর রেশম কুঠিটি কিনে নেন। স্থাপন করেন রামনগরে চিনির কারখানা, রানীগঞ্জে খনি
থেকে কয়লা তোলার বেঙ্গল কোল কোম্পানী। আসামের চা প্রথম আমদানি করেন। এ ছাড়া কার
এন্ড টেগোর কোম্পানীর প্রধান ব্যবসা নীলের চাষ ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে
তাদের নীলের কুঠি ছিল। এই নীল ব্যবসাটিই ছিল সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত কারবার। তাদের
অফিসকে লোকে নীলের বাজার বলে চিনত। এই ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য তিনি
ইংরেজদের নিয়োগ দিতেন। স্থানীয় বাঙ্গালীরা ইংরেজদের ভয় পেত। ফলে তাদের ব্যবসা
চলেছে ইস্ট ইস্টিয়া কোম্পানীর স্টাইলেই। কোনো কোনো ব্যবসা-বানিজ্য আইনসংগত বা
ন্যায়সংগত ছিল বলে মনে করেননি গবেষকগণ। তাঁদের কিছু সন্দেহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর হয়তো এই কারণে দ্বারকানাথ সম্বন্ধীয় দলিলপত্রাদি পুড়িয়ে ফেলেন। তাই
দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সঠিক অনুসন্ধান করার সুযোগ নেই বলে
জানিয়েছেন জীবনীকার ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জমিদারদের শক্তিকে
সংহত করতে এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করার জন্য ১৮৩৮ সালে
জমিদার-সভা বা ল্যান্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন স্থাপন করা হয়। তিনি এর অন্যতম
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু করেছেন কিনা তেমন কোনো
তথ্য জানা যায় না।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে লিখেছেন, অনেকগুলি ঘটনা তাঁহার উপার্জনের সহায়
হইয়াছিল। প্রথমত তিনি নিজে পৈতৃক জমিদারির অধিকারী ছিলেন, তাহা হইতে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক ষাট হাজার টাকা আয় হত। সে সময়ে
তাহার খরচ পরিবার হিসাবে ধরিলে বাৎসরিক দুই-তিন হাজারের অধিক হইবে না। আমরা
তৎস্থানে দশ হাজার ধরিলেও বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়া সঞ্চিত হইবার
অবসর ছিল। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে দেখি যে প্রতি দশ বছরে তাহার পাঁচ লক্ষ টাকা
জমিত।
দ্বারকানাথ তখনকার
দিনে ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীই শুধু নয়—প্রভুত সমাজিক সম্মান ও
প্রতিপত্তি লাভ করেন। নিজে ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। তিনি নিজে প্রথম প্রথম
মদ্য-মাংস খেতেন না। নিরামিষ খেতেন।
দ্বারকানাথে পত্নী
দিগম্বরী দেবী খুবই ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামীর নিরামিষ বাদ দিয়ে মদ্য-মাংস
খাওয়ার এই নবলদ্ধ আভ্যাসকে পছন্দ করেননি। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে
এই পথ থেকে ফেরাতে। কিন্তু তাঁর স্বামী ফেরেননি দেখে, রীতিমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের
ডেকে মতামত চেয়েছিলেন ম্লেচ্ছ সংসর্গে পানভোজনে মত্ত স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা
ধর্মসংগত হবে কিনা। স্বামীসেবা অবশ্য কর্তব্য বলে রায় দিলেও তাঁকে স্বামীর সংগে
এক সঙ্গে থাকতে তারা নিষেধ করেন। ফলে দিগম্বরী দেবী স্বামীর দেখভাল করলেও
সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। শোনা যায়, যতবার
দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি কথা বলতে বাধ্য হতেন—ততবারই তাঁকে সাতঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করতে হত। এভাবে ঠাণ্ডা লেগে
অসুস্থ হয়ে মারা যান দিগম্বরী দেবী।
স্ত্রীর আপত্তির ফলে
দ্বারকানাথ বসতবাটির পরিবর্তে বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাড়ি কিনে বহুমূল্য
আসবাবপত্রে সজ্জিত করে সেখানে তাঁর ভোজসভা ও নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন করতেন। এইসব
আয়োজনে সে সমযে ইংরেজ সাহেবরা নিমন্ত্রণ পেলে কৃতার্থ বোধ করত।
সে সময়ের একটি
সংবাদপত্রে কাগজে হেডলাইন প্রকাশিত হয়েছিল—
শ্রীযুত বা্বু
দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাশা।–গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম
উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবরনল জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও
বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষত: নৃত্যগীত, বাদ্য ও বহ্ণুৎসবজনক
ও অত্যুৎকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল।...অনন্তর মহানাচ শুরু হইল।
কোলকাতায় সে সময়
একটি গান জনপ্রিয় হয়েছিল—
বেলগাছিয়ার বাগানে
হয়
ছুরি-কাটার ঝনঝনানি,
খানা খাওয়ার কত মজা
আমরা তার কি জানি?
জানে ঠাকুর কোম্পানি।।
একটা বর্ণনা পাওয়া
যায় ফেনী পার্কসের বিবরণে, সময়টা ১৮২৩ সালে—দূর্গাপূজায় :
পূজা মণ্ডপের পাশের
একটা ঘরে নানা রকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর
ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক ‘মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার’ সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ এবং ফরাসি মদ্যও ছিল প্রচুর।
মণ্ডপের অন্য দিকে বড় একটা হল ঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজিদের নাচগান
হচ্ছিল, এবং ইউরোপীয় ও এদেশী
ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরাসহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।
হান্টার সাহেব লিখেছেন—এইসব নাচ দেখে দূর থেকে এ দেশের
গ্রামের লোকেরা অবাক হত। তাদের এখানে যোগদানের কোনো সুযোগ ছিল না। দূর থেকে দেখা
যেত কিছু হিছু দৃশ্য আর শোনা যেত বাদ্য আর গানের সুর।
জানা যায় মেম
পটানোতেও দ্বারকানাথ খুব ওস্তাদ ছিলেন। অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে পছন্দের যে কোনও
লেডিকে তিনি কাছে টানতে সমর্থ। বিখ্যাত অভিনেত্রী ইসথার লিচ-এর সঙ্গে তাঁর গভীর
বন্ধুত্বের কাহিনী সেকালে সবাই জানতেন। তিনি এবং তাঁর ষোড়শী কন্যাকে দ্বারকানাথ
কেমন করে নিজের নাগালে রেখেছিলেন সেটাও ছিল সেকালের অন্যতম মুখরোচক কাহিনি। মিস
হার্ব নামে এক লেডি দ্বারকানাথকে লিখেছেন,--‘বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে একবার
তোমার সঙ্গে বসে খেতে চাই’।. চিঠির
শেষ বাক্যে লেখা আছে-‘বিলিভ মি অলওয়েজ অ্যান্ড এভার টু
বি ইওর সিনসিয়ার অ্যান্ড আই ডে সে নট ফারদার।...।. বিলেতে
দ্বারকানাথ গেলে সেখানেও তিনি বিস্তর মেম সাহেবদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছিলেন। তার
অন্যতম বান্ধবী
ছিলেন সুরসিকা ইংরেজ কবি এবং রূপসী ক্যারোলিন নর্টন। সবে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি
হয়েছে তাঁর। শহরে তাঁর বিষয়ে নানা গুঞ্জন। দ্বারকানাথের জন্য তিনি আয়োজন
করেছিলেন কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে স্মরণীয় নৌ-পার্টির। সেই আসরে হাজির ছিলেন
স্বয়ং চার্লস ডিকেন্স। ব্লেয়ার বি ক্লিং লিখছেন—দ্বারকানাথ এসব
ব্যাপারে ঢাকাঢাকি পছন্দ করতেন না।সর্ববিষয়েই তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ভারতিয়দের
পার্টনারশিপ চাই। নারী বাদ যাবে কেন।
এসবই ছিল সাহেব ধরার
কায়দা কৌশল। পয়সাকড়ি কামানোর নিত্যনতুন ফন্দি।
পর্ব দশ...
রামমোহন রায় : ঠাকুরদের
বদলে দেওয়ার মানুষ
রাজা রামমোহন রায়ের
সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় ঘটে ১৮১৫ সালে। এই পরিচয় ঠাকুরপরিবারের জন্য
একটি বদলে যাওয়ার ঘটনা।
১৭৭২ সালে রামমোহন
রায় হুগলীর এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা পারিবারিক
প্রথাঅনুযায়ী ছেলেকে সংস্কৃত শিক্ষাটা খুব ভালো ভাবে দেন। তবে তিনি জানতেন—সংস্কৃত শিক্ষা পণ্ডিতের উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু
জীবিকার জন্য সেটা লাভজনক নয়। জীবিকার জন্য তাকে পাঠানো হল পাটনায়। সেখানে ভালো
করে আয়ত্ব করেছেন ফার্সি ও আরবী ভাষা। এদুটো ভাষা তখনকার রাজভাষা। এ দুটো ভাষা
ছাড়া বিত্ত অর্জন অসম্ভব।
সে সময় সবে কোম্পানীর
শাসন চলছে। দেশে জীবনবিনাশী সত্তরের মন্বন্তর শুরু হয়েছে। দেশে মানুষ মরে-ছেড়ে
যাচ্ছে। সন্নাসী-ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। বাংলায় সংসারবিহীন হিন্দুকে
সন্নাসী বলে। আর সংসারবিহীন মুসলমানকে ফকির বলে। সুবা বাংলার ভাগলপুর-পূর্ণিয়া
থেকে শুরু করে রংপুর-বগুড়া পর্যন্ত এই সন্নাসী-ফকিরদের আন্দোলন হয়।
হেস্টিংস এদেরকে ‘the gypsies of Hindustan’, বঙ্কিমচন্দ্র ডাকাইত
আর যামিনীমোহন গাঙ্গুলি Raiders বলেছেন। প্রাবন্ধিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলেছেন, আকাশেবাতাসে
তখন মন্বন্তরের হাহাকার, অন্যদিকে খাজনা আদায়কারীদের
হুঙ্কার এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছে সন্নাসী-ফকিরদের ইংরেজ
কোম্পানী ও বাহিনীর বিরুদ্ধে রণধ্বনি। সেই সময়টাতে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
চোয়াড় বিদ্রোহ, বাঁকুড়ার প্রজা
বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সন্নাসী-ফকির বিদ্রোহ ইত্যাদি একের পর এক ফেটে
পড়েছিল। সুবে বাংলা তখন নরক। সন্নাসী-ফকির বিদ্রোহের নেতার নাম মজনু শাহ।
রামমোহন পরবর্তীতে যখন জন ডিগবির দেওয়ান হিসবে রংপুরে কাজ করেছেন—তখন তিনি প্রায়ই রংপুর থেকে তিন মাইল দূরে ফুলচৌকির রংমহলে আসতেন।
মজনু শাহের অনুসারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন।
সুফিবাদ--
পাটনার পড়াশুনা করার
সময়ে রামমোহন জীবিকার
ভাষা শিখতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পান।
পরিচিতি হলেন সুফি সাধক ও যুক্তিবাদি মুতাজিলদের চিন্তাধারার সঙ্গে। সুফিরা
মনে করেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনো ফারাক নেই—তারা অভেদ। মানুষই সরাসরিভাবেই ব্যক্তিগতভাবে অদ্বৈতবাদের সাধনার
মাধ্যমে স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সুফিরা এই স্রষ্টাকে বললেন তওহীদ।
রক্ষণশীল মুসলমানরা
বিশ্বাস করেন, মানুষের কর্ম-অকর্ম, এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপ,
সমস্তই সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর ইচ্ছায় সংগঠিত হয়। কি হবে না
হবে, কে কি করবে না করবে—সবই পূর্ব নির্ধারিত। আল্লাহ সব ঠিক করে রেখেছেন। আল কোরআন চিরন্তন
গ্রন্থ। কোনো মানুষ কর্তৃক রচিত হয়নি। এটা ঐশী গ্রন্থ। অভ্রান্ত।
মুতাজিলাবাদ--
মুতাজিলারা ছিলেন
গ্রীক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। তারা বললেন, মানুষের জন্য কুকর্ম বরাদ্দ করে সৃষ্টিকর্তা
আবার তারই জন্য মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্তা স্বাধীন চিন্তা ও
কর্মের অধিকার দিয়েছেন মানুষকে। নিজের স্বাধীনতাঅনুসারে ভালো কাজ বা মন্দ কাজ
করার যে কোনোটাই সে বেছে নিতে পারে। সুতরাং মানুষের দোষগুণ বলে কোনো ব্যাপার থাকতে
পারে না। মুতাজিলারা বললেন, একমাত্র ঈশ্বরই চিরন্তন । তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি
করেছেন। সুফি ও মুতাজিলাদের চিন্তাধারাটা বে-শরা বা শাস্ত্রবহির্ভূত। রামমোহন
দেখলেন, সুফিদের চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার একটা মিল
পাওয়া যায়।
রামমোহনের
ধর্মঅভিযান--
রামমোহন ভারতীয় দর্শন, সুফিবাদ ও
মুতাজিলদের চিন্তাধারা থেকে সিদ্ধান্তে এলেন, ঈশ্বর এক ও
নিরাকার। তিনি সর্বত্র আছেন। ঈশ্বর এক বলে তাঁর সৃষ্টিও এক। মানুষ, স্রষ্টা ও মানবসমাজও এক। কোনো ভেদ নেই। মানুষ স্রষ্টার দেওয়ার অধিকার
ভোগ করে। চিন্তায় ও কর্মে মানুষ স্বাধীন। মানুষ কোন কাজটি করবে তার জন্য ঈশ্বরের
কাছে জবাবদিহিতা করার দরকার নেই। রামমোহনের এই চিন্তা লোকাচারবিরোধি। ফলে গোঁড়া
হিন্দু ব্রাহ্মণ বাবা ছেলের উপর ক্ষেপে গেলেন। তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।
এরপর রামমোহন কিছুকাল
দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ালেন। সে সময়ে বৌদ্ধ অধ্যূষিত হিমালয় অঞ্চল পর্যন্ত
গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাধনায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই দেশ ভ্রমণের
সময়ে তিনি খুব গভীরভাবে খুব কাছ থেকে দেশের সাধারণ মানুষ ও তাঁদের জীবনযাত্র
দেখার সুযোগ পান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক পত্রে জানা যায় ইংরেজ
শাসিত দেশে জনসাধারণের দুর্দশা ও দুরবস্থা দেখে সে
সময় তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে প্রবল বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন তিনি।
এরপরে বারাণসীতে
সংস্কৃত শিক্ষা করতে চলে যান। এখান থেকে সনাতন হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রের আদি তথা
মূল রূপ, উচ্চ ও শুদ্ধ সার জানার চেষ্টা করেন।
তিনি জীবনের এই
পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন একই সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর সাধনা করবেন। তাঁর ভাবনাকে
প্রকাশিত করতে গেলে রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হবে। তাঁকে
প্রতিরোধ করতে হলে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হতে হবে। তিনি ১৮০৩ সালে মার্চ মাসে
ফরিদপুরের কালেক্টর টমাস উডফোর্ডের অধীনে দেওয়ান পদে দুমাসের জন্য চাকরি নিলেন।
প্রায় বছর খানেক পরে রামমোহন আবার মুর্শিদাবাদে উডফোর্ডের অধীনে কাজ করলেন। এরপর
তিনি চাকরি নিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কোম্পানীতে। ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করতে
করতে ইংরেজি ভাষাটা শিখে নিলেন খুব ভালোভাবে। ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যা
চিন্তাভাবনাও আয়ত্ত করে নিলেন।
বই লেখা--
তিনি প্রথম লিখলেন
একটি পুস্তিকা। নাম তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদদিন। অর্থ একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।
বইটির ভূমিকা আরবিতে লিখেছেন। মূল লেখা ফার্সিতে। নিজের পয়সায় প্রকাশ করে
বিতরণ করলেন। দ্বিতীয় বই লিখলেন মনজারৎ-উল-আদিয়ান বা বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা।
বেদান্ত, লোকাচারসিদ্ধ হিন্দুধর্ম, বা-শরা বা
শাস্ত্রীয় ইসলাম, সুফীবাদ বা বে-শরা ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে একটি তুলনামুলক আলোচনা করেছেন এই বইতে।
তিনি এ সময়ে খুঁজছেন ভারতে প্রচলিত ধর্মসমূহের সঙ্গে সারাবিশ্বের ধর্মেরসমূহের
একটি যোগসূত্র।
১৮০৫ সালে তৃতীয়বার
রামমোহন চাকরি নিলেন কোম্পানীতে। কর্মস্থল রাঁচিতে। জেলা আদালতের নিবন্ধক ও জেলা
শাসকের সহকারী জন ডিগবির অধীনে কাজ করতে করতে প্রচুর ইউরোপীয়
জ্ঞানবিজ্ঞানের বই-পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেলেন। ১৮১৫ সালে তিনি ভুটানে যান
কোম্পানীর দূত হিসাবে। ডিগবি লিখেছেন, ফরাসি বিপ্লবের কাহিনী রামমোহনের বিশেষ প্রিয়
ছিল এবং এই বিপ্লবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য থেকে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
প্রথম যৌবন থেকেই তিনি
তেজারতি বা সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসার শুরু করেন। তার এই ব্যবসায়ের
পার্টনার ছিলেন অ্যান্ডরু র্যামজে, টমাস উডফোর্ড
প্রমুখ।এই ইংরেজরা কোম্পানীতে চাকরী করতেন। সে সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী
ছাড়া আর কেউ ব্যবসা বানিজ্য করতে পারবে না। রামমোহনের অংশীদারটি গোপনে এই
তেজারতির কারবারটি করতেন। সুদের টাকা দিতেন মূলত ইংরেজ ব্যবসায়ীদেরকেই।
রামমোহন এই কারবারের সঙ্গে ধীরে ধীরে গোবিন্দপুর, রামেশ্বর, বীরলুক, শ্রীরামপুর
ও কৃষ্ণনগর তালুকগুলি কেনেন। এই তালুক থেকে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল এগার হাজার টাকা।
এইভাবে জ্ঞানী রামমোহন সেকালে বিত্তবান হয়েছিলেন।
১৮১২ সালের আগে থেকেই রামমোহন
কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস না করলেও আন্তর্জাতিকভাবে তার ভাবনা
বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। ১৮১২ সালে স্পেনের প্রগতিশীল লোকেরা একটি বিকল্প
সংবিধান প্রণয়ন করেন। সেটি তারা উৎসর্গ করেন রামমোহন রায়ের নামে। শুধু ইউরোপ নয়
আমেরিকার ভাবুকরাও তার ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।
১৮১৪ সালে রামমোহন
রায় রংপুর থেকে এসে কোলাকাতায় বসবাস করতে শুরু করেছেন। তখন তিনি আত্মীয়সভা
স্থাপন করেছেন। আত্মীয় সভার বৈঠক বসত তাঁর মানিকতলার বাগান-বাড়িতে। পাথুরিয়াঘাটার
প্রসন্নকুমার ঠাকুর,
টাকীর কালীনাথ ঠাকুর ও বৈকুণ্ঠনাথ মুনশি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, বিচারপতি
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ বৈদ্যনাথ মুখেপাধ্যায়, ভূকৈলাসের
কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলেনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু
প্রমুখ আত্মীয়সভায় নিয়মিত যেতেন। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ সেখানে যেতে শুরু
করেছেন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের মধ্যে। সেখানে ধর্ম, দেশের পরিস্থিতি, শিক্ষা ও বিভিন্ন সমস্যা
নিয়ে আলোচনা হত।
বদলে দেওয়ার ভাবনা--
সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন—সে সময়ে রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত দেশী ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে
কথা বলা শুরু করেছেন। শুরু করলেন ধর্মসংস্কারের আন্দোলন। ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের
প্রভাবে তিনি একেশ্বরবাদের প্রচারে নেমে পড়লেন। দ্বিতীয় কাজটি করলেন—সমাজসংস্কারণ আন্দোলন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন। তৃতীয়
কাজটি করলেন, দেশীয় আইন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে। মেয়েদের জন্য পৈত্রিক
সম্পত্তিতে অংশ দাবী করলেন। অতঃপর তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের কাছে তিনি দেশবাসীর
জন্য দাবি করলেন প্রকৃত আধুনিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে অই শিক্ষার সংজ্ঞা ও পাঠক্রমও
তিনি দিয়ে দিলেন।
হিন্দু কলেজ :
পরিবর্তনের সুতিকাগার--
১৮১৭ সালে ২০
জানুয়ারী কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী এই কলেজ প্রতিষ্ঠায়
কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি। কোলকাতার ধনী বাবুরা অর্থ সাহায্য দিয়ে কলেজটি স্থাপন
করেন। রামমোহন কলেজের উদ্যোক্তা হলেও তৎকালীন গোড়া হিন্দুরা তার ভাবনাকে পছন্দ
করত না। তিনি থাকলে এই উদ্যোগ ভেস্তে যেতে পারে আশঙ্কায় তিনি
নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়। নামে হিন্দু কলেজ হলেও সেখানে
বাংলা ভাষার কোনো স্থান ছিল না। সেখানে পড়ানো হত ইংরেজি, ফার্সি, আরবি ইত্যাদি। ছাত্ররা ইংরেজী
ভাষা জানলেও বাংলাতে খুবই দুর্বল ছিলেন। জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের প্রস্তাবে ১৮৫৩
সালে সেখানে একজন বাংলার অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। । হিন্দু কলেজের
ছাত্ররা যুক্তিবাদ, উদারনৈতিকতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পাঠও
নিয়েছিল তখন।
হিন্দু কলেজে মিশ্র
পর্তুগীজ বংশোদ্ভুত শিক্ষক ডিরোজরিওর ছাত্ররা যুক্তির আলোকে ধর্মকে দেখার প্রয়াস
পেয়েছিলেন। কোনো কিছুকেই আপ্তবাক্য হিসাবে গ্রহণ না করে প্রত্যেকটি বিষয়
সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আদর্শ
তাঁর কাছ থেকে ছাত্ররা শিখেছিলেন। এই কলেজের ছাত্ররাই পরবর্তী সময়ে উনিশ শতকের
রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরণের নায়ক। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পনেরো বছরের মধ্যেই এই
ছাত্ররা তাঁদের পোষাক আশাক, খাবার অভ্যাস, বক্তব্য
এবং জীবনযাত্রা দিয়ে রক্ষণশীলতার উপর প্রবরভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। শুরুতে
কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কলেজে প্রবেশাধিকার থাকলেও ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজটি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে
দেওয়া হয়। ১৮৫৫ সালে নাম পাল্টে প্রেসিডেন্সি রাখা হয়।
পর্ব এগার...
জমিদারীর সঙ্গে
আসমানদারীর সূত্রপাত
রামমোহনের অনুরোধে দ্বারকানাথ
ঠাকুর বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলে
ভর্তি করে দিলেন। সেখানে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত পড়েছেন। হিন্দু কলেজে ১৮৩১ সালে ভর্তি
হন। ৩/৪বছর পড়াশুনাও করেন। তাঁর ভর্তি হওয়ার পরে ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ ডিরোজিও
পদত্যাগ করে চলে গেছেন। তার ক্লাশ দেবেন্দ্রনাথের করা হয়নি। কিন্তু তাঁর
শিষ্য ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সেখানে সর্বতত্ত্বদীপিকা নামে একটি সভা
স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। সভার নিয়ম করা হয়েছিল—বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোনো কথোপকথন হইবেক না। সে-সময়ের হিন্দু
কলেজের শিক্ষিত নব্য যুবকেরা ইংরেজি শিক্ষায় মেতে দেশি
ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা শুরু করেছিলেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ সে ধারার
বিরুদ্ধে বাংলা চর্চাকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন।
রামমোহনের প্রভাবে এ সভায় ধর্মবিষয়ক আলোচনাও অন্যতম লক্ষ্য হয়েছিল। সেখানে
একেশ্বরবাদ, হিন্দু, ইসলাম,
খ্রীস্টান, বৌদ্ধসহ সকল ধর্ম নিয়েই
আলোচনা হত। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকত।
১৮৩৪ সালে হিন্দু কলেজ
থেকে ছাড়িয়ে এনে দ্বারকানাথ ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে ইউনিয়ন ব্যাংকে শিক্ষানবিশ
কোষাধ্যক্ষ্ হিসাবে নিযুক্ত করেন। এ সময় দ্বারকানাথ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য
নানাবিধ নৃত্য-গীত-ভোজসভার আয়োজন করতেন। দেবেন্দ্রনাথ এই পরিবেশে বিলাস ব্যাসনের
স্রোতে ভেসে যান।
১৮৩৮ সালে তাঁর
ঠাকুরমা মারা যাওয়ার পরে তাঁর মনে বিচিত্রভাবের উদয় হয়। তিনি রাতারাতি পাল্টে
যান। গভীর তত্ত্বজ্ঞান জানার বাসনা জাগে। তিনি মহাভারত, ইউরোপীয়
দর্শনশাস্ত্র প্রচুর পড়েন। ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক পড়ে তার উপনিষদে ভক্তি জন্মে।
শ্লোকটি--
ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম।।
অর্থ : পরিবর্তনশীল এই
জগতে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। তথাপি সবকিছু পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত। ত্যাগ
অনুশীলন কর এবং সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। অপরের ধনে লোভ
করো না। তিনি যা দিয়েছেন তাকে ভোগ করতে হবে।।
বহুচেষ্টায় পণ্ডিতদের
সাহায্য নিয়ে তিনি এই শ্লোকটির অর্থ বুঝলেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানই তিনি করে
ফিরছিলেন। তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে নিয়মিত উপনিষদ অধ্যায়ন করলেন।
সমধর্মি বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। প্রথমে নিজের বাড়িতে—পরে সুকিয়া স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করে সভার কাজ করেন। তার
পিতা গভীরভাবে ধর্মলোকের চেয়ে ব্যবসালোকে বিচরণ করাটাকেই পছন্দ করতেন। আগে ব্যবসা—তারপর ধর্ম। রামমোহনের কাজেকর্মে তিনি সহায়তা করতেন বটে—কিন্তু তার হিন্দুধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তিনি প্রতিদিন
শাস্ত্রমেনে চলতেন। পূজার্চনা করতেন। ইংলণ্ডে সকালে এই পূজায় ব্যস্ত থাকার সময়ে
রানীর প্রতিনিধি এলেও তাকে বসিয়ে রাখতেন। পূজা শেষে শেষে তার সঙ্গে দেখা করতেন।
এই পূজাটা ছিল তার ব্যবসার জন্য বৃদ্ধির জন্য আরাধনা।
কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ
ঠিক উল্টোপথ বেঁছে নিলেন। তিনি বেছে নিলেন জ্ঞানসাধনার ধর্মপথ। তিনি
উপনিষদের লোকাচারকে প্রশ্ন করে বসলেন রামমোহনের মতো। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে
প্রস্তুত হলেন। কিন্তু পিতাকে অসম্মান করতে চাইলেন না। পিতার প্রত্যক্ষ নজর এড়াতে
তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে যন্ত্রালয়ে গিয়ে পড়েছেন। একারণেই তিনি নিজের
বাড়ি ছেড়ে আলাদা বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা সরিয়ে নিয়েছেন। এখানে তিনি
বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।
রামমোহন রায় ইংলন্ড
চলে গেলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা নিয়ে লুপ্তপ্রায় আত্মীয়সভায় যোগ
দিলেন ১৮৪২ সালে। সভাতে ধর্মালোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন। এছাড়া
তত্ত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের কাজটাও করা শুরু করে তাঁর নেতৃত্বে।
এ সময় দ্বারকানাথ
বিলেত চলে গেলেন। তখন দ্বারকানাথের জমিদারী আর ব্যবসাবানিজ্য সব কিছুর দ্বায়িত্ব
পড়েছে দেবেন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু এসবে বদলে তার উৎসাহ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে।
১৮৪৩ সালে বছর খানেক ইংলন্ডে কাটিয়ে দ্বারকানাথ কোলকাতায় ফিরে এলেন। এসে দেখলেন
দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ রীতিমত বিখ্যাত
হয়ে গেছেন। এই বছর ২১ ডিসেম্বর ২০ জন সঙ্গীসহ আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মে
দিক্ষা গ্রহণ করেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তারা দীক্ষাগ্রহণের
পরপরই বিস্কুট ও সেরী এনে খান। এগুলো হিন্দুরা তখন খেত না। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—জাতিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও
মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহনের সময় হইতে আমাদের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল।
দ্বারকানাথের
জীবিতাকালে এইসব কাজকর্মের খরচাপাতি যোগাড় করার একটি কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
তখন পরগণা থেকে টাকা
আসত কলসীতে করে। কলসীতে করে টাকা এলে পর সে টাকা তোড়া বাঁধা হত।... এখন এই যে
আমার নিচের তলার সিঁড়ির কাছে যেখানে ঘড়িটা আছে, সেখানে মস্ত পাথরের টেবিলে সেই
টাকা ভাগ করে তোঁড়া বাঁধা হত।...কর্তদাদামশায় তখন বাড়ির বড়ো ছেলে। মহা সৌখিন
তিনি তখন।..এবাড়ি থেকে রোজ সকালে একবার করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পেন্নাম করতে
আসতেন---তখনকার দস্তুরই ছিল এই।...
কর্তামশায়কে তো বাপকে
পেন্নাম করে ফিরে আসছেন। সেই ঘরে, যেখানে দেওয়ানজি ও আর কর্মচারীরা মিলে টাকার
তোড়া ভাগ করছিলেন, সেখানে এসে হরকরাকে হুকুম দিলেন—হরকরা তো দুহাতে দুটো তোড়া নিয়ে চলল বাবুর পিছুর পিছু।
দেওযানজিরা কী বলবেন—বাড়ির বড়ো ছেলে, চুপ করে
তাকিয়ে দেখলেন। এখন হিসেব মেলাতে হবে—দ্বারকানাথ নিজেই সব
হিসবে নিতেন তোঅ দুটো তোড়া কম। কী হল।
আজ্ঞে বড়োবাবু—
ও, আচ্ছা—
কিন্তু দ্বারকানাথ
ছেলের এই ধর্মকাজে বিরক্ত হয়েছিলেন। ধারণা করেছিলেন তত্ত্বানুসন্ধানী ছেলে সম্পদ
রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। ফলে তিনি একটি ট্রাস্টডীড করে পৈতিক ও স্বোপার্জিত
কযেকটি জমিদারি তার অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এটা এমন এক ব্যবস্থা করা হল—যাতে তার ব্যবসাবানিজ্যের পতন ঘটলেও এই সম্পত্তি রক্ষা পাবে।
ট্রাস্টিবোর্ড তার রক্ষা করবে। এর ফলে দ্বারকানাথ অর্জিত বিত্তবৈভব শেষ হতে তাঁর
মৃত্যুর পরে আরও তিন পুরুষ লেগেছিল।
দ্বিতীয়বার ইংলন্ডে
যাওয়ার পর ১৮৪৬ সালের ২২ শে একটি পত্রে ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে ভৎর্সনা করেছিলেন।
দেবেন্দ্রনাথের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাল্যকথায় এই পত্রটির বাংলাঅনুবাদ
করেছেন--
আমার সকল
বিষয়াসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের
সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয়
রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার
প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার
আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লন্ডন পরিত্যাগ
করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।...
এইপত্র পেয়ে
দেবেন্দ্রনাথ কিছুটা বিমর্ষ হয়েছিলেন। কিন্তু থামেননি। তিনি সে সমযই দেবেন্দ্রনাথ
সপরিবারে নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। এর ঠিক এক মাস পরে দ্বারকানাথ ইংলন্ডে মারা
যান। বড় ছেলে হিসাবে শ্রাদ্ধ করার দ্বায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথের। তিনি বাবার
শ্রাদ্ধ হিন্দু ধর্মানুসারে করলেন না। আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা নিজ বিশ্বাস
মত কয়েকটিমাত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বরচিত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতিক্রমে এক
গৃহে শ্রাদ্ধ করিলেন। সে স্থলে গঙ্গাজল তুলসী কুশ বা নারায়ণশিলা ছিল না। এ কারণে
দেবেন্দ্রনাথকে বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করলেন। এটা ছিল একটা বড়ো বিদ্রোহ।
দ্বারকানাথের মৃত্যুর
পরে ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের পতন হয়ে ঠাকুর পরিবার গরীব হয়ে যায়। চাকরের ভিড়
কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব
পরিমিত করিলাম; ঘরে থাকিয়া সন্যাসী হইলাম। লিখেছেন
দেবেন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথ তিনশো টাকার ডিনার খেতেন—আর দেবেন্দ্রনাথ তখন চারিআনা মূল্যের ডিনার খাওয়া শুরু করলেন। তখন
তাদের এককোটি টাকার মত দেনা। বিভিন্ন লোকের কাছে তাদের পাওনা ৭০ লাখ টাকা।
ভাইদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ছমাসের মধ্যে পরিস্থিতি সামলে ওঠেন।
এরপরেই আবার তিনি
ভ্রমণে বের হলেন নৌকায় করে। বর্ধমান, আসাম, বর্মায় গেলেন।
১৮৪৮ সালেই তিনি উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলন করেন।
ব্রাহ্মসমা্জের বাড়িটির তেতলা তৈরি করেন। সে সময় ঠাকুর পরিবারের আর কোনো ব্যবসা
বানিজ্য না থাকায় তারা পরিণত হন জমিদারি নির্ভর। ১৮৫০ সা্লে ঠাকুর বাড়ি থেকে
জগধাত্রী পূজা উঠে যায়।
দেবেন্দ্রনাথ
পূজা-পার্বণাদি বন্ধ করে ’মাঘ উতসব’, ‘নববর্ষ’, ‘দীক্ষা দিন’
ইত্যাদি উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি
বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা নামে একটি বিশাল ভূখণ্ড ক্রয় করে আশ্রম স্থাপন করেন। এই
আশ্রমই আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতন। ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ একটি
ট্রাস্ট ডীড তৈরি করে শান্তিনিকেতনকে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন। এবং নিজের
জমিদারির কয়েকটি পরগনার (আনুমানিক ১৮৪৫২ টাকা মূল্যের) সম্পত্তি শান্তিনিকেতন
আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য দান করেন। ডীডে ছিল, ‘’উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার একব্রহ্মের উপসনার জন্য ব্যবহৃত
হইবে। …কোনো সম্প্রদায়বিশেষের অভিষ্ট দেবতা বা পশুপাখি মনুষ্যের মূর্তির
বা চিত্রের বা কোনো চিহ্ণের পূজা হোমযজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। কোনো ধর্ম
বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনো প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না।‘’ এছাড়াও তিনি হিন্দু চ্যারিট্যাবল ইনস্টিটিউশনের বেথুন সোসাইটির অন্যতম
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন
রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫১সালের ৩১ অক্টোবর ব্রিটিশ
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলে তিনি তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি দরিদ্র
গ্রামবাসীদের চৌকিদারি কর মওকুফের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ভারতের
স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত একটি পত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন।
দেবেন্দ্রনাথ বিধবাবিবাহ প্রচলনে উৎসাহী ছিলেন, তবে বাল্য ও বহু বিবাহের বিরোধী
ছিলেন। তবে নিজের পরিবারে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছেন। এটা ছিল তাঁর বৈপরীত্য। শিক্ষাবিস্তারেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব থেকে
ভারতীয় যুবকদের রক্ষার জন্য ১৮৬৭ সালে রাধাকান্ত দেব তাঁকে ‘জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক’ ও ব্রাহ্ম সমাজ
‘মহর্ষি’ উপাধিতে ভূষিত
করে।
পিতৃঋণ শোধ করার
তাগিদেই দেবেন্দ্রনাথ বিষয়সম্পত্তির দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তিনি নিজেই
জমিদারি দেখতে আরম্ভ করলেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে। পরে ছেলেদের উপর দায়িত্ব
দিয়েছেন। কিন্তু নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন। এইক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দেননি।
তাঁর ধর্মবোধ,
ন্যায়পরায়ণাতা, অপৌত্তলিক ধর্মে ও
একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নানা জনহিতকর কর্মে উৎসাহ ইত্যাদি বিষয়
বহুবিখ্যাত। কিন্তু মরার আগে পর্যন্ত সকল দার্শনিকতার পাশপাশি বিষয়সম্পদাদিতে
তাঁর প্রভুত্ব বজায় রেখেছেন।
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
কাটিয়ে ওঠার পরে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগী প্রবলভাবে তিনি
একেশ্বরবাদের প্রচারণায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার জ্ঞান, অর্থ ও
প্রতিপত্তি একক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। সমাজে বঙ্গের রেনেসাঁসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব
হিসাবে শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাশাপাশি নিজের পরিবারেও এর
সুফলগুলো পরিপূর্ণভাবে বিকশারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন উদারভাবে। তাঁর
উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের মতন ব্যবসাবানিজ্যের পথ থেকে সরে আসেন। জমিদারী থেকে
আসমানদারীতে ঝুঁকে পড়েন।
তার উদ্যোগে ঠাকুর
বাড়ি থেকে পত্রিকা বের হয়েছে , নাট্যমঞ্চ হয়েছে, সাহিত্য
রচিত হয়েছে, বিদ্বোৎসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে।
ছেলেরা বিলেতে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাচ্ছে।
দেবেন্দ্রনাথের
সংস্কার কার্যক্রমের কারণে আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে পরিত্যাক্ত হয়েছেন। তারা তার
সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে ভোজন করতে অস্বীকার করেছেন। এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর
পরিবারের জন্য সৃজনশীলতার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমের নতুন স্বজন সন্ধান করেন। যার সুফল
শুধু তার পরিবারেই নয়—আপামর বাংলায়ও ফলেছে। আসমানদারীর
নতুন জমানা এসে গেছে
পর্ব বার....
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
সৌখিন মেজাজের বাবু
দেবেন্দ্রনাথের
চতুর্থ ভাই গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৮৫৪) বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আবার
আসমানদারীর পক্ষেও কাজ করেছেন। দাদার সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সৌখিন
যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবুবিলাস নামে একটি নাটকও লিখেছেন। ব্রাহ্ম হলেও তার
পরিবারে দোল-দুর্গোৎসব অব্যাহত রেখেছেন। এ উপলক্ষ্যে বাড়িতে আয়োজন করতেন যাত্রা
প্রভৃতি লৌকিক বিনোদনের ব্যবস্থা। বেশ বাবু চেহারা ছিল তার চরিত্রে।
রবীন্দ্রনাথ এই পালাগানের স্মৃতি চারণ করেছেন আমার ছেলেবেলা গ্রন্থে।
গিরীন্দ্রনাথের নাতি অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—
দাদামশায়ের সখ ছিল
বোটে করে বেড়ানো। পিনিস তৈরি হয়ে এল—পিনিস কি জিনিস জান, বজরা আর পানসি,
পিনিস হচ্চে বজরা আর পানসির বড়ো ভাই—ভিতরে সব সিল্কের গদি, সিল্কের পর্দা, চারদিকে আরামের চূড়ান্ত।
ফি রবিবারে শুনেছি—দাদামশায় ইয়ারবক্সি নিয়ে বের হতেন--সঙ্গে থাকত খাতা পেন্সিল, ছবি আঁকার সখ
ছিল, দু-একজোড়া তাসও থাকত বন্ধুবান্ধবদের খেলার জন্য।
পিনিসের উপরে থাকত একটা দামামা।। দাদামশায়ের পিনিস চলতে শুরু হলেও সেই দামামা
দকড় দকড় করে পিটতে থাকত। তার উপরে হাতি মার্কা নিশেন উড়ছে পতপত করে। এই তার সখ,
দামামা পিটিয়ে চলতেন পিনিসে।..তার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন কবি
ঈশ্বর গুপ্ত। অনেক ফরমাইশী কবিতাই ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন সে সময়ে।...দাদামশায়ের
যাত্রা করবার সখ, গান বাঁধবার সখ—নানা শাখা নিয়ে তিনি থাকতেন। তিনি বেশ একটা সৌখিনতা তৈরি করেছিলেন
ঠাকুরবাড়িতে।
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৪১-১৮৬৯) : নাট্যশালা স্থাপন
গিরীন্দ্রনাথের ছেলে
গণেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ী বুদ্ধ ছিল ক্ষুরধার। দেবেন্দ্রনাথ তার উপরে
ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে নির্ভর করতেন। তাছাড়া শিল্প-সাহিত্য—ইতিহাসচর্চা-নাট্যাভিনয় ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর বিপুল আগ্রহ ছিল।
১৮৬৬ সালে ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন নবনাটক প্রকাশ করেন।
সেটা ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মঞ্চস্থও করেন। ১৮৬৭ সালের ৬ জানুয়ারি দেবেন্দ্রনাথ একটি
চিঠি লেখেন গুণেন্দ্রনাথকে। তখন দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি কাজে কালিগ্রামে অবস্থান
করছেন। তিনি লিখেছেন—
তোমাদের নাট্যশালার
দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা
অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্বরসের আস্বাদনে
অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই
প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমাদের সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার
জন্য আমার অনুরোধ ছিল। তুমি তাহা সম্পন্ন করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে স্নহপূর্বক
সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।
দেশের
মানুষের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন ঘটানোর উদ্দেশ্যে আয়োজিত চৈত্র মেলা বা
হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি অন্যতম
সংগঠক ছিলেন। এই হিন্দুমেলায় তখনকার কৃষি-শিল্প-সংস্কৃতির একটি প্রদর্শনী ছিল।
সেখানে গ্রাম থেকে কৃষিপণ্য-হস্তশিল্পজাত সামগ্রী প্রদর্শন করা হত। এই
হিন্দুমেলায় মুসলমান গায়কগণও পালাগান করতে আসতেন। কোনো অর্থেই এই চৈত্রমেলা বা
হিন্দুমেলা হিন্দুত্ববাদের জিনিস ছিল না।
ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক
ঐতিহ্যের সঙ্গেও গুণেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। হিন্দি গান ভেঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায়
তিনিও প্রভুত উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সে সময়ে ঠাকুরবাড়িতে বড়ো বড়ো ওস্তাদরা এসে
গান শোনাতেন। নামকরা যাত্রাওয়ালারা এসে অভিনয় করতেন। মেয়েরাও দেখার সুযোগ
পেতেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকটি গুণেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। ১৮৮৬ সালে এই
নাটকটি প্রকাশিত হয়।
দ্বিজেন্দ্রনাথের অল্প
বয়সের ঝোঁক ছিল কাব্য রচনা ও ছবি আঁকায়। ১৮৬০ সালে কুড়ি বছর বয়সে তিনি
কালিদাসের মেঘদূতের পদ্যোনুবাদ করেন। এরপরই দর্শনের ত্ত্ত্বানুসন্ধানে তিনি মনোযোগী
হয়ে পড়েন। তার স্মৃতি কথা থেকে সে সময়ে ঠাকুরবাড়ির একটি চেহারা পাওয়া যায়—
পূজার সময়ে আমাদের
বাড়িতে যে উৎসব দেখিয়াছি, সে রকম উৎসব পরে আর কখনো দেখি নাই। বোধ হয়
আমাদের প্রতিমা দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হইত। পূজার অনেক আগে হইতেই আমাদের
বাড়িতে দর্জি বসিয়া যাইত, জহুরীর আগমণ হইত। দর্জী ও
জহুরী মিলিয়া বাড়ির সকলের পোষাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত আরম্ভ করিত।
গৃহ-প্রাঙ্গণে যে যাত্রা প্রভৃতির আযোজন হইত, তাহাতে
যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল। দরজা বন্ধ করিয়া পাহারা রাখিয়া,
কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত
হইত। ধনী গৃহস্থের বাড়ির পূজার আয়োজনে কেবল মাত্র সেই পরিবারের নিমন্ত্রিত
নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের জন্য করা হইত না। প্রত্যেক গৃহস্থের
পূজার উৎসব একটা বৃহৎ সামাজিক উৎসব ছিল। সমাজের ছোট-বড় সকলেই অবাধে সে উৎসবে
মাতিয়া উঠিত। আমার পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্মানুরাগ বশতঃ পূজার সময় বাড়ি থাকিতেন না।
তিনি কিন্তু আগে হইতেই বিদেশ পর্যটনে বাহির হইতেন।
তাঁর সময়েই
ঠাকুরবাড়িতে নাটক রচনা,
অভিনয় ও আনন্দমুখর সঙ্গীত ধ্বনিত পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।
রবীন্দ্রনাথ তখন বেশ ছোটো। দূর থেকে এসবই দেখতে পেতেন।
সমীর সেনগুপ্ত লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের
শিশুকালে তাদের বাড়িতে তিনটি ধারা দেখা যায়। প্রধান ধারাটি হল জনপ্রিয়, সঙ্গীত-নাটক-প্রমুখ কোলাহল মুখরিত যৌথ আনন্দোৎসবের ধারা। দ্বিতীয়টি হল—পাঠকক্ষে নির্জনে বসে জ্ঞানচর্চার ধারা। তৃতীয়টি হল বুদ্ধিনির্ভর, বিবর্তনকামী,
জ্ঞানাশ্রয়ী ভক্তিবাদের ধারা। এই ভক্তিবাদের ধারাটি আদি
ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মোপসনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের
নেতৃত্ব।
দ্বিজেন্দ্রনাথ এর
মধ্যে থেকেও থাকেননি। একা বসে তত্ত্ব জ্ঞান, গণিতচর্চা আর ছড়া লিখে দিন কাটিয়েছেন। বাংলা
শর্টহ্যান্ড লিখনপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ বড়োদাদা বিষয়ে লিখেছেন—গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন। সমাজের নির্দিষ্ট করে
দেওয়া রীতিনীতি থেকে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে মূল্য দেওয়ার ধারণাটাও তাঁর মধ্যে
প্রবলভাবে ছিল। সামাজিক অনুশাসনের প্রতিবাদ হিসাবে চিন্তাজগতে ব্যক্তিমানসের
অভ্যুত্থান ঘটানো ছিল রেনেসাঁর মূল কথা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই
ধারারই অনুসারী ছিলেন।
১৮৭৫ সালে মেজ ভাই
সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগম সভার প্রথম অধিবেশনটি বসিয়েছেন
তিনি। তৎকালীন বাংলার বিদ্বজ্জনেরা ঠাকুরবাড়িতে ঘোরাফেরা করছেন। বিদ্বজ্জনসমাগম
সভার উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে
পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বাড়ানো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—এই উপলক্ষে অনেক রচনা ও কবিতাদিও
পঠিত হইত, গীতবাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয়ও
প্রদর্শিত হইত এবং সর্ব্বশেষে সকলের একত্র প্রীতিভোজনের মধ্যে দিয়ে এই
সাহিত্য-মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হইত। বছরে একবার এই সভার অধিবেশন হত। দ্বিতীয়
অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খেদ নামে একটি কবিতা পড়েছিলেন। তখন
ভারতী নামে একটি পত্রিকা বের হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। রচনা করছেন বেশ
কিছু ব্রাহ্মসঙ্গীতও। ১৯২১ সালে তিরি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে
উঠেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। এখানে দাদার
সঙ্গে তাঁর ভাবনার পথটি আলাদা হয়ে গেছে।
পশুপাখির প্রতি
দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল বড়ো ভাব। সুধাকান্ত চৌধুরী লিখেছেন—
দূর থেকে তাকিয়ে
দেখলাম দক্ষিণের বারান্দায় বড়োবাবু তাঁর চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর সামনে
একটি টেবিল পাতা। সেই টেবিলের উপরে ছিল দুই একটি ছোটো ছোটো প্লেট। দূরের থেকে
দেখতে পাইনি সেই প্লেটগুলিতে কী আছে। তবে দেখলাম অই টেবিলের উপরে তিন-চার রকমের
পাখি ঠোকর দিয়ে প্লেট থেকে কি সব খাচ্ছে। দেখলাম একটা গাছের থেকে দুটো কাঠবিড়ালী
দৌঁড়ে গিয়ে বড়ো বাবুর চেয়ার বেয়ে টেবিলের উপরে লাফ দিয়ে উঠছে। তাদের
বড়োবাবু বিস্কুটের মতো কী একটা পদার্থ ভেঙে ভেঙে দিচ্ছেন। তারা পেছনের দুই পায়ে
বসে সামনের দু-পা দিয়ে ধরে যেন ছোটো ছোটো হাত দিয়ে ধরে সেই খাবার খাচ্ছে।
পাখিগুলোও কী সব খাচ্ছে—এরা হল সকালবেলায়
বড়োবাবুর প্রাতরাশের সময়ের মজলিশের সভ্যবৃন্দ।
তিনি বাংলা গানের
প্রথম স্বরলিপি তৈরী করেন। এটাকে পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ণরূপ দেন। তিনি
সাঁতাশটি বই লিখেছেন। আত্মজীবনীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—
আমি অনেক লিখিয়াছি; এই লেখাপড়া
ছাড়া আমি আর জীবনের বড়ো একটা কিছুই করিতে পারিতে পারিলাম না। কখনো আমি বিষয়কর্ম
ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতাম না—বাবা ইদানিং আমাকে
কোনও বিষয়কর্মে থাকিতে দিতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ
জমিদারী দেখেছিলেন মাত্র মাসখানেক। এর মধ্যে আবার তিনি সাহজাদপুরেও গিয়েছিলেন।
সেখানে নিজের উদ্যোগে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের খোজ খবর
নিয়েছেন। তাদের খাজনা মউকূপের প্রস্তাব করছেন। এ
ঘটনায় আমলারা বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। আর তখন তখুনি তাকে বাদ দিয়ে তার ছেলে
দ্বিপেন্দ্রনাথকে জমিদারী দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথ পাঁচ বছর
জমিদারি পরিচালনা করেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথ জরিদারি পারিচালনার ভার পান।
সেকালে জোঁড়া সাঁকোর
ঠাকুরবাড়ি ছিল একান্নবর্তী পরিবার। পাঁচ ও ছ নম্বর বাড়ি মিলিয়ে বিশাল বাড়ি।
সত্যন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাড়িটা ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হওয়া আগে
থেকেই হিন্দুত্বের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধ জেগে উঠেছে দেবেন্দ্রনাথের মতো তাঁর ছেলেমেয়েদের
মধ্যেও। নয় বছর বয়সের একটি স্মৃতি বলছেন দেবেন্দ্রনাথের মেজো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ
ঠাকুর। ‘এক সময়ে আমাদের বাড়ি সরস্বতী পূজা হত। মনে আছে একবার সরস্বতী
পূজার অর্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময়
আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর পায়ের উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট।
তাতে দেবীর মুকুট ভেঙে পড়ল।
ছেলেবেলার বর্ণনা
দিয়েছেন—ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়ামচর্চার অভাব ছিল না। ভোরে
উঠে জোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে
আসতুম।..তা ছাড়া ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া এসব ছিল।...হীরা সিং বলে একজন
পালোয়ানের কাছে আমরা কুস্তি শিখতাম।রবীন্দ্রনাথকেও কুস্তি
শিখিয়েছিলেন এই হীরা সিং। সংস্কৃত শেখাতে আসতেন বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। এর মধ্যে
আরবী সাহিত্যেও বেশ বুৎপত্তি লাভ করেছেন।
১৮৫৭ সালে কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পাশ করেন।
তার সঙ্গে আরও পাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। প্রেসিডেন্সী
কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তার সহপাঠী ছিলেন
কেশবচন্দ্র সেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচিত হন সত্যেন্দ্রনাথের
মাধ্যমে। কেশবচন্দ্র সেনকে তার বাড়ির লোকেরা হিন্দু লোকাচার না মানার জন্য
অত্যাচার করছিল। এ কারণে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেশব
চন্দ্রের প্রভাবে সমাজ এক নতুন মূর্তি গ্রহণ করেছিল। সত্যন্দ্রনাথও সেই কর্মকাণ্ডে
মেতে উঠেছিলেন। এ সময়ই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদি থেকে হৃদয়ভেদী প্রার্থনা
আর উপদেশ দিচ্ছেন। আর ঠাকুরবাড়ির সবাই গান লিখছেন। গানে সুর দিচ্ছেন
ব্রাহ্মসমাজের সভাগায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত
গুরু। তিনি ৬০০ ব্রাহ্মসঙ্গীতের সুর করেছিলেন। গানের সারল্যের আদর্শটি
রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু চর্কবর্তীর কাছ থেকেই শিখেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ যে বছর
জন্মেছিলেন সে বছরই তাঁর বড়ো দিদি সুকুমারীর বিয়ে হয়েছে হিন্দুপদ্ধতির বদলে
ব্রাহ্মধর্মানুসারে। এটা ছিল তৎকালীন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের
বিদ্রোহ। ঠাকুর পরিবার আবার একঘরে হয়েছিল এ কারণে। ব্রাহ্মমত ধীরে ধীরে
তাত্ত্বিক রূপ থেকে আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের চেহারা পেয়েছে। পৌত্তিলকতার
বিরুদ্ধেওতাদের বিদ্রোহ সমাজে জায়গা করে নিচ্ছে।
কিছুদিন পরে
সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে পুরনো নিয়ম ভেঙে বাড়ির বাইরে বের করে নিয়ে গেলেন
বোম্বাইতে। তিনি লিখেছেন,
‘জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোনো কোনো
উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে উঠা যায় কী করে? গাড়ি করে তো
যাওয়া চাই। আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ি থেকেই গাড়িতে ওঠা যাক। কিন্তু বাবামহাশয়
সম্মত হলেন না। বললেন মেয়েদের পালকি করে যাবার যে নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক।‘ অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ কর্মচারীদের চোখের সমানে
দিয়ে বাহির বাড়ির দেউড়ি ডিঙিয়ে গাড়িতে উঠবেন, এ তাঁর
কিছুতেই মনঃপুত হল না।সুতরাং গাড়িতে নয়—সত্যেন্দ্রনাথের
স্ত্রীকে গাড়িতে নয় পালকীতে করে জাহাজঘাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
...তখন
অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ
বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপ মোড়া পালকীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে
বেহারারা পালকী সুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে।
সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে
সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৭২ সালে। মেয়ে ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় এক বছর পরে। তখন
তাঁদের ধাত্রীমা রাখা হয়েছিল এক মুসলমান মহিলাকে। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—‘আমি তো মুসলমানীর দুধ পর্যন্ত খেয়েছি’।. অথচ মুসলমানের খাদ্যের ঘ্রাণ নাকে আসায়
ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষের জাত গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে
বারবার গেছেন তাঁর কর্মস্থলে। পারিবারিক বিষয়াদিতে পরামর্শ নিয়েছেন। মেজোবৌঠানের সঙ্গে তাঁর মধুর
সম্পর্ক হয়েছে। তারা তাঁকে বিলেতেও নিয়ে গেছেন। বিলেতি কেতা শেখার ব্যবস্থা
করেছেন। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী বালিকা বধু বলে সন্তানসহ মৃণালিনী দেবীকে
জ্ঞানদানন্দিনী তার হেফাজতে রেখেছেন।
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর
সম্পাদনায় বালক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পত্রিকার প্রদান
লেখক। তিনি ফটোগ্রাফীর চর্চাও করতেন। তিনিই প্রথম সাড়ির নিচে পায়জামা পরা,
সায়া পরা, জামা পরা ও বম্বে ধরনের
সাড়ি পরা ঠাকুর পরিবারে প্রচলন করেন। তারপর বাংলায় এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়। তারাই
বঙ্গে বাঙ্গালীদের মধ্যে জন্মদিন পালন প্রথার চালু করেন। বেশ কিছু বইও লেখেন তিনি।
চাকরি শুরুর দুবছর পরে
সত্যেন্দ্রনাথ বিচার বিভাগে চলে যান। ৩৩ বছর চাকরী করে অবসর নেন ১৮৯৭ সালে। তখন
ছিলেন সাতারা জেলার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসন জজ। অবসর নিয়ে কোলকাতায় বসবাস শুরু
করলেন জোড়াসাঁকোর বাইরে আলাদা বাসা নিয়ে। তাঁদের বাড়িতে কলকাতার ধনী অভিজাত
সমাজের অনেকেই আগমন করতেন। বিশেষ করে তরুণদের আগমন ছিল চোখে পড়ার মত। তাঁর রূপসী
ও বিদূষী কন্যা ইন্দিরা দেবী এইসব সভায় উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের খুব
স্নেহের কলকাতায় এসেই সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে
ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে পড়েন। তিনি নিজে
জমিদারী দেখেন নি কখনো। তার ছেলে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন
দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ১৯০৫ সালে। তার অবিবেচনার কারণে জমিদারিতে প্রচুর দেনা
হয়ে যায়। ফলে ঋণ করতে হয়েছিল।
সত্যেন্দ্রনাথ নয়টি
বাংলা ও তিনটি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেন। সেসবের মধ্যে সুশীলা ও বীরসিংহ নাটক
(১৮৬৭), বোম্বাই চিত্র (১৮৮৮), নবরত্নমালা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রয়াস (১৯১৫), ভারতবর্ষীয়
ইংরেজ (১৯০৮) ইত্যাদি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়াও তার কৃত তিলকের
ভগবদ্গীতাভাষ্য, (কালিদাস) এর মেঘদূত এবং তুকারামের
অভঙ্গের অনুবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশকিছু ব্রহ্মসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গানও
রচনা করেন এবং কিছুকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
১৯২৩ সালের ৯
জানুয়ারি তার মৃত্যু হয়।
সংবাদপত্রে স্বাধীনতা--
ইতিমধ্যে ১৮১৮ সালে
রেগুলেশন নামে একটি বিধি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বিধির বলে সরকারি নীতির সমালোচনা
বা বিরুদ্ধতার অপরাধে যে-কোনও ব্যক্তিকে—তা ইউরোপীয়ই হোন বা ভারতীয়ই হোন—কারণ দর্শাবার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কারাগারে আটক
করা যেত। রামমোহন এই বিধির বিরোধিতা করে কোম্পানীর সরকারকে চিঠি দিলেন। ১৮২৩ সালে
প্রেস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট নামে একটি আইন জারি করা হয়। তাতে নির্দেশ দেওয়া
হয়েছিল—বিনা সরকারি অনুমোদনে সরকারি নীতি সংক্রান্ত কোনও সংবাদ বা আলোচনা
সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না। এটা স্পষ্টতই ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
হরণ। সে সময়ে তিনি লিখছেন—রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে
জনসাধারণের মতামত দেওয়ার এবং সমালোচনা করার অধিকার আছে। জনসাধারণের মতামত ও
বিবেচনা অনুসারে শাসককে রাষ্ট্রশাসন করতে হবে। এবং তিনি আরও বললেন—অবস্থাবিশেষে জনসাধারণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। ১৮৩৫
সালে অই কালো আইন উঠে যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই আইন বাতিলে রামমোহনের ভাবনাকে
বাস্তবায়ন করতে জানপরাণ দিয়ে লড়েন। পাশাপাশি সতীদাহ প্রথা বাতিলের আন্দোলনেও
তিনি সব সময়ই রামমোহনের সহকারী হয়ে উঠেছিলেন।
ব্যক্তিস্বাধীনতার
ধারণার সূত্রপাত--
রামমোহন জমিদারেরসঙ্গে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি এই প্রথা বাতিলের দাবী তুলেছিলেন।
বলেছিলেন চিরম্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে নয়—দিতে হবে কৃষককে। তিনি
ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাটি এনেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার শুরুতে
আছে ক্ষুদ্রতম এককের যিনি কর্তা, তাকে সমালোচনা করার
অধিকার থাকতে হবে। পরিবারের প্রধানকে সমালোচনা করবেন স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সবাই। বৃহত্তর এককের কর্তা হলেন জমিদার। তাকে সমালোচনা করার
অধিকার থাকবে প্রজাদের। তিনি দাবী তুললেন নারীকে
সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে। কৃষককে জমির মালিকানা দিতে হবে। এই বস্তুগত অধিকার
দিলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তন থেকেই আসবে ব্যক্তিস্বাধীনতা।
রাজনীতির উন্মেষ--
এর আগে এদেশের মানুষ
জানতেন না দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রজারও একটি স্থান আছে—আধিকার আছে। কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সে বিষয়ে প্রজার মতামত
থাকতে নেই। প্রজারা জানে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রাজা-বাদশা-জমিদারদের।
প্রজাদের ভালোমন্দ ভাবনা ভাববেন শুধু এই শাসক সম্প্রদায়। রাজনীতি নিয়ে শুধু সেই
অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্তরাই মাথা ঘামাত যারা কোনো না কোনোভাবে
শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রজারা রাজনীতি জানত না। সে সময়ে যে সব
প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল সেখানে প্রজারা নিজেদের ক্ষমতায়নের কথা কখনো ভাবতে পারেনি।
তারা কেবল সচেতন ছিল ধর্ম সম্বন্ধে। আর ধর্ম সকলকালেই শাসিতদের পক্ষে
থেকেছে। সে সময়ে রামমোহন রায় লিখেছেন—রাজনৈতিক সুবিধা ও
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আধ্যাত্মিক ধর্মের সংস্কার দরকার। তিনি লিখেছেন, যাহা শিক্ষা
দেয় যে, সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর কোনো যথার্থ অস্তিত্ব নাই,
পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতির কোনো প্রকৃত সত্তা নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক স্নেহের সম্পর্ক নাই এবং সেইজন্য
যত শীঘ্র পারি তাহাদের ও এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারিলেই মঙ্গল, সেই ধর্মের সঙ্গে কোনো যোগ থাকার কোনো দরকার নাই।
রাজা রামমোহনের এই
ভাবনাগুলো তখন বঙ্গে বাংলার গণজাগরণের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে। দ্বারকানাথ রামমোহনের
প্রতিটি কাজের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। নিজেদের ব্যবসামনোবৃত্তিটার বদলে
বুদ্ধিবৃত্তিক বিত্তের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। রামমোহন ধর্মীয় বাঁধা অমান্য করে বিলেতে
গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথও তাই।
রবীন্দ্রনাথ
পরবর্তিকালে লিখেছেন একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে
অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি
ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর
সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।
পর্ব তের....
নতুন দাদার বোনা বীজ
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
পঞ্চম ছেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নতুন দাদা। ছেলেবেলা থেকেই
তিনি ছবি আঁকতেন। স্কুল অব আর্টে ভর্তিও হয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়ির নাট্যাশালা
প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে অভিনয় করেন। মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে গিয়ে
ফরাসী ভাষা শিখেছেন। সেতার বাজনাতে তাঁর দক্ষতা এসেছে। চৈত্রমেলার জন্য গান
লিখেছেন। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
১৮৬৮ সালে বিয়ে
করেছেন বাবার নির্বাচিত পাত্রী কাদম্বরী দেবীকে। তখন তার নিজের বয়স ১৯ বছর ২ মাস।
আর কাদম্বরীর নয় বছর। রবীন্দ্রনাথের সাত বছর ২ মাস। কাদম্বরী লেখাপড়া জানতেন না।
তাঁকে উপযুক্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঠাকুর পরিবারের দস্তুর মতো।
সে সময়ে রবীন্দ্রনাথদের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। জোড়াসাঁকোর ভেতরে
চাকরদের কাছে বেড়ে উঠেছেন। ভেতরবাড়িটা দূরের। সেখানে যাওয়ার সুযোগ নেই। একারণে
জোড়াসাঁকোর সীমানার মধ্যে থেকে বাইরের আর ভেতরের যা কিছুই তখন দেখতে পেতেন—তার সবই ছবির মত করে তাঁর কৌতুহলী চোখ পড়ে নিত। রাত নটার পরে
তাদের পড়া শেষ হত। ভিতর বাড়ি যাওয়ার সময় পার হতেন খড়খড়ি দেওয়া লম্বা
বারান্দা। দেখতে পেতেন জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় দাসীরা পাশাপাশি পা মেলে বসে আছে।
উরুর উপর প্রদীপের সলতে পাকাতে পাকাতে মৃদুস্বরে নিজেদের দেশের গল্প করছে। তারপর
বালকদের খাওয়া দাওয়া শেষ হত। তখন শঙ্করী কিংবা প্যারি কিংবা তিনকড়ি দাসী এসে
রূপকথার গল্প বলত। শুয়ে শুয়ে কানে শুনতে পেতেন রূপকথা—আর দেয়ালের চুন খসা রেখার মধ্যে সেইসব রূপের গল্পগুলো দেখতে
পেতেন। এইভাবে সাতবছরের রবিবালকের ঘুম নেমে আসত।
এর মধ্যে ২ বছরের বড়ো
কাদম্বরী এসে গেছেন নতুন বৌঠান হয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—তখন অন্তপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে
আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরেরই, যাহাকে কিছুই জানিনা অথচ যিনি আপনার, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারী ইচ্ছা করিত।
ভাব করার চেষ্টা করলেও
দিদি স্বর্ণকুমারীর তাড়া খেয়ে ফিরে বাইরেই আসতে হত। সেখানে শুধু কাদম্বরীই নয়—তার আলমারীর কাঁচের ও চিনামাটির দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী দূর থেকে দেখে
দেখে আঁশ মেটাতো হত। তবে ধীরে ধীরে এই সীমা ঘুচে গেছে। নতুন বৌঠানের সঙ্গে বালকদের
ভাব হয়ে গেছে।
কাদম্বরী বড় হয়ে
উঠছেন। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি
লিখেছেন তাঁর জীবন স্মৃতিতে—স্ত্রী স্বাধীনতার শেষে আমি এত
বড় পক্ষপাতি হইয়া পড়িলাম যে গঙ্গার ধারের কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক
অবস্থানকালে আমি আমার নিজের স্ত্রীকে নিজেই অশ্বারোহন পর্যন্ত শিখাইয়াছিলাম।
তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজন পাশাপাশি চড়িয়া
বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছাইয়া দুইজনে সবেগে
ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত।
এর ঠিক দশ বছর আগে তার
মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে বাড়ি থেকে স্ত্রীকে গাড়িতে করে জাহাজ ঘাটায় যাওয়ার
অনুমতি দেওয়া হয়নি। দশ বছরের ব্যবধানে দেবেন্দ্রনাথের জীবনকালেই তাঁর আরেকপুত্র
স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।
ততদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
বাড়ির প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছেন। নাটকের জন্য আর্কেস্ট্রা তলি করছেন, গান করছেন,
গান বাঁধছেন, সেতার শিখছেন, ফরাসী ভাষা শিখছেন, জোঁড়াসাকোর বাড়িতে
নাট্যশালা তৈরি করেছেন, সেখানে বাড়ির বউদেরও অভিনয়ে
নামাচ্ছেন, ব্রাহ্মসমাজের সভায় বক্তৃতা করছেন, কোলকাতায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে পাটের ব্যবসা--
নীলের ব্যবসাও করছেন। হয়েছেন বহুকাজের কাজী। দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন, গণিত আর ছড়া লেখা নিয়ে ব্যস্ত, সত্যদাদা
সিভিল সার্ভিসে মগ্ন। হেমেন্দ্রদাদা ব্যায়াম আর ছেলেমেয়েদের বিচিত্রবিদ্যায়
সময় কাটাচ্ছেন। এরা কেউই জমিদারীর কাজে আগ্রহী
নন।
১৮৭৩ সালে দাদা
সোমেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। সাড়ে তেরো বছরের বৌঠান কাদম্বরী
তখন খুদে দেওরদের জন্য হবিষ্যান্ন রেঁধে দিয়েছেন। তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিনদিন
তার স্বাদে, গন্ধে যুক্ত করে রেখেছিল লোভী ছেলেদের। তাদের মধ্যে এ সময় অন্তরঙ্গ
সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। ১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন ম্যাকবেথ। সেটা পড়ে
শোনাতে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। এই নাটকে একটি চরিত্রের নাম হেকেটি। সেই
থেকে বৌঠানকে নাম দিয়েছেন হেকেটি।
এই ১৮৭৫ সালে
দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদাদেবীর মৃত্যু হলে ছোটো ছোটো দেবরদের দেখে রাখার কাজটি
নিয়েছেন। তখন তাঁর বয়স ১৬।. আর রবীন্দ্রনাথের ১৪।
মা মারা গেলে এই বিরাট
বাড়িটির দ্বায়িত্ব নিয়েছেন বড়ো দিদি সুকুমারী দিদি। সঙ্গে ছিলেন শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী—এই দুই দিদি। আর ছিলেন বাড়ির অন্যান্য বউ—সর্বসুন্দরী, নীপময়ী, প্রফুল্লময়ী।
কাদম্বরী নিঃসন্তান। স্বর্ণকুমারীর দুমাসের মেয়ে ঊর্মিলাকে নিজের কোলে তুলে
নিয়েছেন এই বালকদের পাশাপাশি। তাকে খাওয়ান। স্নান করান। ঘুম পাড়ান। তিনি
ঊর্মিলার মা হয়ে উঠেছেন। ঊর্মিলার বয়স যখন মাত্র পাঁচ। তখন কাদম্বরীদের তিনতলার
ছাদের ঘর থেকে নমে আসা ঘোরানো সিঁড়ি থেকে একা একা নামতে গিয়ে এই ছোটো মেয়েটি পা
ফসকে পড়ে গেল। মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেল। কেউ কেউ দোষ দিল কাদম্বরীর। প্রচণ্ড
আঘাত পেলেন তিনি। বিষণ্নরোগে আক্রান্ত হলেন। এ সময় তাঁর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রও
সংসারে সময় দিতে পারছেন না। নানাকাজে বাইর বাইরে থাকেন। তখন কাদম্বরীর বয়স ২১।. দুবার
আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন। প্রথমবারে ফিরে এলেন। দ্বিতীয়বারে কাদম্বরী
চলে গেলেন। সেদিন ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল।
সারদা দেবী মারা গেলে
দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তাঁর তেতলার ছাদের ঘরটি
পেয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্বামীস্ত্রী দুজনে টবে ফুলের বাগান বসিয়েছেন। সেখানে
আসর জমে ওঠেছে সাহিত্য ও সঙ্গীতের। এখানে কবিতা পড়তে আসতেন সেকালের বিখ্যাত কবি
বিহারীলাল চক্রবর্তী। সে কবিতা শুনে রবিরও ই্চ্ছে জাগে বিহারীলালের মত কবিতা
লিখতে। বৌঠান তাকে উৎসাহও দেন। রবি লেখেন। বৌঠান শোনেন। আর উৎসাহ দেন দাদা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—তিনি (জ্যোতিরিন্দ্র) আমাকে খুব একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা
দিয়েছিলেন। তাহার সংশ্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা
আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিত না—সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাহাকে
নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে
আশৈশব বাঁধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতার তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। জ্যোতিদাদাই সম্পুর্ণ
নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আত্মোপলদ্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া
দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপনি শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার
জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।
সে সময়ে
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সরোজিনী নাটকটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের জন্য ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ পরিণত গানটি
লিখে দেন। জ্যোতিদাদা তাকে প্রমোশন দিয়ে এরপর থেকেই তার সমশ্রেণীতের তুলে
নিয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকা বের করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই পত্রিকার
কারণে রবির কাছে জীবন অর্থময় হয়ে উঠেছে। তখন তাঁর বয়স ১৬।
রবীন্দ্রনাথ দেখছেন এই
সময় নতুনদাদা এই প্রথম গানের সুর তৈরি করছেন। সুর তৈরি করা যে খুব সহজ বিষয়—সেটা দাদাকে দেখে শিখেও নিচ্ছেন। নতুনদাদা তার পিয়ানোতে নতুন নতুন
সুর করছেন। আর সুরে শান্ত ভঙ্গিতে অনায়াসে কথা বসিয়ে গান রচনা করে ফেলছেন বালক
রবি।
দেবেন্দ্রনাথ এই
কর্মোদ্যোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জমিদারি দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি
জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একতলায় অবস্থিত কাছারির অফিসে হিসাবপত্তর দেখছেন। সঙ্গে গুণেন্দ্রনাথ।
দুপুরের খাবার খেয়ে গুণেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির একতলায় জমিদারির কাজ
করতে করতে কাছারিকে দুই ভাই ক্লাবের মতোই করে নিয়েছেন। কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের
বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না। মাঝে মাঝে একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসলে ছুটি-ছাটায় বালক
রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোলের কাছে এসে বসতেন। গুণেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁকে ভারত বর্ষের
ইতিহাসের গল্প বলতেন। এই বয়সকালেই তিনি চুরি করে দীনবন্ধু মিত্রের জামাই বারিক প্রহসন
বইটি পড়ে ফেলছেন।
জমিদারীর হিসাব দেখার
সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র জমিদারি মহালে চলে গেছেন। মাঝে মধ্যে গেছেন শিলাইদহে।
সেখানে খুঁজে বের করেছেন লালন ফকিরকে। তার গান শুনতে শুনতে স্কেচ করে নিচ্ছেন। আর
নিজে লিখছেন ঐতিহাসিক নাটক পুরুবিক্রম। সেটা ১৮৭২ সালের ঘটনা।
১৮৭৪ সালে সারদাচরণ
মিত্র ও অক্ষয় সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ কয়েক
খণ্ডে। নতুনদাদা সেগুলো কিনছেন। আর রবি পড়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছেন বৈষ্ণব
কবিতার ভাব ও ভাষা। নতুনদাদা এই ছোটোভাইটিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথে
রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার বীজটিকে তিনি পরিকল্পিতভাবে বুনে দিচ্ছেন। জল দিচ্ছেন। আলো
দিচ্ছেন। হাওয়া দিচ্ছেন। আর রবীন্দ্রনাথও এই বীজকে আপনার প্রাণের ভেতরে অঙ্কুরিত
করে নিচ্ছেন। ভ্রুণমূলটি বেরুচ্ছে। বীজপত্রটি মেলছে মাটির ভেদ করে। কাণ্ড জেগে
উঠেছে। শাখা প্রশাখা ছড়িয়েছে। পাতা ধরেছে। ফুল ও ফলে বিরাট মহীরূহে পরিণত
হয়েছে। জমিদার বাড়ির ছেলেটি জমিদারীর বদলে আসমানদারীর খাতায় নাম লিখে ফেলেছেন।
তিনি প্রকৃতি দেখেন। মানুষ দেখেন। মানুষের ভেতরে সহজ মানুষটিকে খুব সহজেই খুঁজে
নিতে পারেন।
তার আগেই
জ্যোতিরিন্দ্র নীলের ব্যবসা কিছু অর্থ করেছিলেন। সেটা দিয়ে তিনি জাহাজ কিনলেন।
নাম দিয়েছিলেন নিজের নাটকের নামে—সরোজিনি। খুলনা বরিশাল রুটে এই
জাহাজটি বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়ে পাল্লা দিতে যাত্রীদের জন্য টিকিট
ফ্রি করে দিলেন। ফ্রি টিকিটের সঙ্গে মাগনা খাওয়া দেওয়া হত যাত্রীদের। ফলে জাহাজ
ব্যবসাটি মার খায়। বিপুল অঙ্কে ঋণী হয়ে পড়েন। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে আর তিনি
বিয়ে করেননি। ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সব কিছু থেকে।
১৮৯৮ সালে তিনি
সত্যেন্দ্রনাথের বির্জিতলার বাড়িতে খুলেছেন পারিবারিক খাতা। এই খাতাটি একটি অনন্য
বস্তু। খাতাটি রাখা থাকত সিঁড়ির কোণে। এখানে পরিবারের যো কোনো সমস্যই যে কোনো
বিষয় নিয়ে মন্তব্য লিখতে পারতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে লিখে
খাতাটির উদ্বোধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরবর্তি তিন বছর অনেক বিচ্ছিন্ন
ভাবনাচিন্তা এখানে লিখে রেখেছেন। সবাই দেখেছেন পড়েছেন। মন্তব্য করেছেন। আর পরে
তিনি এই ভাবনাগুলিকে আশ্রয় করে স্থায়ী পরিণত লেখা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে
শিলাইদহে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয করিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা প্রকৃতির
সঙ্গে।
পর্ব চৌদ্দ....
রবীন্দ্রনাথের জন্মের
কাল
ঠাকুরবাড়ির আঙিনার
আলো
ইংরেজদের শাসনের একশো
বছর পূর্তি হয় ১৮৫৭ সালে। এ বছরই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ইংলন্ডের মহারানী ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার নিয়েছেন। ১৮৫৮ সাল থেকে পরিবর্তনের কাল শুরু
হয়েছে।
এর পঞ্চাশ বছর আগে
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নামে কিন্তু কলেজ হলেও সুনিয়ন্ত্রিণ ছিল
ইংরেজদের হাতে। কলেজটি ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ১৮৫৭ সালে
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিধবা বিবাহ পাশ হয়েছে ১৮৫৬ সালে।
দেবেন্দ্রনাথের
তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মআন্দোলনে পরিণত হয়েছে।
কেশবচন্দ্র সেন মশাই এই আন্দোলনকে নবপ্রাণ দিচ্ছেন।
বাংলা সাহিত্য জগতে
বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য লিখতে শুরু করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র
আলালের ঘরের দুলাল লিখে বাবুদের ফুঁটো করে দিয়েছেন। নাটক লিখছেন রামনারায়ণ
তর্কালঙ্কার—দীনবন্ধু মিত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
উনবিংশ শতাব্দির
প্রথমার্থে ইংরেজদের সাহচর্যে ও ইংরেজীসাহিত্যর হাত ধরে বাংলার স্রোতহীন জীবনে এক
আলোড়ন এসেছিল। দিয়েছিল ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে
নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দেশীয় ভাবধারা মিলিত হয়ে এক বিমিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।
উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর বিদেশী চিন্তাভূমির কর্ষণযন্ত্র দিয়ে বাঙালির
মানসভূমি বিদেশী সাহিত্যের ভাবরসে কর্ষিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে সেই
কর্ষিত ভূমিতেই বীজ বপন করে রাজনীতি শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই বাংলা
তখন ফসল ফলানো শুরু করেছে। বাংলা তখন এক নতুন সভ্যতার দরোজায় পৌঁছে গেছে।
গোটা উনিশ শতক ধরেই
কোলকাতার ঠাকুর পরিবার ব্যবসা বানিজ্য ও ইংরেজদের চাকরির বদৌলতে সমাজে সম্পদ, সামাজিক
সম্মান ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। দ্বারকানাথের সময়ে গেছে তা চূড়ান্ত
সীমায়। দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে সেসব হারিয়ে কেবল জমিদারিনির্ভর এক উচ্চবিত্ত
পরিবার হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।
এই আর্থিক অবনতির
সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পূজা অর্চনার অনুষ্ঠান ধর্মকর্মও বদলে গেছে। দেবেন্দ্রনাথ
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় সব ধরনের পৌত্তলিকতা বর্জন করেন। ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত
দুর্গাপূজা উঠে যায়। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ পুরোপুরি হিন্দুধর্মঅনুসারে না করায়
দেবেন্দ্রনাথকে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করেন। এইসব কারণে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বদলে
ঠাকুর পরিবার বেছে নেন কিছু অসাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠান—মাঘোৎসব,
বর্ষশেষ, নববর্ষ ইত্যাদি। এই
অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দেন অনাত্মীয়-- অন্যপথের লোকজন।
সে সময় ধনী পরিবারে
বাংলাভাষার বদলে ইংরেজি ভাষাই আদরণীয় ছিল। ঠাকুর পরিবারে ইংরেজি ভাষার বদলে বাংলা
ভাষায় কথা বার্তা বলা, চিঠিপত্র লে ও লেখাপড়াও
বাংলাভাষায় প্রচলন হয়। এই বাংলাভাষা ঠাকুরবাড়ির ভাষা নামে পরিচিত হয়েছিল। তারা
বেশভূষা, আদবকায়দা ও চালচলেনও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল।
এইভাবে তারা অর্থবিত্তের বদলে সাংস্কৃতিক অভিজাত্য অর্জন করেছিল।
ঠাকুরপরিবারের
দ্বারকানাথ ইউরোপে গিয়েছিলেন। তার ছেলে দেবেন্দ্রনাথ নিজে না গেলেও তার ছেলে-আত্মীয়স্বজনরা
লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ইংলন্ড যাওয়া শুরু করেছেন। ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্য দর্শন তারা
আত্মস্থ করলেও দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদের মাধ্যমে গভীরভাবে প্রাচীনভারতের সঙ্গে
ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার
লোকসস্কৃতির সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটেছে। ঠাকুরবাড়িতে যাত্রা পালাগান বাউলগানের
আসর বসেছে। আবার বিষ্ণ চক্রবর্তী নিধুবাবু রূপচাঁদপক্ষীদের ছড়া কালোয়াতি আখড়াই
গানের প্রবেশ ঘটেছে।
ঠাকুরবাড়িতে আশ্রিত
দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে, বাড়ির চাকর মহলের মাধ্যমে রূপকথা লোককথা পাঁচালিগানেরও
অবাধ প্রবাহ ছিল। এই সকলের মেলবন্ধনে ঠাকুরবাড়িতে পুরনোর সঙ্গে নতুনের সহযাত্রা
ঘটেছে। বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিরোধ নয়-- ঐক্যের জয়ধ্বনী ঘোষিত হয়েছে। ফলে শুধু
শিল্প সংস্কৃতির মত মানসপরিবর্তন নয়—ব্যবসা জমিদারীর ক্ষেত্রেও তাঁদের
দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছে। ফলে দেখা যায়—দ্বারকানাথের পরবর্তি প্রজন্ম আর ব্যবসায়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন
নি। নতুন করে জমিদারী-বিত্তবেসাত বাড়াতে পারেননি। কিন্তু মানবচিত্তবিদ্যায়
তাঁদের পূর্বপুরুষকে টপকে গেছেন।
শেকসপীয়র ওয়ালস্কট
প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের পাশাপাশি ঠাকুর পরিবার ফরাসী কাব্যসাহিত্যের দিকেও হাত
বাড়িয়েছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে
আত্মস্থ করেছেন। স্বদেশী সাহিত্যকে নব নব ভাবসম্পদে ও সৌন্দর্য পূর্ণ বিকশিত
করেছেন। ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত এসেছেন সেসময়কার প্রখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার
দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল
মধুসুদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের
জন্মের আগেই ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে সাহিত্যরসের সৃজনশীল ধারা পূর্ণমহিমায় প্রবাহমান
ছিল।
রামমোহনের সময় থেকেই
ব্রাহ্মধর্মসমাজে উপসনার অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ
কৃষ্ণ ও বিষ্ণু চক্রবর্তী নামে দুজন বেতনভোগী গায়ক ব্রাহ্মসমাজের গান গাইতেন এবং
গানের সুর দিতেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বেজেন্দ্রনাথ,
সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ অনেক হিন্দি
গান গান ভেঙ্গে বাংলায় ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। একা বিষ্ণু চক্রবর্তী ৬০০
গানের সুর দিয়েছেন। ঠাকুরবাড়িতে যদু ভট্ট গান শেখাতেন। দ্বারকানাথ নিজেও
ইউরোপীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন। সঙ্গীতের এই ধারা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়েছে।
এবাবে দেখা যায় ঠাকুরবাড়িতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।
চিত্রবিদ্যারও বাড়িতে
স্বাভাবিক ও সহজ চর্চা ছিল। গুণেন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন।
তাদের ধারাবাহিকতায় গগনেন্দ্রনাথের পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী
ছিলেন। এছাড়াও হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ,
সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুরেরও সহজাত শিল্পপ্রতিভা ছিল। এরা সবাই মিলে বাংলার শিল্পচর্চার ধারাটাই
পাল্টে দিয়েছিলেন।
ঠাকুরবাড়ির
ঘরগেরস্থালি
পিরালী ব্রাহ্মণ
হওয়ায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অভিজাত বা কুলীন ব্রাহ্মণেরা
বিবাহসম্পর্ক করত না। ফলে তাঁদের নিজস্ব পিরালী ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই বিয়েসাদি
হত। খুলনা-যশোর এলাকায় পিরারী থাক থাকায় এখান থেকে গরীব ঘর থেকে পাত্রী আনা হত।
ফলে বিয়ের পরে এই গরীব আত্মীয়স্বজনদের আশ্রয় হত ঠাকুরবাড়িতে। তাদের ভরণপোষণেরও
দ্বায়িত্ব নেওয়া হত। দেওয়া হত চাকরীবাকরী। ঠাকুর বাড়ির সেরেস্তায় বা
অন্যত্র কাজকর্ম করত। এরকম কজনের নামও পাওয়া যাচ্ছে। জ্যোতি, গুপি, পচা ও পুঁটে। জ্যোতি বাজার করত। গুপি দুধ দোহাত। পচা ও পুঁটে পাই ফরমাস
খাটত। ছেলেদের সঙ্গে খোসগল্প করত। তাদের বউয়েরাও মাঝে মাঝে এসে থাকত। আবার
দেশগাঁয়েও যেত বিষয়সম্পত্তি দেখার জন্য।
ঠাকুরবাড়ির
মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য যেসব পাত্র যোগাড় করা হত পেঁয়াজ খাওয়া ব্রাহ্ম
শ্বশুরের কারণে তাদের জাত যেত। ফলে তাদেরকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করে ঘরজামাই করে
রাখা হত। এভাবে ঠাকুরবাড়িতে এই আশ্রিত লোকজনেরা শাখাপ্রশাখা মিলে রীতিমত একটি কলোনীতে
রূপান্তরিত করে ফেলেছিল।
ঠাকুরবাড়ি ছিল
একান্নবর্তী পরিবার। ধান আসত জমিদারী থেকে। গোলাবাড়িতে মজুত হত। ঢেঁকিশালে ভানা
হত। রান্না হত এজমালি মাইনে করা ঠাকুরের হাতে। রান্নার মধ্যে ডাল, সবজি, মাছ, মাংস অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের
নদিদি স্বর্ণকুমারীর মেয়ে সরলাদেবী স্মৃতিচারণ করেছেন—
আমি যখন প্রায় পাঁচ
বছর বয়সে (১৮৭৭ সাল) জন্মপুরীতে ফিরে এসে তার হাওয়ায় মানুষ হতে লাগলাম, তখন সে পুরী
জমজম গমগম করছে। প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা মহাশয়ের (দেবেন্দ্রনাথ)
ছেলে মেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাতনি,
দাসদাসীতে বাড়ি ভরা। সে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারজন বামুন ঠাকুর
ভোর থেকে রান্না চড়ায়। সে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দুপাশে ভাগ করা মেঝেতে পরিস্কার
কাপড় পেতে ঢালা হয়। সে ভাত স্তুপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই
পরিমাণে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাতব্যঞ্জন ও রাত্রে লুচিতরকারি—লোক গুণে গুণে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে মহলে ঘরে ঘরে
দিয়ে আসে বামুনেরা।
...ঘরে ঘরে
বামুনেরা যে খাবার দিয়ে যেত সেটা হল সরকারি রান্নাঘরের যোগান, এর উপরে ছিল প্রতি মহলে তোলা উনুনে গিন্নিদের নিজের নিজের রুচি ও
স্বামীর ফরমান অনুযায়ী বেসরকারি বিশিষ্ট রান্না আলাদা করে হত।‘ তখন দিনে ১৩০ লিটার দুধ আসত। তখন টাকায় ছসের করে দুধ। সামনে এসে
দুইয়ে দিয়ে যেত গয়লারা। সে দুধে পুরো বন্যা বয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার।
জোড়াসাঁকোর বাড়িটি
ছিল কোলকাতার চিৎপুর রোডে। এটা ছিল আধা শহুরে আধা গ্রাম্য। রবীন্দ্রনাথ
লিখেছেন-তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা এরকম চেহারা লইয়া
প্রকাশ পাইত।
তখন চিৎপুর রাস্তায়
মেঘ কল্লে কাদা হয়। ধুলো উড়িয়ে স্যাকড়া ড়াড়ি চলে। ঘোড়ার গাড়ির চালায়
হাড়জিরজিরে ঘোড়া। তার পিঠে চাবুক পড়ে। বাসগাড়ি-রেলগাড়ি কখনো আসে নি।
তখন কোলকাতার লোকজন
খুব ঢিলেঢালা। কাজের চাপ খুব বেশী ছিল না। কেরানী বাবুরা তামাক খেয়ে পান চিবুতে
চিবুতে আফিসে যেতেন। পালকী বা ভাড়াগাড়ি তাদের নিয়ে যেত। টাকাওয়ালা বাবুদের
জন্য ছিল তকমা আঁকা গাড়ি। বক্সে পাগড়ীপরা কোচম্যান। পিছনে দুজন সহিস। তারা
পথচারী দেখলেই হেঁইয়ো হেঁইয়ো বলে পিলে চমকে দিত। মেয়েদের ঘরের দরোজা দরজা বন্ধ।
বাইরের দরোজাও বন্ধ। গাড়িতে চড়া ছিল লজ্জার। আর কেউ যদি মেয়েদের পা, মোজা বা সেমিজ
দেখে ফেললে লজ্জার শেষ নেই। তবু বাবুদের মেয়েরা পালকীতে চেপে কখনো কখনো বাইরে
যেত। পালকীর চারিদেকে মোটা কাপড় দিয়ে ঘেরা থাকত। পালকীর ভেতরটা অন্ধকার। গুমোট।
তাকে কেউ দেখতে পেত না। সেও কাউকে দেখত পেত না। এই পালকীটাকে চলমান গোরস্থানের মত
দেখতে ছিল। এদের পাশে পাশে পাহারাদার হিসাবে দেওয়ানজীরা চলত। তাদের মোটা গোঁফ।
মাথায় পাগড়ী। হাতে পিতলে বাঁধানো লাঠি। এই পাহারাদাররা ব্যাংকে বাবুদের সঙ্গে
যেত। কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছে দিত। আর পূজাপার্বনের দিনে বাড়ির গিন্নিকে
গঙ্গাতে পালকীশুদ্ধ চুবিয়ে আনত। এটা তাদের গঙ্গা স্নান। আর ছিল কোলকাতায় এখানে
ওখানে বিস্তর শুড়িখানা। মেদো মাতালদের হৈহুল্লা। ঠাকুরবাড়ির পাশেই ছিল কোলকাতার
সবচেয়ে বড় বেশ্যাপাড়া।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর
বাড়ির ফটক পেরিয়ে দুটি বাড়ি ছিল একই প্রাঙ্গনে। একটির নাম আদিবাড়ি বা আদি
ভদ্রাসন বাড়ি। অন্যটি বৈঠকখানা বাড়ি। প্রথমটি দোতলা। আর দ্বিতীয়টি তেতলা।
অনেকগুলো ঘর, অনেকগুলো মহল আর অনেকখানি বাগান জুড়ে এই দুই বাড়ি মিলিয়ে এক বাড়ি।
বাড়ির ঈশানকোণে বিশাল
এক তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ছায়ায় ছিল ছিরু মেথরদের ঘর। বাহির-বাড়িতে
দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চাকরদের মহল। এ ঘরে বালক রবীন্দ্রনাথদের দিন কাটত।
পুকুরের ধারে তারা গয়লানির গোয়াল ঘর।
দেবেন্দ্রনাথ
বৈঠকখানার বাড়িটি গিরীন্দ্রনাথদের ছেড়ে দিয়ে আদি ভদ্রাসন বাড়িটিতে চলে আসেন।
পরে এই বাড়িটিকে তেতলা করা হয়।
ঠাকুরবাড়ির অন্ধকার
আর ভেতরবাড়িতে
একতলায় আলোবাতাসহীন ছোটো ছোটো ঘরগুলিতে গ্রাম থেকে আগত আত্মীয় স্বজনদের বাস।
রবীন্দ্রনাথ নারী শিক্ষা নামে এক বক্তৃতায় লিখেছেন—
ছেলেবেলা থেকে আমাদের
বাড়িতে দেখেছি কত নিঃসহায় অনাথা স্থান পেয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়িটি তাদের বসবাসে
একেবারে পায়রার খোপের মত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অধিবাসিনীদের অবস্থা ছিল তখন অতি
শোচনীয় ছিল। তাদের অশিক্ষিত মন আত্মাবমাননাতে পূর্ণ হয়ে থাকত। তারা কোথাও
আত্মমর্যাদা অনুভব করতে পারেনি। তখনকার দিনে দেশের অন্যান্য মেয়েদের মত তারা
অভ্যস্ত অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা পরস্পরে ঈর্ষা করেছে, নিজেদের মধ্যে
বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা যতরকম কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়েছে। মানুষের জগতে তাদের স্থান
কত তলায়, তা বোধ করবার শক্তি তাদের ছিল না। এর ফলে
হয়েছিল বাড়িময় অশান্তি, পরস্পরের লাগালাগি ও কলহ
বিবাদ।
ওদের সামনে জীবনের সকল
পথই রুদ্ধ, সংকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর আশ্রয়ে পরের অনুগ্রহের জুয়াখেলায় তাদের
রাত্রিদিন কলুষিত।
এই আলোঅন্ধকারের ভেতর
থেকে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। শিখেছেন রবীন্দ্রগিরি।
জ্যোতিরিন্দ্র ৪৬ টি
বই লিখেছেন। অসাধারণ স্কেচ করেছেন। বিখ্যাত চিত্রকর রোদেন স্টাইন
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই স্কেচ দেখে মন্তব্য করেছেন-
তিনি পেশাদার চিত্রকর
নন।...তার অঙ্কিত মুখগুলিতে যে রেখা ও
অবয়বের সংবেদনশীলতা দেখা তা ব্স্মিয়কর। আর আমার মনে হয়েছে, ছবিগুলি আঁকা
হয়েছে নিরতিশয় স্বাভাবিকতার সঙ্গে। পাশ্চাত্য রীতিঅনুসরণ করবার অতিমাত্রিক
প্রবণতা তাঁর মধ্যে নেই। আবার মুঘল ধারা অনুসরণ করবার সচেতন ঝোঁকও তার মধ্যে লক্ষ
করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তাঁর আঁকা ভারতীয় মহিলাদের ছবিগুলি বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য। তার চিত্রশৈলী সরল ও বিনয়পূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটি ড্রয়িং দেখে
অনুভব করা যায় যে তাঁর মডেলের অন্তর্লীন অবয়বের সুকুমারত্ব এবং চরিত্রের বিশেষত্ব
ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় তিনি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন।
আমরা অভ্যস্থ হয়ে
গেছি জমকালো পোষাক পরা মহারাজাদের ছবিই কেবল দেখতে, বা
ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মানুষের ছবি দেখতে। এইসব সংস্কৃতিবান,
রুচিবান, ভদ্র ভারতীয় নারী আর পুরুষের
সম্পর্কে কমই জানি আমরা। তাই এই সোজাসুজি আঁকা ছবিগুলি দেখা আমাদের কাছে এক
অত্যন্ত আনন্দজনক অভিজ্ঞতা।
রবীন্দ্রনাথকেও
পরবর্তিকালে ছবি আঁকতে দেখা যায়। তিনিও নতুন দাদার পথে এঁকেছেন সাধারণ মানুষ আর
প্রকৃতির ছবি। এইখানে এসে বোঝা যায় দাদার হাত ধরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছোটো ছেলেটি
তার ভেতরে বংশধারায় পাওয়া জমিদারী মুখোশটি ছুড়ে ফেলে মানুষের মুখটিকে স্থাপন
করে নিয়েছেন। তিনি অন্যমানুষ। তিনি দ্বারকানাথের মত ব্যবসাদার নন। দেবেন্দ্রনাথের
মত ধর্মমার্গী নন। তার পেশা আসমানদারী। তাঁর শেকড়টি মাটিতে, মানুষে,
প্রাণে—বিশ্বের মহাপ্রাণে।
গ্রন্থসূত্র :
---------
১. রবিজীবনী-:-প্রশান্তকুমার
পাল
২.রবিজীবনকথা-:-প্রভাতকুমার
মুখোপাধ্যায়
৩. রবীন্দ্রনাথের
আত্মীয়স্বজন -- সমীর সেনগুপ্ত
৪. ছিন্নপত্র :
রবীন্দ্রনাথ
৫. হাজার বছরের বাঙাল
সংস্কৃতি গোলাম মুরশিদ
৬. জমিদার রবীন্দ্রনাথ
: শিলাইদহ পর্ব : অমিতাভ চৌধুরী
৭. রবীন্দ্রনাথ ও
রবীন্দ্রনাথ : তপন চট্টোপাধ্যায়
৮. স্মৃতিসম্পুট, রবীন্দ্রস্মৃতি;
পুরাতনী--ইন্দিরা দেবী :
৯. ঐতিহাসিক
অনৈতিহাসিক : শ্রীপান্থ
১০. শাহজাদা
দ্বারাশুকো : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
১১. কলকাতা একাল ও
সেকাল : রথিন মিত্র
১২. রামমোহন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা
: সুরজিৎ দাশগুপ্ত
১৩. ভারত সন্ধানে :
জওহর লাল নেহেরু
১৪. রবি ঠাকুর, রাহাজানি এবং রবীন্দ্র
পূজারীবৃন্দ :ফরিদ আহমদ ও অভিজিৎ রায়
১৫.
রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ : ফরহাদ মজহার
১৬. ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ
১৭. বঙ্গীয়
শব্দার্থকোষ : কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী
১৮. The Nabobs :
Percival Spear
১৯.The Annals of
Rural Bengal : W W Hunter
২০. জোব
চার্নক ও কলকাতার জন্মদিন : গৌতম বসুমল্লিক
২১. মহাভারত
সারানুবাদ : রাজেশেখর বসু



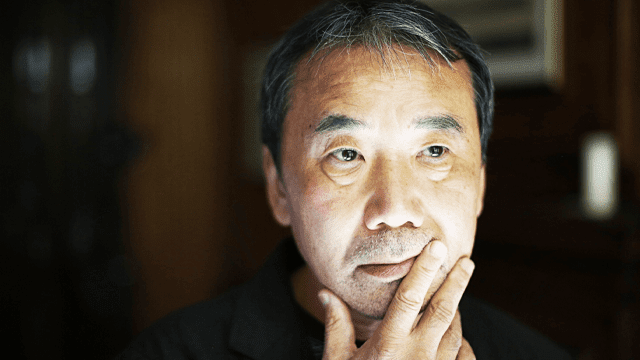







0 Comments