এক.
১৯৩১ সালে ৬ সেপ্টেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন।
...একদিন আমার একজন মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে এক টাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবী করি নি। সে বললে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য।
এ চিঠিতে তিনটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ১. মুসলমান প্রজাদের অন্ন তিনি ভোগ করেছেন—এটা রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। ২. মুসলমান প্রজারা তাকে ভালোবাসে। ৩. রবীন্দ্রনাথ মুসলমান প্রজাদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসার কারণ তার এই মুসলমান প্রজারা ভালোবাসার যোগ্য।
পূর্ববঙ্গে আসার আগে মুসলমানদের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল না। ছেলেবেলায় হিন্দুমেলায় মুসলমান বয়াতির গান শুনেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ ফারসি কবি হাফিজের অনুরাগী ছিলেন। ছেলেবেলায় বাবার কাছে হাফিজের কবিতার শুনতেন। দেবেন্দ্রনাথ ফারসি ভাষা জানতেন। তিনি মূল ফারসিতে আবৃত্তি করতেন। সঙ্গে সেগুলোর বাংলা অনুবাদ শোনাতেন। সে কবিতার মাধূর্য বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। তিনি বলেছেন, কবিতা পারসিক হলেও তার বানী সব মানুষের। ১৯৩২ সালে ইরানে গিয়েছিলেন কবি। হাফিজের সমাধির পাশে সমবেত কবিদের বলেছিলেন, এই ফারসি সুধা তার বাবাকে জীবনান্তকাল পর্যন্ত সান্ত্বনা দিয়েছে।
এ সূত্রেই ঠাকুর পরিবারে উদার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পড়েছেন ফারসী, আরবী, তুর্কী সাহিত্য। জেনেছেন ইসলামী দর্শন, ইতাহাস, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে। তিনি জেনেছেন—ঈশ্বর এক। তার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তিনি সকল বর্ণের। সকল জাতির। এবং জীবনের একটা পর্যায়ে এসে তিনি অনুভব করেন—পূর্ববঙ্গে নতুন করে পাওয়া প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের বিশালতা তার ভাবজগতে পরিবর্তন এনেছে—তার ধর্মচিন্তা, রাজনৈতিক ভাবনা, দর্শন তত্ত্ব, সাহিত্যবোধ, জীবনবোধ পাল্টে গেছে। তার ভেতরের মানুষটার পুরনো বাবুপরিবারের পুরনো খোলসটা ১৮৯১ সালে শিলাইদহে যাওয়ার পরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়েছে। তিনি ভেবেছেন শুধু ভাবজগতের এই খোলস বদলের সঙ্গে তার বহিরাঙ্গের পোষাকটিরও বদল হওয়া দরকার। পোষাকটি হিন্দুরও নয়—মুসলমানেরও নয়। খ্রীস্টান বা বৌদ্ধেরও নয়। বাউলদের আদলে করা হয়েছিল এই আলখেল্লা নামের পোষাকটি। করেছিলেন প্রিয় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পোষাকটি আর পাল্টান নি-- সারা জীবন ধরে পরেছেন।
একটি ঘটনা জানা যাচ্ছে ১৯১১ সালের নভেম্বরের। শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর পুত্রকে ভর্তি করার প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রবন্ধে হিন্দু ও মুসলমানকে সমীপবর্তি করার যে পরামর্শ দিচ্ছিলেন তাকেই বাস্তব রূপ দেবার এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মুসলমান ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সে সময় বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনের অন্যতম ট্রাস্টি। তার কাছ থেকে বাঁধা আসার আশঙ্কা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ২৬ অক্টোবর কলকাতা থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেপালচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে তাঁকে ভর্তি করে কথা বলেন। কিন্তু নেপালচন্দ্রের নিকট থেকে অনুকুল উত্তর পান নি। সে সময়কার ছাত্র-শিক্ষক ও দিপেন্দ্রনাথনাথ ছেলেটিকে ভর্তি করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তখন রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্রকে ২ নভেম্বর ১৯১১ সালে আরেকটি চিঠি লেখেন—
মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একজন চাকর দিতে তাহার পিতা রাজী। অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে খাইবেন। শুধু তাই নয়—সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যুথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না?...প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারের আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না—যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাহার নাম করিয়া প্রসন্ন মনে নিশ্চিন্ত চিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন; আপাতত যদিবা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।
রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টা সত্ত্বেও শান্তি নিকেতনে বালকটিকে সে সময়ে ভর্তি করানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু দশ বছর পরে বিদ্যালয়ের বিশ্বভারতী পর্বে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন।
১৮৯১ সালের লোক গণনার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, নদীর শতকরা ৫৮ জন অধিবাসী ছিলেন মুসলমান। ৪২ জন হিন্দু। এর মধ্যে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে মুসলামানদের সংখ্যা তুলানামূলকভাবে বেশি ছিল। কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল। বর্ণভেদে নদীয়া জেলার হিন্দুদের সংখ্যার অনুপাতটি ছিল নিম্নরূপ—
কামার- ৮%, সদগোপ—৮%, কৈবর্ত—৬%, চামার—২.৭%, গোয়ালা—৫%, বাগদী—২%, তেলি—১.৫%, মালো—২.৩%, কুমোর—১%। মোট—৩৫.৫০%
ব্রাহ্মণ—৩%, কায়স্থ—২%। মোট—৫%।
এই শতকরা ৪২ জন হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ওরা ছিলেন তথাকথিত ভদ্রলোক। এরাই ছিলেন জমিদার, তালুকদার, আমলা, ব্যবসা-বানিজ্যের অধিকর্তা। এদের মধ্যে কায়স্থ শ্রেণীরাই ছিলেন ব্যবসায়ী। ঐ এলাকার যে মহাজন-সুদের কারবারী শোষণ শ্রেণী ছিল এই কায়স্থ বা সাহা শ্রেণীর অন্তর্গত। হিন্দুদের মধ্যে ৭.৬% ছিল শিক্ষিত। এই শিক্ষিত হিন্দুদের সিংহভাগই উচ্চবর্ণের। ব্রাহ্মণ—২৭.৫ জন। কায়স্থ—১৬.৪ জন এবং বৈদ্য ৩২ জন।
মুসলমানদের সিংহভাগই ছল দরিদ্র। শিক্ষার হারও ছিল মাত্র ১.৬ জন।
তাহলে দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশেরও বেশি অধিবাসী ছির দরিদ্র, অশিক্ষিত—নিম্নবর্ণজ, বৃত্তির দিক থেকেও নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নবিত্তের। এরাই মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন।
স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত বিপুল জনতা তাদের কৌলিক বৃত্তিক উপর নির্ভরশীল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে এই মানুষদের প্রায় সকলেই জমি থেকে তাদের জীবিকা উপার্জন করতেন। স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি যে—এদের আয় ছিল অতি নগন্য।
শিলাইদহের অধিকাংশ চরের অধিবাসী ছিল মুসলমান। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তারা খাজনা দিতে চাইত না। ফলে জমিদারের নায়েব-গোমস্তা-আমিনদের সঙ্গে তাদের ঝামেলা লেগেই থাকত। লাঠিয়ালরা এসে লাঠির ঘায়ে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করত। আবার মুসলমান প্রজারা তাদের রুখে দাড়াত। পাল্টা আঘাত করতে ভয় পেত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে এই এলাকায় এলেন—তিনি সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করলেন। তাদের কাছে গেলেন। তাদের বশ করলেন—লাঠির আঘাত দিয়ে নয়—ভালোবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে। ন্যায়-নীতি ও মানবিকতা বোধ দিয়ে। তিনি আস্থা অর্জন করেছিলেন সকল শ্রেণীর বর্ণের ধর্মের সম্প্রদায়ের মানুষের। শিলাইদহের চরের বিদ্রোহী প্রজাদের সর্দার ইসমাইল মোল্লা রবীন্দ্রনাথের শালিসী খুশী মনে মেনে নিয়েছেন। মুসলমান প্রধান কালিগ্রামের সব প্রজা জমিদারের সঙ্গে তাদের মধ্যেকার স্বার্থ ভাগ করে নিচ্ছে। এর আগে এই কাজটি ঠাকুর-এস্টেটের কোনো ম্যানেজার করতে পারেন নি। কখনো কখনো তারা সমস্যারটির সমাধান না করে জিঁইয়ে রেখেছেন।
ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে ইন্দিরাকে তিনি লিখেছেন --একটি তিনি পতিসরের মাঠে গিয়েছেন। সেদিন একজন অতিময় দরিদ্র প্রজা তাঁর পায়ের ধূলো নিতে এসেছে। প্রজাটি অসুস্থ। অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য তিন ধরে উপবাস করছে। তার ধারনা—এই অন্যরকম জমিদারের পায়ের ধূলো নিলে তার অসুখ সেরে যাবে। এটা তার গভীর বিশ্বাস। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন-- রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রামের মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কফিলুদ্দিন বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান ফসলের পোকামাকড় মারার কৌশল নিয়ে আলাপ করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
পূর্ববঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করার সময়ে তিনি অধিকাংশ সময়ই নদীর উপরে বজরা বোটে থাকতে পছন্দ করতেন। তার বজরার প্রধান মাঝির নাম ছিল মেছের আলি। আর মুসলমান বাবুর্চির রান্না তিনি খেতেন। বাবুর্চির নাম ছিল গফুর। কুঠিবাড়ির বাবুর্চির নাম ছিল মোমিন মিঞা। মোমিন মিঞার নাম তিনি নাটকেও লিখেছেন।
আবুল হাসান চৌধুরী ডঃ আহমদ শরীফকে ১৮৯৫ সালে চিঠিতে লিখেছিলেন, চরের মুসলমান প্রজাদের উচ্ছেদ করে সেখানে নমশুদ্র প্রজা বসানোর পরিকল্পনাটা রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। তিনি এই হীনপরিকল্পনাটির কোনো প্রমাণ সেখানে দেন নি। বা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেন নি। কিন্তু ২০১১ সালে সেই আবুল আহসানই সেই পুরণো চিঠিটির হীনপরিকল্পনাটিকে নাকচ করেছেন। তিনি বিস্তারিত প্রমাণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ লিখেছেন—মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়-গভীর-আত্মিক।..তিনি এদেরকে এতটাই বশ করেছিলেন যে, যখন শিলাইদহের জমিদারী রবীন্দ্রনাথের হাতছাড়া হয়ে গেছে, নতুন মালিক তাঁর ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথকে আসতে হলো চরের অধিবাসী মুসলমান প্রজারা আবার বিদ্রোহী হয়েছে বলে।
১৯২০ সালে ঠাকুর এস্টেটের জমিদারী ভাগ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাতের ভাগে পড়ে কালিগ্রাম জমিদারী। শিলা্ইদহ-সাহাজাদপুরের বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারী অংশটি পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিলাইদহ ও পদ্মা আর তাঁর নিজের রইল না। সুরেন্দ্রনাথও জমিদারী পরিচালনা করতে আসেন নি। তিনি নায়েব-গোমস্তাদের হাতে জমিদারী ছেড়ে দেন। ফলে প্রজা অসন্তোষ দেখা দেয়। আরও পরে সুরেন্দ্রনাথ সে জমিদারী রক্ষা করতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবারের কাছে এই সম্পত্তি বেঁচে দেন।
রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে শেষবারের মতন এলেন এই চরের প্রজাদের মনের-মতের পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে। তাদের যে অসন্তোষ, তারা যে জমিদারকে মানতে চাচ্ছে না বা সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যে খুব ভালো হয়ে উঠছে না, সেটা মেটানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন।
২৩ মার্চ ১৯২২ তারিখে রাত্রের ট্রেনে করে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আ্যান্ডরুজকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে রওনা হন। ২৪ মার্চ শিলাইদহে পৌঁছান। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন-- শিলাইদহে এসে তার ভালো লাগছে। এদিন তিনি রচনা করলেন পূর্বাচলের পানে তাকাই গানটি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে গানটি পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন—পুরনো শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ঢিলে হয়ে গেচে। কর্তব্য জগতের বিপুল যে-একটা ভারাকর্ষণ ছিল সেটা ফস করে আমার চারদিক থেকে খসে পড়েছে। গুরুতর দ্বায়িত্ব বলে যে সমস্ত পদার্থকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতুম হঠাৎ তাদের কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে। এটা তার শিলাইদহে শেষ আগমন। তিনি ২৫ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত চারটি গান লেখেন। আসা-যাওয়ার পথের ধারে, কার যেন এই মনের বেদন, নিদ্রাহারা রাতের এ গান, এক ফাগুনের গান সে আমার।
শিলাইদহটি তিনি মন থেকে ভালো বেসেছিলেন। এটা চলে তাঁর হাত থেকে চলে যাওয়ায় বেদনা পেয়েছিলেন। ৫ এপ্রিল ১৯২২ তারিখে রাণু অধিকারীকে একটি চিঠি লেখেন শিলাইদহ থেকে--
আগে পদ্মা কাছে ছিল—একন নদী বহু দূরে সরে গেছে---আমার তেতলা ঘরের জানলা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি। অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল—শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত। রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতাম। তার পরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতবার সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না; ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল,--সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের একটি নীলতর পাড়ের মত একটি বনরেখা দেখা যায়, সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি ঐ আমার পদ্মা, আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়ে রয়েছে। এই ত মানুষের জীবন, ক্রমেই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিষ ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মত প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মত জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।
এখানে দুসপ্তাহ ছিলেন। সঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিএফ এন্ডরুজ। ২১ শে চৈত্র গ্রামবাসীরা কবি ও এন্ডরুজ সাহেবকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানান। এই সভায় একাধিক মানপত্র দেওয়া হয়। এদিনই শিলাইদহ অঞ্চলের মুসলমান মহিলাদের পক্ষ থেকে কবিকে একটি নকশি কাঁথা উপহার দেওয়া হয়। এটি বর্তমানে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। শিলাইদহ জমিদারীর প্রজারের পক্ষ মানপত্রটি রচনা করেছিলেন জেহের আলী বিশ্বাস বলে চর কলারোয়া গ্রামের একজন মুসলমান প্রজা। তিনি লেখেন—আজ আমাদের কী আনন্দে দিন...সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শরবেণুরবে গাইছে—ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।
তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। আর কিছু নয়। জেহের আলী বিশ্বাস রচিত বিরাট এই মানপত্রের শেষ দিকে বলা হয়—
সমুদ্রমন্থন করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিযা অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে আনন্দটুকু পেয়েছি, আর যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে :
১. গৃহস্থেরা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে; তবু তাহাদিগকে দুমুঠো ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিরূপে তাদের এই দুরাবস্থা দূর হইতে পারে এই সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।
২. দেশ হইতে হাজার হাজার মন শস্য সস্তা দরে বিদেশে চলিয়া যাচ্ছে, আর বিদেশ থেকে যা আসছে তা তাহাদিগকে আতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হচ্ছে। তার প্রতিকারের উপায় কি, এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।
৩. বর্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকের কি কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।
৪. দেশে গরীবের ছেলে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে সহায় অভাবে জীবনে উন্নতির দিকে যাইতে পারে না জন্য ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।
অতএব প্রার্থনা, অধীনগণের এই ক্ষুদ্র এ আকিঞ্চন গ্রহণ করিলে জীবনে ধন্য হইব। নিবেদন ইতি। ১৩২৮। ২১ চৈত্র।
‘জগৎপূজ্য কবিসম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু’ নামে খোরসেদপুরের অধিবাসিবৃন্দ মানপত্রে লেখেন—
…আবার এসেছে ফিরে এ পল্লীর আনন্দ দুলাল
দশদিক আকুলিয়া পত্র পুষ্পে সেজে ওঠ কদম্ব তমাল।
শাখে শাখে ডাকে পাখি দাঁড়াইলা পল্লী আজি উৎসব সজ্জায়
কবীন্দ্রের চরণের তলে, অর্ঘ্য করে নতমুখী সেবিকার প্রায়।।…
১৯৩৭ সালে পতিসরের প্রজাদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সে বছরের পূন্যাহে (১০ শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)পতিসরে আসেন। সেখান থেকে কালীগ্রামে। এখানে কবি বারো বছর পরে এলেন। তখন থাকতেন বোটে। কবির আগমণ উপলক্ষে রসুনচৌকি আর দিশি বাদ্যভাণ্ডের ধ্বনিতে সরগরম হয়ে উঠল গ্রামগুলি। পরের দিন সংবর্ধনা জানাবার বিপুল আয়োজন করেছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় পতিসর হাইস্কুলে বসেছে অভিনন্দন সভা। পুষ্পমাল্যে বরণ করা হল কবিকে। স্থানীয় জনসাধারণের অনেকেই বক্তৃতা করলেন। কবিও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন—‘’সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে, তোমাদের দেখে যাবো—আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমরা এগিয়ে চলো,--জনসাধারণের জন্যে সবার আগে চাই শিক্ষা—‘এডুকেশন ফার্স্ট’, সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বাঁচাও, মানুষ করো।‘’ অনেক বৃদ্ধপ্রজা, যুবকেরাও ভাবাবেগে কেঁদে ফেললেন, কবির কণ্ঠও যেন রুদ্ধ।
বড়ো আকারের অভিনন্দন সভাটি অনুষ্ঠিত হল কাছারি প্রাঙ্গণে। জনৈক মুসলমান প্রজা অভিনন্দন পাঠ করলেন—
মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি—
প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা।
দেবতার দান অক্ষয় হউক, হৃদিপটে থাক স্মৃতিকথা।।
কালীগ্রাম পরগণার প্রজাবৃন্দের পক্ষে—
মোঃ কফিলদ্দিন আকন্দ রাতোয়ান।
পতিসর, সদর কাছারী, রাজশাহী, ১২ শ্রাবণ, ১৩৪৪।
পতিসরের একটি ঘটনা বলেছেন অন্নদা শঙ্কর রায়। তখন তিনি রাজশাহীর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথ পতিসরে এলে তার সঙ্গে অন্নদা শঙ্কর রায় দেখা করতে গেছেন। সেখানে একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার কাছে মন্তব্য করেছেন যে—আমাদের ধর্মের মহামানবকে আমরা দেখিনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখলে তেমনই মনে হয়।
সে সময়কার একটি ছবি শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বইতে আছে যে চরের প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন চরের ভেতর দাঁড়িয়ে। মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কটাই নির্দেশ করে এ ছবিটি।
১৮৯১ সালে জমিদারি পরিচালনা করতে এসে রবীন্দ্রনাথ মহাজনী প্রথার সর্বনাশা রূপটি দেখেছিলেন। সে সময়ের মহাজনদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহা পরিবারের লোকজন। তিনি সে সময় ঘোষণা করেছিলেন—সাহাদের হাত থেকে শেখদের রক্ষা করাই আমার প্রথম কর্তব্য। তার জমিদারী এলাকার অধিকাংশ প্রজাই ছিল দরিদ্র এবং মুসলমান। শেখ বলতে এই দরিদ্র প্রজাদেরই বুঝিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ যেসব পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন—যেমন কৃষি ব্যাংক খুলে দরিদ্রপ্রজাদের ঋণ প্রদান, মণ্ডলী প্রথার মাধ্যমে সমবায় প্রথায় চাষ পদ্ধতি প্রচলন, তাঁত-রেশমের প্রশিক্ষণ স্কুল খোলা, উন্নত কৃষি প্রদ্ধতির প্রচলন, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি-- সেগুলো সরাসরি আঘাত করেছিল কায়েমী স্বার্থের রক্ষক হিন্দু গোমস্তা, আমলা, মাহজন এবং জোতদারদের দূর্গে। ফলে শিলাইদহ এলাকায় তিনি সব সময় এদের দ্বারা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছিলেন। তারা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্বেষ প্রচার করেছিল। তারা রবীন্দ্রনাথের জেদ আর কল্যাণব্রতের সামনে বিপন্ন বোধ করেছিলেন। ঠাকুর-এস্টেটের অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান। তারা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সব ধরনের কল্যাণকর্মে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিল। এ কারণেই তারা তাকে ভালোবাসত। তাকে ভক্তি করত। কায়েমী স্বার্থবাদীরা সে সময় প্রচার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম বলে মুসলমানদের প্রতি তার এত প্রীতি।
জমিদারী পরিচালনার কাছে এসে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সম্পর্ক পরিচয় ওঠে এই নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে। পল্লীর সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ইংরেজ রাজত্বে এই সমাজ ও অর্থনীতি উভয়েরই পরিবর্তন ঘটেছিল। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাতে পুরনো সমাজকাঠামোর অবক্ষয় তাকে বিস্মিত করেছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন—নতুন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষীয় এককালীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ স্টেটের কাছে মর্মান্তিকভাবে আত্মবিলোপ করতে বাধ্য হচ্ছে। এবং দেখেছিলেন—পল্লীতে এই দরিদ্য মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনটাই বড়। সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার ছিদ্র ধনীদের মধ্যেই গোপনে গোপনে আছে। সেখানে বাইরে থেকে রোগজীবাণু সংক্রমণ ঘটলেও ঘটতে পারে।
মুসলমান খণ্ড—২
হযরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বাণী পাঠিয়েছিলেন স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দিকে। ১৯৩৪ সালের ২৫ জুন ঔই বাণীটি হযরত মোহম্মদের জন্মদিনে আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—
ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে উহার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করিতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা ইহা সম্ভবপর হইবে না। তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির উৎসারিত। অদ্যকার এই পূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্য আমার ভক্তি-উপহার অর্পন করিয়া ঊৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সাত্ত্বনা কামনা করি।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীর ৩য় খণ্ড জানিয়েছেন, বানীটির ইংরেজী পাঠও আছে। ইংরেজী পাঠটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন। বাংলা পাঠে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদকে মহাঋষি হিসাবে অভিহিত করেছিলেন কবি। কিন্তু ইংরেজী পাঠে তিনি মহাঋষি শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন—Grand Propfet of Islam.
১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর নবী দিবস উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ বোম্বের আনজুমানে আহমদিয়ার সম্পাদককে—
Message to the Secretary, Anjuman Ahmadiya, Bombay, on Prophet Day—
Islam is one of the greatest religious od the world and the responsibility is immense upon its followers who must in their lives bear testimony to the greatness of their faith. Our one hope of mutual reconciliation between different communities inhabiting India, of bringing about a truly civilized attitude of mind towards each other in this unfortunate country depends not merely on the realization of an intelligent self-interest but on the eternal source of inspiration that comes from the beloved of God and lovers of men. I take advantage of this auspicious occasion today when I may join my moslem brothers in offering my homage of adoration to the grand prophet of Islam and invoke his blessings for India which is in dire need of success and solace.
Rabindranath Tagore
26.11.1933.
দিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত The Peshwa পত্রিকার নবী সংখ্যার জন্য ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ গ্রন্থে ভূঁইয়া ইকবাল সেই বানীটি শান্তি নিকেতনের রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগার থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।
Message for the Prophet Number of The Peshwa, Jama Masjid, Delhi.
I take this opportunity to offer my veneration to the Holy Prophet Mohammad, one of the greatest personalities born in the world, who has brought a new and latent force of life into human history, a vigorous ideal of purity in religion, and I earnestly pray that those who follow his path will justify their Noble faith in their life and the sublime teaching of their master by serving the cause of civilization in building the history of the modern India, helping to maintain peace and mutual goodwill in the field of our national life.
Rabindranath Tagore.Santiniketon
27the February 1936.
প্রথম বাণীটিতে রবীন্দ্রনাথ ইসলামের প্রবর্তকের নাম সরাসরি বলেন নি। তিনি তার স্বভাবসুলভ ভাষায় মহাঋষি বলেছেন। দ্বিতীয় বাণীটি প্রথম বাণীটিরই অনুবাদ। সেখানে ইসলামের মহাঋষি শব্দের বদলে প্রোফেট বা নবী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় বাণীটিতে সুস্পষ্টভাবে পবিত্র নবী মোহাম্মদ হিসাবে অভিহিত করেছেন।
শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তিনজন ধর্মপ্রবতর্কের নাম করেছেন। নামের তালিকা দেখলে বোঝা যায়—তিনি বয়স হিসাবে সিনিয়রিটি নির্ধারিত করেছেন। শুরুতে গৌতম বুদ্ধ, দ্বিতীয়টিতে যীশু এবং সবশেষে হযরত মহম্মদকে আলোচনায় এনেছেন। তিনি তিনজনের মধ্যেই মানুষত্বের সংগ্রামে তাঁদের আত্মনিবেদনকে সভ্যতার বড় অবদান হিসাবে দেখেছেন। লিখেছেন—
নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিষ তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ মন্ত্র পড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে– মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গন্ডির বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্মপনথীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ। কিন্তু, তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে যিশুকে মরু-প্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদন্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।
মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খন্ড খন্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে অন্তরের দিকে, অখন্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্য সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।
মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিতমূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে, সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।
মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে, সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।
পূর্ববঙ্গে যে বছর এসেছিলেন জমিদারী পরিচালনা করতে সেই ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অর্ধশতকে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্যক ধারণা পান এবং তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন অকাতরে। শুরু করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা সাধনায় মুসলমান মহিলা নামে প্রবন্ধ লিখে। পরিচয় পত্রিকায় কালান্তর পর্যন্ত নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে ৩০টিরও বেশী প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর গভীর বিশ্লেষণী অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি কিছু বানিয়ে লেখেন নি। পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের জীবনকে কাছ থেকে দেখেই তিনি লিখেছেন। এখানেই তাঁর লেখাটার শক্তি।
১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। নানা রোগে শোকে জীর্ণশীর্ণ। নিজের হাতে লিখতেও পারেন না। হাত কাঁপে। তখন ১২ ভাদ্র সিরাজগঞ্জ থেকে আবুল মনসুর এলাহী বক্স এসেছিলেন শান্তি নিকেতনে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এলাহী বক্স সিরাজগঞ্জে সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেবক নামে এই মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। তাকে রবীন্দ্রনাথ অটোগ্রাফ দিয়ে লিখেছেন—
যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।।
মৌলানা জিয়াউদ্দিন বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। পরে বিশ্বভারতীর ইসলামি সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ি অসৃতসর, পাঞ্জাব। তিনি সদ-বন্দ-ই টেগোর নামে ১০০টি রবীন্দ্রকবিতা ও গানের ফারসীতে ও কলম-ই টেগোর নামে কবিতার উর্দু তরজমা করেন। বই দুটিই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ১৯২২ সালে ২৪ জুলাই শান্তি নিকেতনে সুফি ধর্ম বিষয়ে মৌলনা জিয়াউদ্দিন প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২৩ সালে ১৬ মার্চ শান্তি নিকেতনে জিয়াউদ্দিন কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন এবং ইংরেজীতে তার অনুবাদ পাঠ করেন।
মৌলানা জিয়াউদ্দিন শান্তি নিকেতনের বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িত ছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীতে ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগকে একটি শক্ত ভিত্তির উপরদাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুমরণ করেন ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে। কবি গভীর ভাবে শোকাহত হন। রবীন্দ্রনাথ ৮ জুলাই মৌলানা জিয়াউদ্দিন নামে ৪৮ লাইনের একটি কবিতা লেখেন। শান্তি নিকেতনে সে সময় একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মৌলানা স্মরণে একটি দীর্ঘ ভাষণও দেন। মিসেস জিয়াউদ্দিনকে ৬ জুলাই টেলিগ্রামে শোকবার্তা পাঠান –
Ziauddin’s passing away is a terrible blow to me personally and Santiniketon. Rabindranath Tagore.
6.7.38.
ভাষণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—
আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরো অনেক গভীর।
জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হাল্কা মেঘের মতো। জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ কথা ভাবতে পারি নে। কারণ তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোতভাবে আশ্রমের সব-কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।
তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন করে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে, যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্বতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মতো তেমনি করে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সংকোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে আমরা এক জন পরম সুহৃদকে হারালাম।
মৌলানা জিয়াউদ্দিন/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে;
"এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
"বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়,
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্যভারে ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী,
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই--
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে--
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি--
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি--
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দমহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়--
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভনিশ্বাসে।
শান্তিনিকেতন,
৮ জুলাই, ১৯৩৮
১৯২১ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় সৈয়দ মুজতবা আলী ঈদ উৎসব নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। নসিরুল্লাহ এ বৎসর শান্তিনিকেতনে কিছুকাল উর্দু শেখান।১৯২৩ সালে সৈয়দ মুজতবা আলীর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় রামচন্দ্র নামে এক প্রাবন্ধিক The little I know of Islam পাঠ করেন।
১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের কাজী আব্দুল ওদুদ শান্তি নিকেতনে নিজাম বক্তৃতা করেন। কাজী আব্দুর ওদুদ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক। ১৯৩৫ সালে ২৬-২৮ মার্চ তিনদিন তিনি শান্তি নিকেতনে তিনটি বক্তৃতা দেন। তিনটির বিষয়—মুসলমানের পরিচয়, হৃদয়ের জাগরণ এবং ব্যর্থতার প্রতিকার। তখন রবীন্দ্রনাথ খুবই অসুস্থ। তবুও তিনি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তব্য পুরোটাই শোনেন। কাজী আব্দুল ওদুদের সঙ্গে ছিলেন কবি আব্দুল কাদির ও কাজী মোতাহার হোসেন। তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে ১৯৩৬ সালের ৪ ফ্রেব্রুয়ারী কবি কাজী আব্দুল ওদুদের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বইটির ভূমিকা লিখে দেন। বইটি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়।
মুসলমান খণ্ড—৩
রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ ভাষণে লিখেছেন, আমি সেখানে (পল্লীগ্রামে) থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।
নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘরভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধরে এদের উপকার করতে হয়। অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, ‘ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি।‘ তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।
রবীন্দ্রনাথ এদের জন্য একটি ক্লাব করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঘর তোলা হয়েছে। সেখানে রাখা হয়েছে খবরের কাগজ। সেখানে গানবাজনার আয়োজনের ব্যবস্থাও হল। সেখানে মাস্টারও রেখে দিলেন। হিন্দুপ্রধান এলাকায় সেই ক্লাবঘরটি কেউ ব্যবহার করল না। স্কুলঘরে ছাত্র জুটল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বলল, ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।
রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন মুসলমানদের গ্রামে সেই ইস্কুল ঘরটি টিকে গিয়েছিল। তারা আদরের সঙ্গে সেটাকে বাস্তবায়ন করেছে। মুসলমানদের মধ্যেই আত্মশক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। এই আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথাই তিনি সারা জীবন ধরে বলে গেছেন।
কবি গোলাম মোস্তফা বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত ইসলামের চমত্কার সৌসাদৃশ্য আছে৷ তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ, অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে৷... শুধু বাংলা ভাষায় কেন, জগতের কোন অমুসলমান কবির হাত দিয়া এমন লিখা বাহির হয় নাই৷' ('ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৯)৷ কবি রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ভোলার কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হককে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বলেছিলেন—মুসরমানদের প্রতি আমার মনে কিছুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখার কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।
যোগাযোগ উপন্যাসে লিখেছেন সেই প্রজাদের প্রসঙ্গে--
এ দিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি— রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।
গোরা উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শিলাইদহের নদীর উপরে—বোটে বসে। সেখানে একটি উপ আখ্যান আছে। গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা একটি গ্রামে গিয়েছে। সঙ্গে রমাপতি নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গ্রামটি নদীর চরে—মুসলিম পাড়া। সেখানে মাত্র একঘর হিন্দু পাওয়া গেল। তারা নিম্নশ্রেনীর হিন্দু জাতের—নাপিত। তারা একটি মুসলমান বালককে পুত্রজ্ঞানে প্রতিপালন করছে।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,
উভয়ে চলিতে চলিতে এক জায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সে তো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, “ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাত নেই।”
তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে— বিস্তীর্ণ বালুচর, নদী বহুদূর। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল, “হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?”
নাপিতের ঘরে একটা কাঁচা কূপ আছে— কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সে কূপ হইতে রমাপতি জল খাইতে না পারিয়া মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।
গোরা জিজ্ঞাসা করিল, “এ ছেলের কি মা-বাপ নেই?”
নাপিত কহিল, “দু’ই আছে, কিন্তু না থাকারই মতো।”
গোরা কহিল, “সে কী রকম?”
নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহার মর্ম এই—
যে জমিদারিতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুই বার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল— আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে— প্রজাদের কাহারও ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না। ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন-কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক পুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশ-দেড়েক তফাতে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে, তদন্ত উপলক্ষে গ্রামে যে কখন আসে এবং কী করে তাহার ঠিকানা নাই। গতকল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল— দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে ‘বেটা তো জোয়ান কম নয়, দেখেছ বেটার বুকের ছাতি’ বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন একটা খোঁচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। পূর্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতরো উপদ্রব করিতে সাহস করিত না, কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষমাত্রই হয় গ্রেফতার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।
গোরা তো উঠিতে চায় না, ও দিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে। সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, “হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে?”
নাপিত কহিল, “ক্রোশ-দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি, তার তহসিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব চাটুজ্জে।”
গোরা জিজ্ঞাসা করিল, “স্বভাবটা?”
নাপিত কহিল, “যমদূত বললেই হয়। এত বড়ো নির্দয় অথচ কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। এই যে কদিন দারোগাকে ঘরে পুষছে তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে— তাতে কিছু মুনফাও থাকবে।”
রমাপতি কহিল, “গৌরবাবু, চলুন আর তো পারা যায় না।” বিশেষত নাপিত-বউ যখন মুসলমান ছেলেটিকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়িতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।
গোরা যাইবার সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিঁকে আছ? আর কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই?”
নাপিত কহিল, “অনেক দিন আছি, এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না। আজ এ পাড়ার পুরুষ বলতে আর বড়ো কেউ নেই, আমি যদি যাই তা হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।”
গোরা কহিল, “আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়া করে আবার আমি আসব।”
দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটিয়া গেল। বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায় ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইলেই যে ভালো হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে এবং ঘটিতেই বাধ্য এবং ইহারাই সেজন্য প্রধানত দায়ী এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেই তো হয়, ফেসাদ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়? বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।
মধ্যাহ্নরৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি কথাও বলিল না। অবশেষে গাছপালার ভিতর হইতে কাছারিবাড়ির চালা যখন কিছুদূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোরা আসিয়া কহিল, “রমাপতি, তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চললুম।”
রমাপতি কহিল, “সে কী কথা! আপনি খাবেন না? চাটুজ্জের ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে তার পরে যাবেন।”
গোরা কহিল, “আমার কর্তব্য আমি করব, এখন তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যেয়ো— ঐ ঘোষপুর-চরে আমাকে বোধ হয় কিছুদিন থেকে যেতে হবে— তুমি সে পারবে না।”
রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোরার মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দু ঐ ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পানভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়াছে তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় নহে, এক-এক মুহূর্ত তাহার কাছে এক-এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; গোরার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের জন্য তাহাকে অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি খর্ব ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে, এ কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, ‘পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হোক, এই আচারবিচারের ভালোমন্দের কথা পরে ভাবিব, কিন্তু এখন তো পারিলাম না।’
নাপিত গোরাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। গোরা প্রথমে আসিয়া নাপিতের ঘটি নিজের হাতে ভালো করিয়া মাজিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইল এবং কহিল— ঘরে যদি কিছু চাল ডাল থাকে তো দাও আমি রাঁধিয়া খাইব। নাপিত ব্যস্ত হইয়া রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিল। গোরা আহার সারিয়া কহিল, “আমি তোমার এখানে দু-চার দিন থাকব।”
নাপিত ভয় পাইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, “আপনি এই অধমের এখানে থাকবেন তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু দেখুন, আমাদের উপরে পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, আপনি থাকলে কী ফেসাদ ঘটবে তা বলা যায় না।”
গোরা কহিল, “আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিস কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে, আমি তোমাদের রক্ষা করব।”
নাপিত কহিল, “দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তা হলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে দিয়েছি। এতদিন কোনোপ্রকারে টিঁকে ছিলুম, আর টিঁকতে পারব না। আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তা হলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।”
গোরা চিরদিন শহরে থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে, নাপিত কেন যে এত ভয় পাইতেছে তাহা তাহার পক্ষে বুঝিতে পারাই শক্ত। সে জানিত ন্যায়ের পক্ষে জোর করিয়া দাঁড়াইলেই অন্যায়ের প্রতিকার হয়। বিপন্ন গ্রামকে অসহায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার কর্তব্যবুদ্ধি সম্মত হইল না। তখন নাপিত তাহার পায়ে ধরিয়া কহিল, “দেখুন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পুণ্যবলে আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, আপনাকে যেতে বলছি এতে আমার অপরাধ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রতি আপনার দয়া আছে জেনেই বলছি, আপনি আমার এই বাড়িতে বসে পুলিসের অত্যাচারে যদি কোনো বাধা দেন তা হলে আমাকে বড়োই বিপদে ফেলবেন।”
নাপিতের এই ভয়কে অমূলক কাপুরুষতা মনে করিয়া গোরা কিছু বিরক্ত হইয়াই অপরাহ্নে তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। এই ম্লেচ্ছাচারীর ঘরে আহারাদি করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা অপ্রসন্নতাও জন্মিতে লাগিল। ক্লান্তশরীরে এবং উত্ত্যক্তচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে সে নীলকুঠির কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহার সারিয়া রমাপতি কলিকাতায় রওনা হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই, তাই সেখানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না। মাধব চাটুজ্জে বিশেষ খাতির করিয়া গোরাকে আতিথ্যে আহ্বান করিল। গোরা একেবারেই আগুন হইয়া উঠিয়া কহিল, “আপনার এখানে আমি জলগ্রহণও করব না।”
মাধব বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গোরা তাহাকে অন্যায়কারী অত্যাচারী বলিয়া কটুক্তি করিল, এবং আসন গ্রহণ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা তক্তপোশে বসিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানিতেছিল। সে খাড়া হইয়া বসিল এবং রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কে হে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?”
গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া কহিল, “তুমি দারোগা বুঝি? তুমি ঘোষপুরের চরে যে-সমস্ত উৎপাত করেছ আমি তার সমস্ত খবর নিয়েছি। এখনো যদি সাবধান না হও তা হলে— ”
দারোগা। ফাঁসি দেবে না কি? তাই তো, লোকটা কম নয় তো দেখছি। ভেবেছিলেম ভিক্ষে নিতে এসেছে, এ যে চোখ রাঙায়!ওরে তেওয়ারি!
মাধব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দারোগার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আরে কর কী, ভদ্রলোক, অপমান কোরো না।”
দারোগা গরম হইয়া কহিল, “কিসের ভদ্রলোক! উনি যে তোমাকে যা-খুশি-তাই বললেন, সেটা বুঝি অপমান নয়?”
মাধব কহিল, “যা বলেছেন সে তো মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চলবে কী করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর তো কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বললে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে তো জানা কথা। কী করবে, তাকে তো খেতে হবে।”
বিনা প্রয়োজনে মাধবকে রাগ প্রকাশ করিতে কেহ কোনোদিন দেখে নাই। কোন্ মানুষের দ্বারা কখন কী কাজ পাওয়া যায়, অথবা বক্র হইলে কাহার দ্বারা কী অপকার হইতে পারে তাহা বলা যায় কি? কাহারো অনিষ্ট বা অপমান সে খুব হিসাব করিয়াই করিত— রাগ করিয়া পরকে আঘাত করিবার ক্ষমতার বাজে খরচ করিত না।
দারোগা তখন গোরাকে কহিল, “দেখো বাপু, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি; এতে যদি কোনো কথা বল বা গোলমাল কর তা হলে মুশকিলে পড়বে।”
গোরা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, “মশায়, যা বলছেন সে কথাটা ঠিক— আমাদের এ কসাইয়ের কাজ— আর ঐ-যে বেটা দারোগা দেখছেন ওর সঙ্গে এক বিছানায় বসলে পাপ হয়— ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারি নে। আর বেশি দিন নয়— বছর দুত্তিন কাজ করলেই মেয়ে-কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে স্ত্রী-পুরুষে কাশীবাসী হব। আর ভালো লাগে না মশায়, এক-এক সময় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি! যা হোক, আজ রাত্রে যাবেন কোথায়? এইখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্যে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।”
গোরার ক্ষুধা সাধারণের অপেক্ষা অধিক— আজ প্রাতে ভালো করিয়া খাওয়াও হয় নাই— কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন জ্বলিতেছিল— সে কোনোমতেই এখানে থাকিতে পারিল না, কহিল, “আমার বিশেষ কাজ আছে।”
মাধব কহিল, “তা, রসুন, একটা লণ্ঠন সঙ্গে দিই।”
গোরা তাহার কোনো জবাব না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।
মুসলমান খণ্ড ৪
১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে গিয়েছিলেন। সিলেটের ব্রাহ্ম সমাজ, মহিলা সমিতি ও আনজুমানে ইসলামিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। খান বাহাদুর আবদুল মজিদ,মৌলভী আবদুল করিম, রায়বাহাদুর সুখময় চৌধুরী, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত প্রমুখ জননেতা রেল স্টেশনে কবিকে অভ্যর্থনা জানান।
সৈয়দ মুর্তাজা আলী স্মৃতিকথায় লিখেছেন, চাঁদনি ঘাটে সিলেটের বনিয়াদী জমিদার পরিবারের-- মজুমদার বাড়ি, কাজী বাড়ি (এহিয়া ভিলা) ও দস্তিদার বাড়ির প্রতিনিধিরা ঘোড়ায় চড়ে এসে কবিকে সম্বর্ধনা করেন। কবি, মৌলভী আবদুল করিমকে নিয়ে বসেন এক সুসজ্জিত ফিটন গাড়িতে।
কবিকে অব্যর্থনা করা হয় রতনমণি লোকনাথ টাউন হলে। সেখানে সর্বাগ্রগণ্য জননেতা সৈয়দ আবদুল মুজদ কবিকে অভিনন্দন জানান উর্দু ভাষায়। ছাত্রদের কাছে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন কবি। মুর্তজা আলীর ভাই সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ।
রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে মুজতবা আলী কারো কাছে পরামর্শ না করে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন—‘আক্ঙ্ক্ষা করতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?”
রবীন্দ্রনাথ তখন সিলেট থেকে গেছেন আগরতলাতে। সেখান থেকে চিঠির উত্তর দিয়েছেন দশ বারো লাইনে। চিঠির মর্ম ছিল, আকাঙক্ষা উচ্চ করতে হবে—এ কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—যেন স্বার্থই মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদগ্র কামনাই মানুষের কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিৎ তা এতদূর থেকে বলে দেয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।
কবির এই চিঠি পেয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তি নিকেতনে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। মুজতবা আলীই বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগের প্রথম বাইরের প্রথম ছাত্র।
প্রায় এক বছর সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তি নিকেতনে একই ঘরের নিচে কবির সঙ্গে বসত করেছেন। মুজতবা আলী লিখেছেন—সেখান থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা-আটটা, নটা, তারপর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ—দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়ে দেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ—লেখাপড়া। একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—কাজ—কাজ—কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তারপর খাওয়া সেরে আবার লেখালেখা পড়া। মাঝে মাঝে গুণগুণ করে গান—আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা! আর কী অরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা।
সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধরা ছোঁয়ার অতীত; সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে—কিন্তু আমাদের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু; নিতান্তই মাটির মানুষ।
সঙ্গীতজ্ঞ আব্দুল আহাদ ১৯৩৮ সালে শান্তি নিকেতনে সঙ্গীতভবনে ভর্ত্তি হন। তাঁর প্রথম রবীন্দ্রদর্শন বিষয়ে লিখেছেন, আমি (শান্তি নিকেতন) যাবার অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দীভবনের উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধনের দিনে প্রথম কবিগুরুকে দেখলাম, কী শান্ত সৌম্য মূর্তি। সাদা চুল এবং দাড়ি, সবকিছু মিলে সবার থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব। কবিগুরু তখন কিছুটা কুঁজো হয়ে হয়ে গেছেন। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া কবিগুরু উত্তরায়ণের বাইরে আসেন না।
কবি বন্দে আলী আলী মিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটা ছিল সহজ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত অনুরাগ কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে দেখা করেন। তিনি লিখেছেন, দোতলার সিঁড়ির মুখে উত্তর দিকে, বারান্দায় কবি চেয়ারে বসে লিখছিলেন। আমি গিয়ে কদমবুসি করে বইখানি হাতে দিলুম।
কবি আমায় বসতে বলে ফাইন্টেন পেনটা মুড়ে অনুরাগের পাতা উল্টাতে শুরু করলেন। কবি (টেলিফোন পেয়ে) নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ সুঠাম দেহ, ধুসর রঙের দীর্ঘ আলখাল্লা পা অবধি পড়েছে—নীচে সবুজ সাটিন লুঙ্গি ধরনের পরা। যীশুখ্রীস্টের ছবি দেখেছি-- দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথকে দেখে সেই কথা মনে পড়লো। রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, আভিজাত্য ইত্যাদির এমন সুসংহত সন্নিবেশ অপর কোনো মহাপুরুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে কিনা জানি না।
শাহেদ সোহরাওয়ার্দী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন অক্সফোর্ডে। সেটা ১৯১৩ সালে। রবীন্দ্রনাথ সবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শাহেদ সোহারাওয়ার্দি বাংলা জানতেন না। তিনি লিখেছেন, প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের গানের সমাদরের কথা, বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরেই তা গাওয়া হচ্ছে—এ খবর যখন শুনি-- অনেকটা অবিশ্বাসের সঙ্গেই সে কথা গ্রহণ করেছিলাম। কবির সঙ্গে যাদের প্রথম পরিচিতি ঘটে অনুবাদের ভিতর দিয়ে, তাদের মত আমার কাছেও তাঁর কাব্যের স্বকৃত ইংরেজী সংস্করণ যে এক আশ্চর্য আবির্ভারের মত বোধ হয়েছিল তা শুধু নতুনত্বের খাতিরেই নয়, তাঁর কাব্যের নিজস্ব সাহিত্যিক রসের জন্যই সে বিস্ময় এত বেশী।
প্যাডিংটন স্টেশনে পৌছে আমি একটা ট্যাক্সি করে চেলসীতে গেলাম, সেখানে এক বিরাট বাড়িতে কবি সদলবলে ছিলেন। একটা প্রশস্ত কামরায় আমায় নিয়ে গেলেন। আমি সেখানেই কবিকে প্রথম দেখি। কবি একটা ডিভানের উপর বসেছিলেন, আর দেওয়ালের চারদিক ঘিরে নানা জাতীয়—ভারতীয়, ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়—স্ত্রীপুরুষ চেয়ারের উপর বসেছিলেন। সমস্ত ঘরে এমন তন্ময় নিঃশব্দতা যেন সবাই গীর্জায় বসে আছেন। ঘরের এক কোণে একজন ইংরাজ মহিলা মাটি দিয়ে কবির মাথার ছাঁচ গড়ছিলেন। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম অন্য এক কোণে হিংস্রদর্শন যুবা, তাঁকে পোল মনে হল, কবির আলখাল্লার অনবদ্য ভাঁজগুলি রেখায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।
...সেদিন ভেবেছিলাম যে ভাস্কর ও চিত্রকরের সুবিধার জন্যই কবি নিশ্চল মূর্তিতে নিমীলিত চোখে বসে আছেন, কিন্তু পরে তার তাৎপর্য ভাল করে বুঝেছি। ইচ্ছামত ও বিনা আয়াসে তিনি নিজের মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন এবং তখন তাঁর যে নিস্পন্দ ভাস্কর্য রূপ তা অনন্য সাধারণ। এ দূর্লভ শক্তির বিকাশ কবির মধ্যে যে পরিমাণে দেখেছি, অন্য কোথাও তা দেখি নাই। সাহচর্যের ভিতর সুদূর নিঃসঙ্গতা, কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অন্তরতম জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ, পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করবার এ শক্তি স্বপ্নদ্রষ্টা ও আদর্শবাদিদের থাকে—তাঁরও ছিল। এ রকম ব্যক্তিদের সঙ্গে সহবতী চলে কিন্তু ঘনিষ্ট হওয়া যায় না। ...কবি চিরকালই আমার কানের চেয়ে চোখকে বেশী আকর্ষণ করেছে।
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমি দেখেছিলাম প্রাচ্যের সুর-ঝঙ্কার, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রতীক। নদীর জলধারা যেমন করে বয়, বায়ূহিল্লোলে ধানের শীষ যেমন করে জাগে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাঁর কাছে তেমন করে আসে। স্বভাবে কোমল লঘুপদক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে ইপ্সিতার যে অভিসার, রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সেই গতি।
মোহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে প্রথম যখন গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাসাদপ্রতীম সৌধের একটি কক্ষে বসেছিলেন। কক্ষটির সাজসজ্জা সাদামাটা ধরনের। কবি বসে আছেন একটি সাবেকী তক্তপোষ আশ্রয় করে। সেখানে চেয়ার টেবিলের বাহুল্য নেই। তক্তপোষের একপাশে বই রাখার একটি মঞ্চবিশেষ। তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হল। মোহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ লিখেছেন—যেন কতদিনের পরিচয়। যিনি সবাইকে আপন জ্ঞান করেন তাঁহার কাছে আমি আপন—বিশেষতঃ আমার সাক্ষাৎ যে উদ্দেশ্যপ্রোণেদিত তাহা অবগত হইয়া তিনি নিতান্তই পরিচিতের মত আলোচনায় রত হইলেন।
কবি জসীমউদ্দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন একটি নাট্যাভিনয়ে। জসীমউদ্দিন তখন ফরিদপুর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সেদিন রবীন্দ্রনাথের শেষবর্ষণ নাটকটির অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন তিনি আট আনার টিকিট কেটে। দর্শকদের মধ্যে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর সুসজ্জিত মেয়েরা রহস্যময়ী চাঁদের মত বসে আছে। জসীমউদ্দিন লিখেছেন, কিছুক্ষণ পরে সামনের মঞ্চের পর্দা উঠিয়া গেল। বর্ষাকালের যত রকমের ফুল সমস্ত আনিয়া মঞ্চটিকে অপূর্বভাবে সাজান হইয়াছে। সেই মঞ্চের উপর গায়ক-গাযিকা পরিবৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আসিয়া যখন উপবেশন করিলেন, তখন আমার সামনে উপবিষ্ট সেই রহস্যময়ী চাঁদেরা জোনাকীর মতো যেন ম্লান হইয়া গেল।
নাটক শেষ হলে কবি মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। অনেকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। জসীমউদ্দিনও তাদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রণাম করলেন না। আর দশজনের মত তাকে প্রণাম জানিয়ে পথের দশজনের মধ্যেই মিলিয়া যাবেন—কবির সঙ্গে তরুন কবি চসীমউদ্দিনের সেই সম্পর্ক নয়। তিনি শুধু এক দৃষ্টিতে রবিকবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
১৯২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি ঢাকায় এসেছিলেন। সেদিন বিকেলে করোনেশন পার্কের বিশাল জনসভায় প্রথম দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লেখক আবুল ফজল। তিনি রেখাচিত্র বইয়ে লিখেছেন সেদিনের স্মৃতি—কবির জন্য মঞ্চ তৈরী হয়েছিল পার্কের পূব ধারে—কাজেই কবি যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন তখন তিনি সূর্যের মুখোমুখি। দীর্ঘ বপু, চুল দাড়ি গোঁফ সবই রূপার মতো সাদা। কিন্তু দেহের কোথাও জরার চিহ্ণ লক্ষ্য গোচর নয়। যখন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে-- সে সূর্যের তখনকার কিরণের সঙ্গে তার গায়ের রং একাকার হয়ে মিশে গেছে, সে সূর্যের দিকে চেয়ে, তার অস্তগমনের সঙ্গে নিজের অস্তগমনোন্মুখ জীবনের তুলনা দিয়ে এক অতুলনীয় ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন, তখন বিপুল জনতা কবি-মুখ-নিসৃত ভাষার সৌন্দর্যে ও কণ্ঠের মাধুর্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো।
কোনো কথা কি ভাষার জন্য তাকে ভাবতে দেখিনি, ঝরণার ধারার মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে বানীর স্রোত বয়ে চলেছে। কোনো উত্তেজনা নেই, হাত-পায়ের ছোড়াছুড়ি নেই, নেই কোনো পেশাদার বক্তার মতো কণ্ঠের উত্তান-পতন, স্থির শান্ত মুখশ্রীতে নেই কোন বিপর্যয়—প্রায় আধ ঘণ্টা কি তারো বেশী এক অপূর্ব বাণী স্রোতে আমরা যেন অবগাহন করে উঠলাম।
কবি জসীমউদ্দিন ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় বইটিতে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি তাঁকে বলেছিলেন—দেখ, জমিদারির তদারকী করতে সাজাদপুরে যেতাম। আমাদের একজন বুড়ো প্রজা ছিল। যৌবনকালে সে অনেক ডাকাতি করেছে। বুড়ো বয়েসে সে আর ডাকাতি করতে যেত না। কিন্তু ডাকাতরা তাকে বড়ই মানত। একবার আমাদের এক প্রজা অন্য দেশে নৌকা করে ব্যবসা করতে যায়। ডাকাতের দল এসে তার নৌকা ঘিরে ধরল। তখন সে আমাদের জমিদারির সেই বুড়ো প্রজার নাম করল। তারা নৌকা ছেড়ে চলে গেল। এই বলে চলে গেল, ও তোমরা অমুক দেশের অমুকের গাঁয়ের লোক। যাও, তোমাদের কোনো ভয় নেই। সেই বৃদ্ধ মুসলমান আমাকে বড়ই ভালবাসত। তখন নতুন বয়স। আমি জমিদারির তদারক করতে এসেছি। বুড়ো প্রায় পাঁচশ প্রজা কাছারির সামনের ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, এত লোক ডেকে এনেছ কেন? সে উত্তর কলল, ওরা আপনাকে দেখতে এসেছে। ওরে তোরা দেখ। একবার প্রাণভরে সোনার চাঁদ দেখে নে। আমি দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলাম।
মুসলমান খণ্ড—৫
সুফিয়া কামাল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। কবি তখন আলমোড়ায়। কবি সুফিয়া কামালকে কয়েকটি লাইন লিখে পাঠালেন—
বিদায়-বেলার রবির সনে
বনশ্রী তার অর্ঘ্য আনে
অশোক ফুলের বরুণ অঞ্জলি।
আভাস তারই রঙিন মেঘে
শেষ নিমিষে রইল লেগে
রবি যখন অস্তে যাবে চলি।
কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ কাব্যের ২৬৭ সংখ্যক কবিতাংশে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি পাঠিয়ে কবি সুফিয়া কামালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সুফিয়া কামালের বাড়ি বরিশালে জেনে কৌতুক করে বলেছিলেন-তুমি আমার বেয়াইয়ের দেশের মানুষ। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর-মিষ্টি তুমি। কবির মেজো মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন বরিশালে।
সুফিয়া কামাল লিখেছেন, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সুরসিক সুন্দর মনের মানুষ। কতবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। তাঁর নিজের করা নাটক দেখতে আমাকে ডেকেছেন। নিজ হাতে নাম লিখে তাঁর গোরা বইখানা আমাকে উপহার দিয়েছেন। লিখেছেন--
শ্রীমতি কল্যাণীয়া সুফিয়া খাতুনকে
স্নেহ উপহার দিলাম
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ আশ্বিন ১৩৩৬।
সুফিয়া কামাল প্রথম দিন জোড়াসাঁকোতে গিয়েছিলেন বোরকা পরে। সঙ্গে তাঁর স্বামী নেহাল হোসেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাও গিয়েছিলেন কবির কাছে বোরকা ছাড়াই। পায়ে হাত দিয়ে কবিকে সালাম করছেন। তিনি লিখেছেন, আমি সেলাম করে উঠলে দুহাত উর্দ্ধ তুলে চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ ধরে কি প্রার্থনা করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখেছি তাঁর সর্বদেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। তারপরে তিনি পাশে বসিয়ে গল্প করতে আরম্ভ করলেন—তোমরা যে পর্দ্দা থেকে বাইরে এসেছ এই আমি আশ্চর্য হয়েছি। দ্যাখো সূর্যের কিরণ না পেলে যেমন গাছপালা বড় হয় না ফলমুল ভালো দেয় না, মানুষও তেমনি বাইরের আলোবাতাস ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। পদ্ম পঙ্ক থেকে উর্দ্ধে উঠেই সূর্যের কিরণ লাভ করে, না হলে সে লাভ করতে পারত না। আর এখানেই তার সার্থকতা।
রাহাত আরা বেগম রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটক উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি স্বামীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, খুবই ভদ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের সঙ্গে মিশলেন। অনেক কথা বললেন। ...আমাদের দুজনকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সওগাত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার পরে জোড়াসাঁকোতে কবির সঙ্গে দেখা করলেন। কবিকে সালাম জানালেন। শান্তস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি সালাম গ্রহণ করে বসতে বললেন। সওগাত পত্রিকা থেকে দুটো কবিতা পড়লেন। সওগাত নামটির প্রশংসাও করলেন। নাসিরউদ্দিন সওগাত পত্রিকার জন্য কবির কাছে কবিতা চাইলেন।
কবির সব লেখাই তখন বিশ্বভারতীর কাছে প্রদান করেছেন। কবির লেখা পেতে হলে বিশ্বভারতীকে টাকা দিতে হয়। এই লেখা থেকে প্রাপ্ত টাকা বিশ্বভারতীর পরিচালনার কাজে ব্যয় হয়।
নাসিরউদ্দিন সেকথা শুনে ফিরে গেলেন। টাকা দিয়ে লেখা নেওয়ার সঙ্গতি তাঁর নেই। কদিন পরেই ডাকে কবির একটি চিঠি তিনি পেলেন। সঙ্গে একটি কবিতা। কবি তাঁকে লিখেছেন--
বিশ্বভারতীকে টাকা দিয়ে আমার লেখা নেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না বলে সেদিন জানিয়েছিলে। আমি লক্ষ্য করেছি তুমি খুব নিরাশ হয়ে চলে গেলে। একটা কবিতা পাঠালাম। আশা করি তোমার ভাল লাগবে। এর জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে না।
এরপর মাঝে মাঝেই কবি নিজের উদ্যোগেই সওগাত পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছেন। সওগাতের দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি কথিকা পাঠিয়েছিলেন। নাম ছিল—সওগাত।
কবি জসীমউদ্দিনের নকশী কাঁথার মাঠ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করে লিখেছিলেন—জসীমউদ্দিনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির কদর এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমন খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।
একরামউদ্দীন (১৮৮০—১৯৩৫) ‘রবীন্দ্রপ্রতিভা’ সমালোচনাগ্রন্থ লিখেছিলেন। বইটিকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। কবি চিঠিতে লিখেছিলেন-- আপনি যে সরস বাংলা ভাষায় আমার রচনার সমালোচনা করিয়াছেন তা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।
ইমাম গাজ্জালীর ইয়াহিয়া-উল-উলমুদ্দিনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কিমিয়া সাআদাত অনুবাদ করেছিলেন মীর্জা মোহাম্মদ ইউসফ। বইটির নাম রেখেছিলেন সৌভাগ্য স্পর্শমণি। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন। গ্রন্থটির মধ্যে ভাবের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন।
সারা তৈফুর (১৮৮৮-১৯৭১) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলাজীবনীকার। তিনি এ কে ফজলুল হকের ভাগ্নি ও ইতিহাসবিদ-পুরাতত্ত্ববিদ সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের স্ত্রী। তাঁর স্বর্গের জ্যোতিঃ পুস্তিকা রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। বইটির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল মৌলবী মুজিবর রহমান সম্পাদিত দি মুসলমান পত্রিকা। সেখানে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উদ্ধৃতি ছিল—আপনার স্বর্গের জ্যোতি: গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম, ইহার ভাষা ও রচনা সুন্দর হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের অভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন।
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮০—১৯৪০) হযরত মোহাম্মদের কিশোর জীবনী লিখেছেন নূরনবী নামে। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির বইটির পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে চিঠিটির অংশ বিশেষ ছাপা হয়েছিল। সেখানে নূরনবীর বইটির প্রশংসা করেছেন। বইটির বিষয় ও রচনাপ্রণালী শিশু পাঠকদের পক্ষে মনোরম বলে প্রশংসা করেছেন।
কাজী আবদুল ওদুদের নদীবক্ষে উপন্যাসটি পড়ে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ কবি লিখেছেন--
আপনার লিখিত নদীবক্ষে উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষীগৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকতা, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষভাবে আনন্দলাভ করিয়াছি—এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।
কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম প্রবন্ধ সংকলনে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভাবর প্রথম বিকাশ। তিনটি প্রবন্ধ শুরুতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশি হয়েছিল। কবি বইটি পড়ে লিখেছেন—এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর একসঙ্গে মিশেছে।...গোঁড়ামীর নিবিড় বিভীষিকার ভিতর দিয়ে কুঠার হাতে তুমি পথ কাটতে বেরিয়েছ, তুমি ধন্য।
১৬ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে কাজী আবদুল ওদুদকে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিতে কবি তাঁর নিজের গান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, আমার গান সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধ পূর্ব্বেই পড়ে আমি বিশেষভাবে খুশি হয়েছিলাম। তার কারণ আমার পাঠকেরা আমার গানকে কাব্যের সম্পূর্ণতা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখে। সুরের একান্ত আশ্রিত সে রকম কবিতাও আমার আছে—সুর থেকে বিচ্ছিন্নতার বৈধব্য দশায় সে শ্রীহীন এবং প্রায় নিরর্থক। কিন্তু আমার বিস্তর গান আছে তা কাব্য, বাইরে থেকে সুর যোজনা না করলেও সুর আছে তার অন্তর্নিহিত। আমার নিজের বিশ্বাস কাব্য হিসাবে আমার অধিকাংশ কবিতার চেয়ে সেগুলো শ্রেষ্ঠ। বঙ্গসাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ বিষয়ে তিনি ওদুদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে তিনি ওদুদকে লেখেন--সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্মই এই সকল আদর্শ তার মধ্যে প্রধানত পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় প্রত্যক্ষভাবে নয়, এই কারণেই সে আদর্শ সর্ব্বজাতীয় হয়ে ওঠে—উপস্থিত কালের মধ্যেই তার ফল ফলে না দীর্ঘকালে তার সফলতা।
কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২—১৯২৬) আবদুল্লাহ (১৯৩৩) উপন্যাস পড়ে কবি ওদুদকে লিখেছিলেন, আব্দুল্লাহ বইখানি পড়ে আমি খুশি হয়েছি। বিশেষ কারণ এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের খবর জানা গেল। এ দেশের সামাজিক আবহাওয়াঘটিত একটা কথা এই বই আমাকে ভাবিয়েছে। দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করেছে সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ? এই রোগ বিষে ভরা বর্ব্বরতার হাওয়া এ দেশে আর কতদিন বইবে। আমরা দুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলে চলব।
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ভাষা ও সাহিত্য ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ সালে। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ শহীদুল্লাহকে ১৯৩২ সালের ২৯ জুলাই চিঠি লিখে জানান, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের আহবান করে আপনি যে প্রবন্ধ কয়টি লিখেছেন, তা হিন্দুদেরও বিচার্য্য। বাংলার ভাষাতত্ত্ববিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার প্রশংসা অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আপনি আমাকে সাধুবাদ দিয়েছেন তাতে আমি সংকোচ বোধ করি। যে সময়ে আমি এই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম তখন এ পথে আমি ছিলাম একা। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমি সম্পূর্ণ আনাড়ি। অন্ধকারে আমার প্রদীপ ছিল না, হাতড়িয়ে বেড়িয়েছি। যখন থেকে আপনাদের হাতে আলো জ্বলল, তখন থেকেই এই অধ্যবসায় ত্যাগ করেছি।
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইরানী কবি হাফেজের কবিতার পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। সেগুলো পড়ে কবি এই চিঠিতে অনুবাদ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন কবি—বাংলা ভাষায় আরবী ও পারসী সাহিত্যের অনুবাদ অবশ্য কর্তব্য আমার তাতে সন্দেহ নেই। যদি বিশ্বিভারতীর এ অর্থদৈণ্য কখনো দূর হয় তবে এ কাজে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হব।
বিদেশী ভাষার উচ্চ শ্রেণীর কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা বর্জ্জনীয় বলে আমি মনে করি। কবিতায় এক দিকে ভাবার্থ, আর এক দিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাষার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কোনোমতেই চালান করা যায় না। চেষ্টা করতে গেলে ভাবার্থের প্রতিও জুলুম করতে হয়। এই কারণেই পদ্যে আপনার হাফেজ অনুবাদ চেষ্টার আমি অনুমোদন করতে পারলেম না।
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। কবি সেটি পড়ে কবি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে চিঠিতে জানিয়েছেন। ব্যাকরণখানি সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়েছে—এতে ছাত্রদের উপকার হবে বলেও লিখেছেন। বইটি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য।
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একমাত্র ছেলে রথীন্দ্রনাথের বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে ১২ মে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়র ম্যানেজিং কমিটির (সিন্ডিকেট) সদস্যরূপে বরণ করে চিঠি লিখেছিলেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে। শহীদুল্লাহ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমস্যার কারণে তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম সংসদের সদস্যপদ লাভের দুর্লভ সম্মান গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। তবে সংসদের সদস্যদের তালিকায় শহীদুল্লাহর নাম মুদ্রিত হয়েছিল। অধ্যাপক ভুঁইয়া ইকবাল লিখেছেন--সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শহীল্লাহর নিযুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। অথচ এই শাস্ত্রীই ১১ মাস আগে শহীদুল্লাহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার সময়ে তাঁর নিযুক্তির সমর্থন করেছিলেন। আমাদের ধারণা, ওই পরিস্থিতিতে শহীদুল্লাহ হয়তো রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে উপযুক্ত সাড়া দেওয়া নিরাপদ বিবেচনা করেন নি।
নবীন কবিযশোপ্রার্থী আজিজুল হাকিম কবির বাণী চেয়েছিলেন। কবি ১৯২৯ সালের ১০ অক্টোবর তাঁকে লিখেছিলেন, আমার বাণী আমার কাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। যখন আমার কাজের সঙ্গে পরিচয় হবে তখন আমার বাণী শুনতে পাবে। আমাদের দেশে আমরা কেবল কথা বলচি এবং কথা বলচি এবং কতকগুলি বাধা-কথার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়েচি। বড়ো কথা মাত্রই অত্যন্ত পুরোনো, কাজের মধ্যে দিয়েই জীবনে তাদের নূতন করে আবিষ্কার করি। যতক্ষণ না করি ততক্ষণ সে কথাগুলো বস্তার ভিতরকার বীজের মতো, যে বীজ উপযুক্ত মাটির মধ্যেই সক্রিয়, সার্থক হয়। অন্যত্র কেবল মাত্র বোঝা হয়ে থাকে।
মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্ত্বে হিন্দু মোসলেম সম্প্রীতি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ১৯৩৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দন্তচিকিৎসক ডাঃ আর আহমদকে শুভেচ্ছা পত্র লিখেছিলেন। তিনি কবির দাঁতের চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে কবির সহকর্মী প্রমোদেলাল গাঙ্গুলির দন্তক্ষয়ের চিকিৎসা করার অনুরোধ করেছিলেন।
বন্দে আলী মিয়ার ময়নামতি চর কাব্যগ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে পাঠপ্রতিক্রিয়া লিখেছেন, তোমার ময়নামতির চর কাব্যখানিতে পদ্মাচরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে তুমি দেখেছ এবং কলমের অনায়াস ভঙ্গিতে লিখেছ। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি তাতে করে কবিতাগুলি আরো সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাপাড়ের পাড়াগাঁয়ের এমন নিকট স্পর্শ বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না।
পদ্মা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বড়ো জায়গা আছে। সারা জীবন ধরে যে নদীকে দেখেছেন বা ভেবেছেন বা গড়েছেন সে নদী পদ্মাই। শিলাইদহ থেকে চলে আসার অনেক দিন পরে, যখন তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, বাইরে যাওয়ার আর সামর্থ্যটি নেই—তখন তিনি লিখেছিলেন শান্তি নিকেতনের কোপাই নদীটিকে নিয়ে একটি কবিতা। কোপাই নদীটিকে লিখতে গিয়ে হঠাৎ করে লিখে ফেলেন পদ্মার কথাই।
পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ওইখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের-ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।
১৮৯১ সালের অক্টোবরে (সোমবার ৩ কার্তিক) ইন্দিরাকে লিখেছিলেন কবি, কোজাগার পূর্ণিমার দিন নদীর ধারের আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম—আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল;ঠিক ‘কথোপকথন’ বলা যায় না, বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপচাপ করে শুনে যাচ্ছিল, নিজের হয়ে একটে জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না—আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসঙ্গত কথাও বসিয়ে দিতুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল, কী আর বলব। কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না;--ও-ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্না ঝিক ঝিক করছে; একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই, ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই, একটি তৃণ নেই—মনে হয়, যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীর চাঁদের উদয় হচ্ছে, জনশূণ্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যাক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের ‘তেপান্তের মাঠ’ এবং ‘সাত সমুদ্র তেরো নদী; ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধু করছে। আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটি মাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিল আর-এক পারে, জীবনের পারে...
বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমরা তেমনি পদ্মা-আমার যথার্থ বাহন; খুব বেশি পোষ-মানা- নয়, কিছু বুনোরকম; কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। ...আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকারের একটি স্বতন্ত্র মানুষের ...
(ছিন্নপত্র, ২ মে ১৮৯৩)
মুসলমান খণ্ড—৬
রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালের ১৩ জুলাই পাবনার সিরাজগঞ্জের সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আবুল মনসুর এলাহী বক্সকে চিঠিতে লিখেছেন, মানুষের দুঃখ দূর ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। তোমরা সেই শ্রেয়ঃ সাধনায় ব্রতী হয়েছো, তার সফলতা চিরদিন অন্তরে বাহিরে তোমাদের অনুবর্তী হোক এই আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ।
এর পরই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মুসলমান সম্পর্কে তাঁর ধারণা, বোগদাদের মরুভূমিতে একজন বেদুয়িন দলপতি আমাকে এই বলেছিলেন যে, যাঁর বাক্যের দ্বারা , কর্মের দ্বারা, কোনো মানুষ পীড়িত হয় না, তিনিই যথার্থ মুসলমান। যাঁর বাক্য অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুঃখীর সান্ত্বনা তিনিই সত্য ধর্মের দূত।
জসীমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এই সমস্যার মূলসূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই যে ঘরে আগুন লাগে তার কারণ সেই ঘরের মধ্যে বহুকাল আগুন সঞ্চিত ছিল। যাঁরা বলতে চান, আমরা সবাই মিলে মিশ হয়ে ভালো ছিলুম, ভাল ইংরেজ এসেই আমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল, তাঁরা সমস্যাটি এড়িয়ে যেতে চান।
সে সময়ে বন্দে মাতরম গানটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুব বিরোধ চলছিল। রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্দিনকে বলেছিলেন, বন্দে মাতরম গানটি যেভাবে আছে, তোমরা মুসলমানেরা এ জন্য আপত্তি করতে পার। কারণ এ গানে তোমাদের ধর্মমত ক্ষুণ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তখন কংগ্রেসের জহর লাল নেহেরু গানটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির এ গানে মুসলমানদের আপত্তিজনক অংশটি কেটে ফেলার জন্য কবি নেহেরুকে পরামর্শ দেন। এর কংগ্রেসের কোনো সভায় বন্দে মাতরমের আপত্তির জায়গাটি আর না গাওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।
জসীমউদ্দিনের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, কেন যে মানুষ একের অপরাধের জন্য অপরকে মারে! ও-দেশের মুসলমানেরা হিন্দুদের মারল, তাই এদেশের হিন্দুরা এখানকার নিরীহ মুসলমানদের মেরে তার প্রতিবাদ করবে, এই বর্বর মনোবৃত্তির হাত থেকে দেশ কিভাবে উদ্ধার পাবে বলতে পার? দেখ, কী সামান্য ব্যাপার নিয়ে কলহ হয়। গরু কোরবানী নিয়ে, মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একটা পশুকে রক্ষা করতে কত মানুষকে হত্যা করছে।
এইসব আলোচনা করতে করতে কবি মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। জসীমউদ্দিন জানাচ্ছেন, কবির মনে একদেশদর্শী হিন্দুত্বের স্থান ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা স্বাধীন মতবাদ নিয়ে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করতেন, তাদের প্রতি কবির মনে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।
বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের নেতা কাজী আব্দুল ওদুদকে বিশ্বভারতীতে নিজাম-বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আব্দুল ওদুদ সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বিষয়টি নিয়ে তিনদিন লিখিত বক্তৃতা দেন। কবি তখন বেশ অসুস্থ। কিন্তু অসুস্থতা নিয়েও তিনি নিজে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শুনেছেন। কবি আব্দুল কাদির জানিয়েছেন, সে-সময় তাঁর (কাজী আবদুল ওদুদ) সঙ্গী হয়ে আমি ও সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। আমরা প্রায় সপ্তাহকাল রবীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেছিলাম। প্রত্যহ দুপুরে দক্ষিণায়নে আমাদের আহারের সময় কবিগুরু উপস্থিত থাকতেন এবং নানা প্রসঙ্গে আলাপ করতেন। সে আলাপ জুড়ে থাকত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি—হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা।
শামসুন্নাহার মাহমুদকে ১৯৩৩ সালের ৭ নভেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিতে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বিষয়ে কবি লিখেছিলেন—আমি পারস্য ইরাক ইজিপ্ট ভ্রমণ করে এসেছি। বহু শতাব্দীর মোহান্দকার ভেদ করে সর্বত্রই নবপ্রভাতের আলোক আজ প্রকাশিত, সর্বত্রই সেখানকার নানা লোকের মুখে শুনে এলেম ভারতবাসীর অন্ধতার প্রতি ধিক্কার। স্পষ্ট উপলদ্ধি করেছি আজকের দিনে নবজীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত সমস্ত প্রাচ্য মহাদেশের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তির ক্ষেত্রে কাঁটাগাছ রোপণ করে বসেছি। এই মূঢ়তার অপমান সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আজ অনাবৃত্ত অথচ হতভাগ্য দেশে এর প্রতিকার আজ এত দুঃস্বাধ্য।
ময়মনসিংহের করিমগঞ্জের জুট রেজিস্ট্রেশনের সহকারী ইন্সপেক্টর কাজী আহমদকে লেখা চিঠিতে জানা যাচ্ছে কবি ধর্মান্ধদেরকে ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিকারী হিসাবে মনে করেন। তিনি লিখেছেন —ধর্ম যদি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে খর্ব্ব করে তার চেয়ে শোচনীয় কিছু হতে পারে না। যারা সর্ব্ব মানুষের এক ঈশ্বরে যথার্থ বিশ্বাস রাখেন তারা কোনো কারণেই মানবকে অপমান করে নিজের ধর্মকে অপমানিত করতে পারে না। এই আমার মত। ক্ষুদ্র হৃদয় যাদের ঈশ্বরের সিংহাসনকে তারা সংকীর্ণ করে—এটা আপরাধ।
এই অপরাধের জন্য তিনি কঠোরভাবে সেকালের হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই দায়ী করেছেন। তবে সেই অপরাধটা কিন্তু নিম্নবর্গীয় হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে দেখতে পান নি। শিলাইদহ সহ পূর্ব বঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করার সময়ে তিনি নিম্নবর্গের বাউলদের দেখেছেন। সে অভিজ্ঞতা থেকে কবি লিখেছেন—আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অর্ধ অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে; কোরান পুরানে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।
হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বটা শুরু হয়েছিল বৃটিশদের আগমণের পরে। বৃটিশ বেনিয়ারা শুরুতে শাসক মুসলমানদের বদলে হিন্দুদের শাসনকার্যে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। মুসলমানরা ইংরেজদের শত্রুজ্ঞানে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে শিক্ষা দীক্ষা অর্থ বিত্তে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে যায়। তবে এই এগিয়ে যাওয়াটা কিন্তু উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়েই ঘটে। এদেরকে বাবু হিসাবে গণ্য করা হত। মুসলমানদের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে ইংরেজরা যতটা দায়ী—ততটা মুসলমান সম্প্রদায় নিজেরাও দায়ী। তারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। এবং এক্ষেত্রে হিন্দুরাও দায়ী। কারণ ক্রমঅগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায় অর্থনীতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সমতা আনার কোনো চেষ্টা করে নি। বরং তারা তাদেরকে সামাজিকভাবেও পিছিয়ে যেতে দিয়েছে। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা থেকেই সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ যখন এই সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দেখেন তখন কিন্তু নির্মোহভাবে সকলের ছিদ্রটাকে দেখিয়ে দেন। এবং একটা বিষয় স্পষ্ট যে এই বিভেদটা উচ্চবিত্ত হিন্দু ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাবুদের মধ্যেই ছিল। তারা একে পুষ্টি দিয়েছে। অথচ নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না। নিম্নবর্গের একজন জোলা মুসলমান এবং একজন নমশুদ্র হিন্দু সমভাবে এই বাবুদের কর্তৃক অপমানিত ও শোষিত হয়েছে। গোরা উপন্যাসের দরিদ্র চাষী ফরু সর্দার যখন জমিদার বা ইজারাদারদের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখন তাকে সহযোগিতা করে হিন্দু নাপিত। আবার যখন মুসলমান অধ্যুষিত পাবনা সিরাজগঞ্জে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিল একজন হিন্দু প্রজা। তাঁর সহযোগী মুসলমান প্রজা। ইতিহাস বলে এই বাবু হিন্দুরা যেমন নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানকে শোষণ করেছে—একইভাবে মুসলমান জমিদার-ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিম্নবর্গের স্বধর্মের প্রজাদের দিক থেকে। ভুলে গেলে চলবে না-- সেকালে বাংলায় মুসলমান জমিদার শ্রেণীর সংখ্যাও কিন্তু কম ছিল না। তারা এই নিম্নবর্গের মুসলমান প্রজাদেরকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে হিন্দুর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে। আবার নিম্নবর্গের হিন্দুদেরকে প্রতিবেশী মুসলমানের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফেসাদে নামিয়েছে। দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করেছে। নিম্নবর্গের মানুষের স্বার্থরক্ষার র জন্য শিক্ষিত ধনী হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই কখনো ভাবেন নি। তাদের জন্য কাজ করেন নি। তারা নিজেদের আখের গোছানোর রাজনীতিটা করেছেন। তাদের এই রাজনীতিটা কখনো ধর্মরক্ষায় ছিল না। ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দুদের সঙ্গে উচ্চবিত্তের মুসলমানদের ক্ষমতার লড়াই। প্রতিটা দাঙ্গার ইতিহাসটাও এই রকম। এগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে--এগুলো ধনীগরীবের লড়াই। শোষক-শোষিতের লড়াই। শোষকদের মধ্যে যেমন সম্প্রীতি আছে, আবার শোষকদের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে লড়াই আছে। ধর্মকে—সম্প্রদায়-বিভেদকে এই শোষক শ্রেণীই নানা কায়দায় ব্যবহার করেছে।
কবি ঠিকই বুঝেছেন যে, ভারতের স্বরাজ-সমস্যার অন্যতম প্রধান বাধা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের বৈষম্য—অর্থাৎ একদিকে সামাজিক ভেদবুদ্ধির পাপ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই স্বার্থ প্রধানত উপরতলার মানুষের, এবং দুই পক্ষেরই সাধারণ গ্রামীণ জনতা এই স্বার্থবুদ্ধির শিকার। আর এই খেলায় বাতাস দিয়েছে শাসক ইংরেজের চতুর কুটনীতি।
ব্যাধি ও তার প্রতিকার লেখায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলো ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখে দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মুনষ্যোচিত., যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বরকে কোনোদিনই ক্ষমা করিতে পারিবেন না।
হিন্দু ও মুসলমান নামে একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অন্য দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত নিতান্ত ভালোভাবে মেশামেশি করিতেন। তাঁহাদের মা-মাসিগণ ঠাকুরানীদের কোলো পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারি দিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হিন্দুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন—সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইট এবং অপর পক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ হইয়াছে।
তিনি রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ১৯০৮ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে—কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের মহৎ কোনো আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রিয় কর্তব্য-পালনই পদে পদে দুরূহ হইতে তাকিবে।
কবি তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেখেছেন, বাইরে থেকে এই বিভেদকে উস্কানী দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেটা ব্যাধির লক্ষ্মণ—ব্যধি নয়। ব্যাধিটা রয়েছে আমাদের মধ্যে। সুতরাং ব্যাধির প্রকাশ নিয়ে হাক পাড়লেই হবে না। ব্যাধির কারণটা দুর করতে হবে। ব্যাধির কারণটা দুর করা গেলে ব্যাধির প্রকাশটাও দূরে চলে যাবে। তখন মিলনের জন্য হাপিত্যেশ করা লাগবে না। একই হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হবে আপনিতে। তখন হিন্দু মুসলমানের সুবিধার্থে, মুসলমান হিন্দুদের সুবিধার্থে মিলবে না—অসুবিধায়ও মিলবে। সুখে মিলবে—অসুখে মিলবে। আনন্দে মিলবে—বেদনায়ও মিলবে। এটাই আত্মার মিলন। সুবিধা কথাটাই সব সময় সন্দেহজনক। সুবিধার পরিস্থিতিটা চলে গেলে অসুবিধা চলে আসে। তখন সকল ব্যবস্থাই ফাঁকি বলে মনে হয়।
হিন্দু মুসলমান রচনায় এই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করে বলেছেন -- আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষাঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরীক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।
রবীন্দ্রনাথ এই বিভেদের কারণটি আরও সুর্নিদিষ্ট করে উন্মোচন করেছেন-- আমরা গোড়া হইতেই ইংরেজির ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে মিটিয়া না গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্তাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। পদ-মানশিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উটে ইহা হিন্দুদের পক্ষেই মঙ্গলকর।
সমস্যা প্রবন্ধে কবি বলেছেন, ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। এই সমকক্ষতা তাল ঠোকা পালোয়ানীর ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।
হিন্দু মুসলমান রচনায় দেখিয়েছেন দিনে দিনে কীভাবে এই ভেদরেখাটি ঘনীভূত হচ্ছে। কবি বলেছেন, এই সমকক্ষতার অভাবে ভেদটা এমন দাঁড়িয়েছে যে ধর্মমতে হিন্দুর বাঁধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা অন্যদিকে সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?
সমস্যা রচনায় তিনি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায়না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে। ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো বলে ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর।
গোরা উপন্যাসে পরেশবাবু নামে একটি চরিত্র বলেছিলেন, একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি এমন আপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না, অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতে হয়। আরেকটি জায়গায় বলেছেন, ‘আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য ঘৃণা করছে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।‘ হিন্দুতে মুসলমানে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। হিন্দুতে-হিন্দুতে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। এসেছে মুসলমানে মুসলমানে। আশরাফে আতরাফের সেই জাতিভেদের অসাধারণ উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে দেখেন নি। দেখেছেন বাস্তবতার ভিতর থেকে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা প্রচলিত হিন্দুত্ববাদিদের সন্তুষ্ট করে না। তাদের বিরুদ্ধেই যায়। তিনি হিন্দুত্বের অন্যতম পরিচায়ক ধূতি চাদরকে জাতীয় পোষাক হিসাবে বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন ধূতি পাঞ্জাবী আধুনিক নয়। অফিস আদালতের উপযোগী নয়। এর বদলে তিনি জাতীয় পোষাক হিসাবে চাপকানকে বেছে নিয়েছেন। এই চাপকান পরা নিয়ে সেকালে কোনো কোনো হিন্দু আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন চাপকানটা মুসলামানী ড্রেস। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মিলনের উৎসের মধ্যে থেকেই চাপকানকে থেকে থাকেন। বলেন, মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমনই ঘনিষ্ট আদানপ্রদান হইয়াছে গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দু মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে সকল পরিবর্তনেরই মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়ের সহায়তা করিয়াছে। এখনো পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়, সে-বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব তাহা নহে, তাহার জন্য হিন্দুদেরও স্বাধীনতা আছে।
তিনি এরপরই দিচ্ছেন সঙ্গীতের উদাহরণ। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, উহাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে। যেমন মুসলমান-রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।
তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্সকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্ভাবাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন প্রাণশক্তির দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল—চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দণ্ডকার্য, নৃত্য, গীত এবং রাজকার্য, মুসলমানের ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে।
কিন্তু ধীরে ধীরে একটি দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমানে হয়েছে। সেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মনের মিলনের অভাব। ঠিক এইখানে দার্শনিক কারণের মধ্যে তিনি থাকেন না। তিনি দেখেছেন আসলে মনের মিলটা অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করে। এই অর্থনীতিক অসাম্য দূর করতে না পারলে কোনো মিলনপ্রচেষ্টাই ভেতর থেকে হবে না। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাটা যে অসত্য ছিল না তার প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় বঙ্গবিভাগের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন চলে যায়। তারা মনে করেছিলেন মুসলমানদের জন্য আলাদা ভুখণ্ড হলে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় অর্থনীতক বৌদ্ধিক সর্বপ্রকার উন্নতির দিকেই চলে যাবে।
কবি বলেন--আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ বেশি তাহার পক্ষে বেশি হইবে কিনা, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ। এই বিভেদকে দূর করার জন্য তিনি অর্থনৈতিক-সামাজিত অসমতা দূর করা পাশাপাশি শিক্ষাকে ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসাবে মনে করেন। এ কারণে তিনি পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান জীবনের কথা লেখার আহ্বান জানান। স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতিয় সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য অঙ্গ হওয়া উচিৎ।
বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ-দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকর বিসয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শান্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু মাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না। ...বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্য পুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত। (মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা, রর।)
জীবনের শেষ দিকে কবি ইরাক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে বাগদাদ পৌরসভা থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনইতিহাসের গৌরবের যুগে আপনাদের আরবসভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি জায়গাজুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল; আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় করে আমার দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী সার্বজনীন আদর্শ নিয়ে; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিরিয়ে দিন তাঁরা।
মানুষের মধ্যে যা-কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই, আপনাদের মহানুভব ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করি—মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য নির্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাত্বভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে ভারতের জাঈয় চেতনা জর্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা, তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আজ আপনাদের কবিদের আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্ররণ করুন, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তিলাভের পথ।
বন্ধুগণ, আজ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অভাব মোচন করাতেই জাতীয় আত্মপ্রকাশের সকল দ্বায়িত্ব শেষ হয় না---দেশকালে সীমানা অতিক্রম করে আপনাদের বাণী পৌঁছানো চাই সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের নৈতিক সমস্যাগুলো আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রয়োজন হলে দ্বিধা না করেই সত্যবাক্য শোনাতে হবে।
মুসলমান খণ্ড—৭
কবি আবদুল কাদিরের দিলরুবা কাব্যগ্রন্থখানি ১৯৩৩ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পেয়ে আবদুল কাদিরকে জানান তিনি বইখানি পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। ভাষা ও ছন্দে আবদুল কাদিরের প্রভাব অপ্রতিহত। এবং কবি তাঁর প্রশংসা করে লেখেন, বাংলার কবি সভায় তোমার আসনের অধিকাংশ অসংশয়িত।
তারপর কবি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন—বিষয় অনুসারে যে কবিতায় তুমি মাঝে আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার করেছ আমার কানে তা অসঙ্গত বোধ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আবদুল কাদিরের কবিতার উপর শুধু চোখ বোলাননি। জহুরীর মত খুটে খুটে দেখেছেন তার ভাব, ভাষা, ছন্দ ও শব্দ। ফলে ঐ চিঠিটি সংক্ষিপ্ত হলেও কবি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চোখা মন্তব্য করেছেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিনের মুসলিম বীরাঙ্গনা বইটি সম্পর্কে। লিখেছেন, উদ্দীপনার বেগে মুসলিম বীরাঙ্গনার ভাষাসংযম রক্ষা হয়নি, বলবৃদ্ধির চেষ্টায় তার বলহানী করা হয়েছে। চিঠিটি লেখা হয়েছিল আবদুল কাদিরকে ১৯৩৮ সালে।
আবদুল কাদিরের চিঠিটি পড়েছিলেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পড়ে তিনি কবির সঙ্গে মুসলিম বীরাঙ্গনা অন্যান্য দিক বিষয়ে কবির কাছ থেকে শোনার জন্য আলাপের আগ্রহ বোধ করেন। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিনকে ১৯৩৮ সালের ১৫ জানুয়ারি কবি চিঠিতে লেখেন, মুসলিম বীরাঙ্গনার আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার নিয়ে কোনো আপত্তি করিনে। আমার বক্তব্য এই যে, ঐতিহাসিক যে সকল ঘটনার মধ্যেই স্বতঃই বীরত্বের প্রকাশ আছে তাদের বিবরণ যত সহজ হয় ততই তাদের নিজের দিপ্তি সুস্পষ্ট থাকে, লেখক যদি ব্যগ্র হয়ে কলমের উত্তেজনা প্রয়োগ করেন তাহলে ইতিহাসের স্বাভাবিক শক্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হয়—পাঠকের চিত্ত যে অসাড় নয় একথা ধরে নেওয়া ভালো।
এইটুকু লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটিতে তারিখ বসিয়েছেন। চিঠিটি এখানেই শেষ হতে পারত। তিনি শেষ না করে আরেকটি বাক্য যুক্ত করেছেন তারিখের পরে—বইখানি (মুসলিম বীরাঙ্গনা) সাধারণের পাঠোপযোগী তাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বইটির বিষয়বস্তুকে তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বইটির শব্দ ব্যবহার নিয়ে কিছু অনুযোগ করেছেন।
মুসলিম বীরাঙ্গনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ভিত্তি দটো—
১. ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্য রচনার বিবরণ সহজ হওয়া দরকার।
২. লেখকদের আবেগ প্রকাশ করা ভালো কথা নয়।
৩. পাঠককে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রতিটি চিন্তাই সৃজনশীল বলেই বহুরেখিক। এই বহুরৈখিকতাকে লেখক সম্মান না করলে তার বিষয় ক্লিশে হয়ে পড়ে।
শব্দ ব্যবহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতটা সোজা সাপটা। ইচ্ছে করলেই তাঁকে আবার ভুল বোঝার অবকাশও আছে। কবির ক্ষেত্রে সে রকম ভুলও করা হয়েছে। সে ভুলটা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১৫০ বছর পরেও কেউ কেউ কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে দেখিয়ে থাকেন।
আবুল ফজলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল ঢাকায় ১৯২৬ সালে। ঢাকা বিশ্বিবদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন ৩১ আগস্ট। ১৯৪০ সালে আবুল ফজল তাঁর লেখা চৌচির ও বিচিত্র কথা বই দুটি পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে গল্পকার আবুল ফজল লিখেছিলেন—
‘গল্পগ্রন্থ দুটিতে বঙ্গের পূর্ব সীমান্তবাসী মুসলমান সমাজ ও পরিবার-জীবনের কিছু কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তাদের মুখের ও জীবনের সাহিত্য এখনো অপ্রচলিত বহু শব্দ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আমার বিবেচনায় মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে গেলেই এ রকম বহু অপ্রচলিত শব্দ বাংলা ভাষাকে হজম করতেই হবে।
মুসলমান নায়িকা মুসলমান নায়ককে দস্তরখানা বিছিয়ে নাস্তা পরিবেশন করছে, বহু ভেবেও এরকম বাক্যকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তিত করতে পারিনি। দস্তরখানার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আমি খঁজে পাইনি, তৈয়ার করে নিতেও পারিনি। অথচ দস্তরখানা মুসলমান পরিবারে রোজ দুবেলাই ব্যবহার করা হয়। নাস্তার প্রতিশব্দ জোর করে হয়ত ‘জলখাবার’ করা যায়, কিন্তু তা করলে মুসলমানের কানে তা শব্দের শুদ্ধিকরণের মতই শোনাবে। আর নিশ্চিত মুসলমান জীবনেও শব্দের ব্যবহার না হয়ে পোষাকী হয়েই থাকে।
হাসান সোহরাওয়ার্দীর বাড়ির জেয়াফতে আমার দাওয়াত আছে, এর পরিবর্তে কোন মুসলমান হাসান সোহরাওয়ার্দীর বাড়ির ভোজে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলে না, বল্লে অনুবাদের মত শোনাবে।‘
আবুল ফজল চিঠির শেষ দিকে বলেছিলেন, যে জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রূপ নেবে, সে জীবনের পরিবেষ্টনকে বাদ দিয়ে সে সাহিত্যের অন্য কোনো স্বধর্ম আশা করা যায় কিনা ভাববার বিষয়। ব্যাকরণ ও অভিধান ঘেটেই সম্ভবত সে স্বধর্ম খুঁজে বের করতে হবে।
চিঠিতে সর্বশেষে তার রচনায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের সাহিত্যে ব্যবহার সম্পর্কে কবির অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ চোখে কম দেখেন। পড়তে কষ্ট হয়। ডাক্তার চোখকে বিশ্রাম দিতে বলেছেন।
আবুল ফজলকে এর দিন ছয়েক পরে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ বেশ বড়ো সড়ো একটা জবাব পাঠান। শুরুতেই কবি জানাচ্ছেন, ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিকই বলছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না, তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূল করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মন্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথা আমদানী করে এসেছে। বাংলাভাষায় পারসী আরবি শব্দের সংখ্যা নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটি বিধান আছে যার দ্বারা নতুন শব্দের যাচাই হতে থাকে।
ধরা যাক খুন শব্দটি। এটা হত্যা বা কিলিং অর্থে আমাদের ভাষায় পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। এই শব্দটি থেকে খুরোখুনি, খুন খারাবি বা খুন জখমও হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম মোহররম কবিতায় লিখেছেন--
নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,-
“আম্মা ! লা’ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া !”
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !
এ কবিতায় খুন শব্দটি রক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু খুন শব্দটি এখানে রক্ত অর্থে ব্যবহার করায় অর্থের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে খুনের বদলে রক্ত অর্থে প্রচলিত কোনো শব্দ বসালেই যুক্তিযুক্তি হত।
এর পরেই রবীন্দ্রনাথ খুনের মামলাটি করে বসেন। তিনি লিখেছেন—‘খুন খারাবি’ শব্দ ভাষা সহজে মেনে নিয়েছে। আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামী, কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি। কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ওই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ওই অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে।
এ সময় কোনো কোনো মুসলিম লেখক বা পত্রিকাগোষ্ঠীর বাংলার শব্দের সঙ্গে অকাতরে এবং অসাহিত্যজনোজিতভাবে আরবী-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা দেয়। এমন কি তাদের মাতৃভাষা কী হবে এ সংশয়ও গ্রাস করে। এ বিষয়গুলো নিয়ে আলতাফ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা করছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশভাষাকে পীড়িত করবার চেষ্টা কোনো সভ্য দেশে দেখা যায়নি।
রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালি বলে মনে করেন বলেই এই অনুযোগটি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেমের মুসলমানকে যদি বাঙ্গালি বলে গণ্য না করতুম তাহলে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা না করে সান্ত্বনা পেতুম।
শব্দের কোনো ধর্ম হয় না। ধর্মেরও কোনো শব্দ হয় না। শব্দ জীবনাচরণের সঙ্গে গড়ে ওঠে, ব্যবহৃত হয়—শব্দ বেঁচে থাকে, রূপান্তরিত হয এবং কখনো কখনো শব্দ মরেও যায়। আবার মৃত শব্দেরা পূনর্জীবিতও হয়। ধরা যাক পিতা শব্দটি। যাত্রাপালায় এখনো ব্যবহৃত হলেও হতে পারে। কিন্তু শব্দটি এখন বাহ্যত আমাদের জীবন থেকে দুরে চলে যাচ্ছে। শব্দটি সংস্কৃত। তবুও কোনো হিন্দুও বর্তমানে পিতা শব্দটিকে সচরাচর ব্যবহার করে না। বাবা শব্দটি সকল বাঙ্গালি ব্যবহার করেন। বাবা শব্দটি আরবী।
মার্কিন দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্প্যানিস প্রচলিত। স্প্যানিস ভাষায় বাবা শব্দ হল পাপী। কিন্তু বাংলায় বাবা শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে পাপী শব্দটি অপরিচিত। যারা স্পেন দেশে থাকেন বা স্প্যানিস ভাষা জানেন তারা হয়তোবা পাপী বলে মাঝে সাজে সম্বোধন করে থাকেন। বাংলায় পাপী শব্দটির অর্থ যে পাপ করেছে বা ইংরেজিতে সিনার। বাংলা ভাষায় পাপী শব্দটা ব্যবহার করলে শব্দটি পাঠকদের কাছে অনর্থ হয়ে উঠবে। কেউ-ই পাপী হতে চাইবে না। প্রবল আপত্তি করে বসবে। সেক্ষেত্রে ইংরেজী ফাদার শব্দটি বাংলায় এত বেশী পরিচিত যে ফাদার বললে বা লিখলে কেউ আপত্তি করবে না।
সাধারণ লোকের ধারণা বাবু শব্দটি হিন্দু সংস্কৃত শব্দ—সংস্কৃত শব্দ থেকে উঠে এসেছে। বাবু শব্দটি হিন্দুদের নামের আগে দেওয়া না হলে অসম্মানজনক মনে হত। মনে করা হয় বাবু শব্দটি হিন্দু ভদ্রলোক বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। আবার মুসলমানদের সাহেব বলাই চল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুর বাশার জানাচ্ছেন-- বাবু শব্দটা ফার্সি। সাহেব শব্দটাও ফার্সি। সুতরাং বাবু শব্দটাতে হিন্দুত্ব খোঁজার কোনো মানেই হয় না। যদি সেটা করা হয় সেটা সাম্প্রদায়িকতা হবে। বাবু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল ‘বু’ মানে গন্ধ এবং ‘বা’ মানে সহিত বা সাথে। অর্থাৎ গন্ধের সহিত অর্থাৎ যে গন্ধ মাখে, সে-ই হচ্ছে ‘বাবু’। সেজন্য কলকাতার বাবু মানে হল সুগন্ধিত হয়ে যে রাস্তায় বেরোয় তার থেকে বাবু, বাবু-সম্প্রদায়। বাবু সম্প্রদায় কলকাতায় জন্মেছিল—তারা জমিদার বা উচ্চবিত্ত। জমিদারদের ভেতর থেকেই তথাকথিত অভিজাত হিন্দু জমিদারদের বাবু বলা হত। পানি শব্দটা আরবী নয়। এটা প্রাকৃত হিন্দি। পানীয় শব্দটা সংস্কৃত। পানীয় থেকে পানি হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই জলকে পানি বলছে। আবার বাংলাদেশের এক সময় সবাই জলই বলত। এখন হিন্দু-মুসলমান সবাই জলকে পানি-ই বলতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুরা জলকে পানি বলে পান করবে না। আঙ্কেল শব্দের বাংলা কাকা শব্দটিও সংস্কৃত নয়। চাচা শব্দটির মতই কাকা শব্দটিও বিদেশী।
রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ কবিতাটি বহুল পঠিত। হিন্দু পুরাণ থেকে বিদায় অভিশাপের কাহিনীটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন বিদায় শব্দটি আদৌ সংস্কৃত জাত নয়—একটা আরবী শব্দ। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু পুরাণের গল্প নিয়ে কাহিনী-কবিতা লিখেছের আরবী শব্দ ব্যবহার করে। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—লতা মুঙ্গেস্করের গাওয়া এই গানটি বাংলার সকল মানুষে প্রিয় গান। এই গানের মা শব্দটির মধ্যে যারা সংস্কৃত বা ব্রাহ্মণ্যত্ব খোঁজেন তারা বিদায় শব্দের বেলায় কি করবেন? বাতিল করে দেবেন? আফ্রিকান এবং স্প্যানিস ভাষাতেও মা মানে স্নেহময়ী জননী।
উলু শব্দটি বিষয়ে বঙ্গীয় শব্দার্থকোষে কলিম খান লিখেছেন—বিবাহাদি উৎসবে স্ত্রীলোকের করণীয় মঙ্গলধ্বনিবেশেষ। নিজেদের কোনো সাফল্য প্রকাশ করার জন্য যে ধ্বনি করা হয়, সেটি উলুধ্বনি নাম পেয়েছে। হিন্দু নারীরাই শুধু উলুধ্বনি দেয় না, বিভিন্ন উৎসবে আনন্দে বিয়ে সাদিতে আরবের নারীরাও উলুধ্বনি দেয়। কোনো দেশের খ্রিষ্টানরাও দেয়। হিব্রু ভাষায় হালেলুইয়া নামে একটি শব্দ আছে। ঈশ্বরের উদ্দশ্যে সমবেত ইহুদিরা জয়ধ্বনি করে এই হালেলুইয়া শব্দের মাধ্যমে। কলিম খান মনে করেন এই হালেলুইয়া উলু ধ্বনির জ্ঞাতি।
বই শব্দটি এসেছে আরবী অহি শব্দ থেকে অর্থাৎ বই শব্দটি আল্লার চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। অহি হচ্ছে ঈশ্বর বা আল্লার প্রত্যাদেশ। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ অহি পেতেন। এই অহি শব্দ থেকেই বহি—বহি থেকে বই শব্দটি এসেছে। বই শব্দটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ একটি শব্দ। কিন্তু এক সময় বইকে হিন্দু শব্দ বলে বাতিল করে মুসলমানী শব্দ হিসেবে কিতাব শব্দকে প্রচলন করা হয়েছিল। তৃতীয় বড় বোনকে বা দিদিকে সেজ দিদি বা সেজদি বলা হয়। সেজ দিদির মধ্যে আছে সেহ্ । সেহ্ শব্দটি ফার্সি। সেহ্ শব্দটির অর্থ তিন। যেমন সেতার—তিন তারের সমাহার। ফার্সি সেহ্ এর সঙ্গে সংস্কৃত-ধাতু ‘জ’ যুক্ত হয়ে সেজ শব্দটি তৈরি হয়েছে। অফিস-আদালত-জমি-জিরাত ফার্সি শব্দ। বাংলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ব্যবহার করেন। এগুলো এখন বাংলা শব্দ-ই। আবার কেদারা শব্দটি চেয়ার অর্থে বাংলায় টেকেনি। চেয়ার শব্দটিই চলেছে। জরকাঠি শব্দটির জন্মমাত্রেই মৃত্যু ঘটেছে। জরকাঠি দিয়ে নয়--থার্মোমিটার দিয়েই বাঙ্গালিদের জ্বর দেখা হয়।
আবার তৎসম শব্দ নির্বান, যোগ, প্রাণায়াম—ইংরেজীতে দিব্যি নির্বানা, ইয়োগা এবং প্রাণায়ামা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি ‘বাৎসায়নের কামসূত্র’টি কামসূত্র নামেই মার্কিন দেশে লেখা হয়। মেডিটেশন শব্দটির সঙ্গে ধ্যান শব্দটি জায়গা করে নিচ্ছে। এই সব সংস্কৃতজাত বাংলা শব্দগুলি ইংরেজীতে ধীরে ধীরে মিশে গেছে। কেউ আপত্তি করছে না। হালাল বা হারাম শব্দটির সঙ্গে মার্কিনীরা পরিচিত। রেস্তোরাতে বড় বড় করে লেখা হয়—হালাল ফুড। কেউ মুসলিম শব্দ করে হেলা করে না। এখন হালাম বা হারাম শব্দদ্বয় বাংলা ভাষারই অন্তর্গত। কিন্তু উর্দু শব্দ ‘সাজিস’ ষড়যন্ত্র শব্দ হিসেবে অপরিচিত। সুতরাং সাজিস শব্দটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে ব্রাকেটে ষড়যন্ত্র অর্থটি বলে দেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ এইখানেই আপত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—যে শব্দ সাধারণ্যে ব্যবহৃত বা প্রচলিত সে শব্দ ব্যবহারে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের লাভই হবে। এ কারণে তিনি আহ্বান করেছিলেন মুসলমান সাহিত্যিকদের লেখালেখিতে আসতে। তারা লিখলে তাদের ঘরে ব্যবহৃত শব্দ সাহিত্যের ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে। ভাষাগত অসাম্যতা দূর হবে। হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রদায়গত বিভেদও কমে আসবে— তাদের মিলনের পথ দেখাবে।
তিনি আবুল ফজলকে চিঠিতে বলেছেন, আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা অই সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি।... চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ভুল ঘটতে থাকবে।
এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ভাষা বা সাহিত্যে সম্প্রদায়গত ভেদরেখায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর দুরাশা গল্পটি এক মুসলমান রমনীকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি উর্দু জবানী ব্যবহার করেছেন। এই রমনীটি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর মেয়ে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষায় লিখেছেন। গল্পে রমনী বলছেন, বাবুজী, এক সময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইদের প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত। আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই। ...তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ অবলীলায় জেনানর বদলে মহিলামহল, পর্দার বদলে ঘোমটা বা আড়াল, বিবিসাহেবার বদলে বউঠান, মাপ করোর বদলে ক্ষমা করো বসাতে পারতেন। সেটা না করে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন—সেগুলো মুসলমান উচ্চবিত্ত পরিবারের নিত্যব্যবহার্য শব্দ। এই শব্দগুলো আমাদের বাঙ্গালী সমাজেও অপরিচিত নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ এ শব্দগুলোকে মুসলমানী শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন নি। মানুষের শব্দ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। একজন মুসলমান নবাব নন্দিনীকে বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে অবিকৃতভাবে শব্দগুলির ব্যবহার সিদ্ধ মনে করেছেন।
ঠিক এই গল্পের অন্যত্রই তিনি সংস্কৃতবহুল শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন, হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালীদাস-রচিত মেঘদূত-কুমার সম্ভবের বিচিত্র সঙ্গীত মর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিন্টস পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমনীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্নভাবে অনুভব করিতে পারে, এমত নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে।
আমরা ধীরে ধীরে টের পাই রবীন্দ্রনাথের বয়স বাড়ছে আর তিনি তাঁর ভাষার শরীর থেকে সাধুভাষার এই বাহুল্য ছেড়ে যাচ্ছেন। সংস্কৃতশাসিত ভাষাকে মুক্ত করার জন্য এককভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন। লড়াইয়ে জয় তাঁরই হচ্ছে। বাঙ্গালীর জীবনের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে তিনি নির্মাণ করছেন । সে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান। কোনো ভেদ নেই। পদ্মায় তাঁর নৌকার মাঝি ঝড় এলে আজান দিয়ে উঠেছে। মুসলমান মাঝিটির আল্লা শব্দটি তাঁর কলমে আল্লা শব্দ হিসেবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাগজের বুকে নেমে এসেছে। একটুকু দ্বিধা আসে নি রবীন্দ্রনাথের মনে। আল্লা সার্বজনীন মানুষেরই শব্দ।
সংযুক্ত
শব্দতত্ব/ রবীন্দ্রনাথ
... সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক্ তবু বাংলার সাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রীমহাশয়ের। এ কথা শুনতে যত সহজ আসলে তা নয়। ভাষায় বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার বেশির ভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে পাওয়া। এই শব্দের কোনোটাকে বলি তৎসম, কোনোটাকে তদ্ভব।
ছাপার অক্ষরে বাংলা পড়ে পড়ে একটা কথা ভুলেচি যে সংস্কৃতের তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নেই বললেই হয়। "অক্ষর" শব্দটাকে তৎসম বলে গণ্য করি ছাপার বইয়ে; অন্য ব্যবহারে নয়। রোমান অক্ষরে "অক্ষর" শব্দের সংস্কৃত চেহারা তযড়বতক্ষত বাংলায় ষযযবতক্ষ। মরাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রায় সংস্কৃতেরই মতো, বাংলায় তা নয়। বাংলার নিজের উচ্চারণের ছাঁদ আছে, তার সমস্ত আমদানি শব্দ সেই ছাঁদে সে আপন করে নিয়েছে।
তেমনি তার কাঠামোটাও তার নিজের। এই কাঠামোতেই ভাষার জাত চেনা যায়। এমন উর্দু আছে যার মুখোশটা পারসিক কিন্তু ওর কাঠামোটা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় উর্দু ভারতীয় ভাষা। তেমনি বাংলার স্বকীয় কাঠামোটাকে কি বলব? তাকে গৌড়ীয় বলা যাক্।
কিন্তু ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা স্বাজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অব্রাহ্মণ যদি পৈতে নেবার দিকে অত্যন্ত জেদ করতে থাকে তবে বোঝা যায় যে, নিজের জাতের পরে তার নিজের মনেই সম্মানের অভাব আছে। বাংলা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃত বলে চালালে তার গলায় পৈতে চড়ানো হয়। দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেকদিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেছে; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদিবা হয় তবু পতিতব্রাহ্মণ, অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায় চোখের আড়ালে রাখা কর্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলাদেশে "মস্ত ভিড়"কে কোথাও যেন কবুল করা না হয় স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় "মহতী জনতা"কে।
এমনি করে সংস্কৃত ভাষা অনেক কাল ধরে অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা ভাষাকে অপত্য নির্বিশেষে শাসন করবার কাজে লেগেছিলেন। সেই যুগে নর্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধ হয় ঘটত না। তখন যে-ভাষাকে সাধুভাষা বলা হত অর্থাৎ যে-ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আদ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের সমাসদর্পণ আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমারমতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমারমতি ছিল।
ভাষা সম্বন্ধে আর্য পদবীর প্রতি লুব্ধ মানুষ আজও অনেকে আছেন, শুদ্ধির দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি-- তাই কান সোনা পান চুনের উপরে তাঁরা বহু যত্নে মূর্ধন্য ণ-য়ের ছিটে দিচ্ছেন তার অপভ্রংশতার পাপ যথাসাধ্য ক্ষালন করবার জন্যে। এমন-কি, ফার্সি দরুন শব্দের প্রতিও পতিতপাবনের করুণা দেখি। "গবর্নমেন্টে"র উপর ণত্ব বিধানের জোরে তাঁরা ভগবান পাণিনির আশীর্বাদ টেনে এনেছেন। এঁদের "পরণে" "নরুণ-পেড়ে" ধুতি। ভাইপো "হরেনে"র নামটাকে কোন্ ন-এর উপর শূল চড়াবেন তা নিয়ে দো-মনা আছেন। কানে কুণ্ডলের সোনার বেলায় তাঁরা আর্য কিন্তু কানে মন্ত্র শোনার সময় তাঁরা অন্যমনস্ক। কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তাও চোখে পড়ল,-- অথচ কানাই পাহারা এড়িয়ে গেছে। মহামারী যেমন অনেকগুলোকে মারে অথচ তারি মধ্যে দুটো একটা রক্ষা পায়, তেমনি হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যে বাংলায় মূর্ধন্য ণ অনেকখানি সংক্রামক হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় নতুন গ্র৻াজুয়েট এটার উদ্ভব তাঁদেরি থেকে, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লাগল ছাপাখানার কম্পোজিটরকেও। দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।
প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলেই মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্ম, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল। তাঁরা প্রমাণ করতে চান নি যে ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সমস্তই হিমালয়ের মাথার উপরে জমাট করা বিশুদ্ধ বরফেরই পিণ্ড। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।
ঘরে বাইরে উপন্যাসে মুসলমান
আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র— কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিঁকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।
--এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমর স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী
--এইরকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কালেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কালেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স্ পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।
আমি বললুম, সে আমি পারব না।
তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে?
বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।
মাস্টারমশায় ছিলেন ; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।
তারা বললে, দেশের জন্যে—
মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এইসমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?
তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেছি।
তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিঁকে থাকবার জন্যে— ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না— ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে ; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত— আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।
তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?
আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।
এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?
আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি ; এমন-কি, অন্য এলেকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই—
সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।
আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয় ; তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।
মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।
সায়ান্স্ ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।
মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয়
জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম ব্যাবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না ; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে— আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।
এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে ; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব’লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।
মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?
আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।
এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।
মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।
তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ‘বন্দেমাতরং’ বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।
এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?
ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে এক-শো টাকা জরিমানা করেছে।
কেন, ওর অপরাধ কী?
ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব ; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে— লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে এক-শো টাকা জরিমানা।– এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!
কাপড়ের কী হল?
পুড়িয়ে ফেলেছে।
সেখানে আর কে ছিল?
লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন ; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব, বিলিতি ব্যাবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বোরোতে হবে।
আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।
পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষি দেবে না।
কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!
সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?
মৌলানা জিয়াউদ্দিন
আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরো অনেক গভীর।
জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হাল্কা মেঘের মতো। জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ কথা ভাবতে পারি নে। কারণ তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোতভাবে আশ্রমের সব-কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।
তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন করে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে, যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্বতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মতো তেমনি করে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সংকোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে আমরা এক জন পরম সুহৃদকে হারালাম।
প্রথম বয়সে তাঁর মন বুদ্ধি ও সাধনা যখন অপরিণত ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্রমপদক্ষেপে তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সংযোগের পরিণতি মধ্যাহ্নসূর্যের মতো দীপ্যমান হয়েছিল, আমরা তাঁর পূর্ণ বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আশা ছিল আরো অনেক কিছু তিনি দিয়ে যাবেন। তিনি যে বিদ্যার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান তেমন করে আর কে নেবে; আশ্রমের সকলের হৃদয়ে তিনি যে সৌহার্দের আসন পেয়েছেন সে আসন আর কী করে পূর্ণ হবে?
আজকের দিনে আমরা কেবল বৃথা শোক করতে পারি। আমাদের আদর্শকে যিনি রূপ দান করেছিলেন তাঁকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়ায় মনে একটা অক্ষম বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। কিন্তু আজ মনকে শান্ত করতে হবে এই ভেবে যে তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। তাঁর সুস্থ চরিত্রের সৌন্দর্য, সৌহার্দের মাধুর্য ও হৃদয়ের গভীরতা তিনি আশ্রমকে দান করে গেছেন, এটুকু আমাদের পরম সৌভাগ্য। সকলকে তো আমরা আকর্ষণ করতে পারি না। জিয়াউদ্দিনকে কেবল যে আশ্রম আকর্ষণ করেছিল তা নয়, এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন, এখানকার হাওয়া ও মাটির রসসম্পদে, এখানকার সৌহার্দে তাঁর হৃদয়মন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেলেন তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে, তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা ভুলব না।
আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে এরকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর এক দিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে-- এ আমার জীবনে একাট চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।
শান্তিনিকেতন, ৮। ৭। ৩৮
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদা লিখেছিলেন, 'কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত ইসলামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে৷ তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ, অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে৷... শুধু বাংলা ভাষায় কেন, জগতের কোন অমুসলমান কবির হাত দিয়া এমন লিখা বাহির হয় নাই৷' ('ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৯)৷
আমার আরেকটা অভিজ্ঞান হল--বরিশালেই সম্ভব জীবনানন্দের সৃষ্টি। অন্যত্র নয়। বরিশাল হল সৃষ্টিশীলতার জন্মদাত্রী। এখানে হাওয়ায় কবিতা ঘুরে বেড়ায়। আলোতে গল্পর দেখা মেলে। অন্ধকারে জেগে ওঠে উপন্যাসের গভীর মন্দ্রধ্বনি।
৭. ৯. ৮৫
শ্রদ্ধাভাজনেষু
স্যার, সালাম জানবেন। অসুস্থতার জন্যে আপনার চিঠির জবাব দিতে কয়েকদিন দেরী হলো। অনুগ্রহ করে মাফ্ করবেন আমাকে।
ঠাকুর জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ কাঙাল হরিনাথের ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’র কোন্ বর্ষ কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আমার সঠিক জানা নেই। আমাদের কাছে ‘গ্রামবার্তা’র যে ফাইল আছে, তাতে এই সংবাদ নেই। প্রজাপীড়নের এই সংবাদ-সূত্রটি পাওয়া যায় কাঙাল-শিষ্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র একটি প্রবন্ধে। কাঙালের মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে মৈত্রেয়বাবু কাঙাল হরিনাথের সংবাদপত্র পরিচালনায় সততা ও সাহসের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রজাপীড়নের সংবাদ ‘গ্রামবার্তা’য় প্রকাশের উল্লেখ করেন। ঠাকুর-জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে হরিনাথ নিজে অক্ষয়কুমারকে যে পত্র লেখেন, তিনি এই প্রবন্ধে তা উদ্ধৃত করে দেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুষ্ট ও অপ্রসন্ন হন এবং তাঁর অন-রঙ্গ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে অক্ষয়কুমারের ‘রানী ভবানী’ গ্রন'প্রকাশের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করান। কাঙাল-পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার-সূত্রে জানা যায়, ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ-প্রকাশের অপরাধে (?) তাঁরা লাঠিয়াল-গুণ্ডা লাগিয়ে কাঙালকে শায়েস-া করার ব্যবস'া নেন। এইসব ঘটনা ঠাকুর-জমিদারীর ইতিহাসের দুঃখজনক ‘কালো অধ্যায়’।
এ-ছাড়া অন্যত্র, যেমন মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত ‘হিতকরী’ পত্রিকায়, ঠাকুর-জমিদাররা যে প্রজাসাধারণের দুঃখ-কষ্ট মোচনে তেমন তৎপর ও মনোযোগী ছিলেন না তার ইঙ্গিত আছে। ঠাকুরবাবুরা তাঁদের জমিদারী-এলাকায় গো-কোরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই নির্দেশ অমান্যকারীদের নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়। শিলাইদহ ঠাকুর-জমিদারীর এই ভূস্বামী-স্বার্থরক্ষার কৌশল-ব্যবস্থা ও প্রজাপীড়নের ঐতিহ্য চারপুরুষের, দ্বারকানাথ থেকে সুরেন্দ্রনাথ পর্যন-। কাঙাল হরিনাথের দিনলিপিতেও এর ইঙ্গিত মেলে।
শিলাইদহ জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথের আমলেও কিছু অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। চরের মুসলমান প্রজাদের ঢিঁঢ করবার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সামপ্রদায়িক-বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। এ-ছাড়া পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিরীক্ষামূলক শখের কৃষি-খামারের প্রয়োজনে গরীব মুসলমান চাষীর ভিটেমাটি দখল করে তার পরিবর্তে তাকে চরের জমি বরাদ্দের মহানুভবতাও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন। এ-সব কথা ও কাহিনী উক্ত-জীবনীকারদের যত্ন ও সৌজন্যে চাপা পড়ে গেছে। সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরতে গেলে অনেককেই হয়তো সামপ্রদায়িক বা রবীন্দ্র-বিদ্বেষী শিরোপা, নয়তো সুভো ঠাকুরের (‘বিস্মৃতিচারণার প্রতিক্রিয়া’ দ্রষ্টব্য) মতো ধিক্কার ও তিরস্কার অর্জন করতে হবে।
ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা-পীড়নের বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীকে (তিনি নিজে শিলাইদহবাসী ও ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন এবং এই বিষয়গুলো জানতেন) চিঠিপত্রে নানা প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি এ-সব জিজ্ঞাসার জবাব এড়িয়ে ও অস্বীকার করে এই ধরণের কৌতূহলকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করেছিলেন।
উপরি-বর্ণিত বিষয়গুলোর কিছু কিছু তথ্য আমার সংগহে আছে। আপনার প্রয়োজন হলে সেগুলো পাঠাতে পারি। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। এই বিষয়ে আপনি কোন প্রবন্ধ লিখেছেন কী না জানিয়ে বাধিত করবেন। আমার গবেষণার কাজ (‘মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা’) চালিয়ে যাচ্ছি। এ-বছরের মধ্যে থিসিস্ জমা দেবো এমন আশা আছে। আমার লেখার কাজে আপনার প্রশ্রয় ও প্রেরণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আপনার জবাবের প্রত্যাশায় রইলাম। আন-রিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে শেষ করি।
স্নেহসিক্ত,
আবুল আহসান চৌধুরী ৩৬
পাশাপাশি ঠাকুর বাড়ির অন্য জমিদারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও প্রজা-পীড়ন, মুসলমান প্রজা-পীড়নেরও বিষয়েও র অভিযোগ আছে, অভিযোগ আছে প্রজা-নির্যাতনের দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলার, ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখার। খাজনা পরিশোধে অপারগ মুসলমান প্রজার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবার, এমনকি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষা দেবার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে মুসলমানদের এলাকায় বসতি স্থাপনের সামপ্রদায়িক বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদী কাঙাল হরিনাথের পত্রিকা ‘গ্রামবার্তা’য় ঠাকুর জমিদারদের নিপীড়নের অনেক খবর বিবরণ ছাপা হতো। বিশিষ্ট লেখক শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র লেখা ‘সিরাজদ্দৌলা’ গ্রনে'র প্রশংসাসূচক আলোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরে যখন রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর জমিদারদের নানা নিষ্ঠুর ঘটনা উল্লেখ করে কাঙাল হরিনাথ শ্রী অক্ষয় মৈত্রেয়কে চিঠি লেখেন, এবং মৈত্রেয় মহাশয় তাঁর এক প্রবন্ধে হরিনাথের চিঠির ভাষ্য উল্লেখ করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ রুষ্ট হয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র ‘রানী ভবানী’ গ্রন' প্রকাশের অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিদাতা বন্ধু জমিদার নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে প্রত্যাহার করিয়ে নেন। ‘রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন’ প্রবন্ধের জন্য অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ গবেষক অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীকে কাঙাল হরিনাথের ‘গ্রামবার্তা’ এবং ঠাকুর জমিদারদের সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। শরীফ সাহেবের চিঠির উত্তরে অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর লেখা চিঠিতে সংশ্লিষ্ট প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়।
আহমদ শরীফ তাঁর ‘রবীন্দ্র সাহিত্য ও গণমানব’ প্রবন্ধে লিখেছেন --রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের গভীরে প্রোথিত সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়াচেতনা ও স্বার্থবোধ শেষাবধি পরিহার করতে সমর্থ হননি। একজন কারখানা মালিক যেমন তার শ্রমিকদের দাবি আদায়ের মিছিলে সামিল হতে পারে না, সামন্ত বেণে-বুর্জোয়া-জমিদার রবীন্দ্রনাথও তেমনি পারেননি দুস্থ-দুঃখী-চাষী-মজুরের শোষণ-পীড়ণ জর্জরিত জীবনের আলেখ্য আঁকতে। এ হচ্ছে শ্রেণীক ও ব্যক্তিক স্বার্থ চেতনার বন্ধন। নইলে যে রবীন্দ্রনাথ প্রমত্তা পদ্মায় জেলে-মাঝিকে ডুবে মরতে দেখেছেন, পদ্মার যমুনার তীর ভাঙনে হাজার হাজার গরিব চাষী-মজুরকে নিঃস্ব হতে উদ্বাস্তু হতে দেখেছেন, দেখেছেন স্বচ্ছল চাষীকে সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে, প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষে অনাহারে-অপুষ্টিতে-তুচ্ছ রোগে ভুগে ভুগে অকালে অপমৃত্যু কবলিত হতে হাজার হাজার নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নির্বিরোধ মানুষকে। আরো দেখেছেন তাঁরই হুকুমে বা সম্মতিতে তাঁরই গোমস্তাদের খাজনার দায়ে তাঁরই গরিব প্রজার ঘটি-বাটি ক্রোক করতে, প্রজাকে ভিটে-ছাড়া করতে, বারবার দেখেছেন ঝড়-খরা-বন্যা তাড়িতি মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশা ও অপমৃত্যু–সেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল-বিচিত্র রচনায় এদের নাম-নিশানা মাত্র নেই কেন! বোঝা গেল, শোষক তিনি যত বড়ো মহাপুরুষই হোন, শোষিতের পক্ষে লড়াই দূরে থাক, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশেও অনীহ।
শুধু সহানুভূতি প্রকাশে অনিচ্ছুকই নন, নিজেদের শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তিনি। ফলে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। জমিদারী প্রথা যে প্রজা মঙ্গলের জন্য উত্তম সেটাকেই বিশ্বাস করতেন তিনি। সেকারণেই বলেছেন, “জমিদারী উঠে গেলে গাঁয়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে। [প্রমথ চোধুরী–রায়তের কথা]
গোরা ২৬ পরিচ্ছেদ
যোগাযোগ—
এ দিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি— রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।
৪১ মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায় নি। নিজের ’পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগীদের তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা করে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওয়ালা একটা পত্তনি তালুক ওদের নীলের কারবারের শামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হয়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক; দলিল স্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেস্টারি করে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো
ডঃ আহম্মদ শরীফ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন--‘ সাড়ে সাতশ বছরের পুরনো দেশজ কিম্বা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোনো ব্যক্তিগত কৃতি কিম্বা গুণ-মান-মাহাত্ম্য তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমনকি আকবর বাদশাহ কিম্বা মঈনউদ্দীন চিশতি, রাজিয়া–আনারকলি–নূরজাহানও নন। ছয়শ বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা ও বিত্তবান জ্ঞান-কৃতি-কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর (তাজমহলই ব্যতিক্রম) আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি। এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল।’
আহম্মদ শরীফের এই অভিযোগকে আশ্রয়কে করে আরও দুএকজন একটু কঠোর ভাবেই বলেন, আগেই বলা হয়েছে বক্তব্যের দিক থেকে তিনি ঠিকই বলেছেন, আহমদ শরীফের বক্তব্যও তাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কলমের নিবে একাধিকবারই মুহম্মদ-এর নাম লিখিত হয়েছে, আকারে ইঙ্গিতেও হয়েছে। (সাদ কামালী)



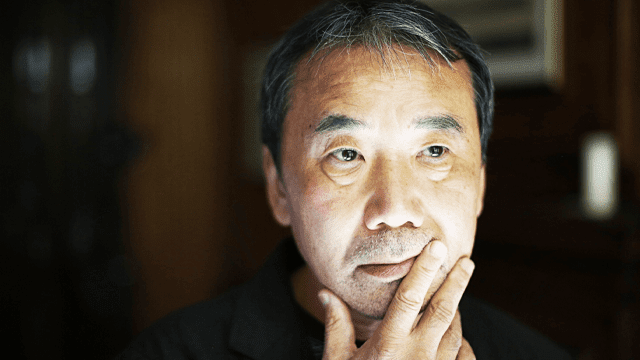







1 Comments
আপনার লেখা আগে পড়ি নি। সেটা আপসোষ। এখন কি লিখছেন? আমার ইমেইল bhdebashish@gmail.com আপনার মেইল আই ডি পেলে যোগাযোগ রাখা যাবে।
ReplyDelete