
লেখাটা হল একটা লড়াই। বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির লড়াই। এই স্মৃতি আমার পূর্ব পুরুষের। আমার নিজের স্মৃতি। এই স্মৃতির মধ্যে থেকেই আমার পরের মানুষগুলো জন্ম নিচ্ছে। এগুলো আমার পূর্বপুরুষরা লিখেছেন। এখন আমি লিখছি। এর পরে উত্তর পুরুষ লিখবে’… কথা হচ্ছিল কুলদা রায়ের সঙ্গে। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে, ১৯৬৫ সালে।
পড়াশোনা করেছেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে। ধানের আমিষ বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করছেন। মূলত গল্পকার। আরও লেখেন কথাসাহিত্য বিষয়ে গদ্য। তাঁর লেখায় স্মৃতির সঙ্গে উঠে আসে দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর সঙ্গে কথা হল নতুন বই, লেখালেখি, গল্প, গল্পের কলকব্জা, গল্পের মানুষ, সাহিত্যের সংকট, স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা নিয়ে, ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ার থেকে আমেরিকার নিউইয়র্কে।
--এমদাদ রহমান
এমদাদ রহমান :
আমরা জেনেছি, এবার আপনার দুটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। একটি গল্পের, আরেকটি বই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কারা প্রকাশ করছেন?
কুলদা রায় :
গল্পের বইটির নাম– বৃষ্টি চিহ্নিত জল। মোট ১৫টি গল্প থাকছে এই বইটিতে। বইটি কোলকাতা ও ঢাকা থেকে বের হবে। ঢাকার প্রকাশক নালন্দা।
আমার আরেকটি বই প্রকাশিত হবে ঢাকা থেকে। নাম রবীন্দ্রনাথের জমিদারগিরি ও অন্যান্য বিতর্ক। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাকিস্তান আমল থেকে নানা বিতর্ক ধারাবাহিকভাবে করা অব্যাহত রয়েছে। যেমন তিনি প্রজানীপিড়ক জমিদার ছিলেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িক ছিলেন। মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন। হিন্দুত্ববাদী শান্তি নিকেতন গড়েছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কোনো লেখাপত্র করেননি। ইত্যাদি। এই বিতর্কগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সাহিত্য বিচার নেই—আছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচার। এটা একধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা চলছে। একটু তথ্য খুঁজে দেখলেই বোঝা যায় এই বিতর্কগুলো অসার—অসত্য। এই বিতর্কগুলোর সত্যাসত্য খুঁজে দেখা হয়েছে এই বইটিতে।
এমদাদ রহমান :
আপনার গল্পের বইয়ের নামটা এমন যে মনে হয় এই নাম দীর্ঘদিন পাঠকের মনের ভিতর গেঁথে থাকবে। বৃষ্টি চিহ্নিত জল। এমন নামকরণের কারণ কী? শুনলে মনে হয়, এটি বুঝি কবিতার বই? বরিশাল কিংবা কবি জীবনানন্দের সঙ্গে কি কোনও যোগসূত্র…
কুলদা রায় :
বইটির নাম বৃষ্টি চিহ্নিত জল। যে কেউ এই নামটি দেখলে মন করবে–এটা কবিতার বই না হয়ে যায় না। ভেতরে একটাও কবিতা নেই। কিন্তু প্রতিটি গল্পের মধ্যে পরী আছে।
আমি জলের দেশের মানুষ। জন্ম হয়েছে গোপালগঞ্জে। এই এলাকাটি বাংলাদেশের বিল হিসেবে পরচিতি। ছয় মাস জলের নিচে থাকে। দিগন্ত জুড়ে আউশ-আমন ধানের ক্ষেত। গ্রামগুলো বর্ষাকালে জলের উপর ভাসে। নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আমার শহরটি একসময় জলের নিচ থেকে ভেসে উঠেছে। ছেলেবেলায় দেখেছি প্রবল বন্যায় জল ঢুকে পড়ে পথে-ঘাটে, অলিতে গলিতে, বাড়ির মধ্যে। আমরা বারান্দায় বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছি। জল নিয়ে একটি আর্কিটাইপাল ব্যাপার আমার মধ্যে আছে।
এই জলের মধ্যেই আবার জলের হাহাকার আছে। কোনো বছর যদি বৃষ্টি আসতে দেরি হয় বা স্বাভাবিক বৃষ্টি না হয় বৈশাখে, জ্যৈষ্ঠে অথবা আষাঢ়ে তাহলে বীজ বোনা যায় না। বীজ বুনতে পারলেও অঙ্কুর শুকিয়ে যায়। গাছ মরে যায় জলের অভাবে। তখন অভাবে পড়ে মানুষ। এই অভাবটি আমাদের সঙ্গে আছে হাজার বছর ধরে। মুর্শিদাবাদে যখন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দোলার পতন ঘটল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করল, তখন তারা খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। সে সময় প্রবল খরায় বাংলার মাঠঘাট পুড়ে গেল। মন্বন্তর দেখা দিল। একভাগ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল। এক ভাগ মানুষ বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সেখানেও তারা বাঘের পেটে মরল। কুমীরের খাদ্য হল। মশার কামড়ে মরল। আর বাকী যারা বেঁচে ছিল তারা খজনা দিতে দিতে শুকিয়ে গেল। তারা জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। মেঘের জন্য অপেক্ষা করত। বৃষ্টির অপেক্ষা করত। বৃষ্টি এলে ফসল হবে। মানুষ খেতে পারবে। প্রাণে বাঁচতে পারবে। হাসতে পারবে। এবং আমি লক্ষ্য করি আমাদের ভারতীয় প্রাচীন পুরান-পুস্তকে যে শ্লোক রচিত আছে সেখানে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আছে। জলের জন্য প্রার্থনা আছে। প্রবাদে আছে—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।
আমি নমোশুদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ, আমার পূর্ব পুরুষ হাইলা-জাইলা—এখনো তো তাই, এই নমোশুদ্র সম্প্রদায়ের অঙ্গে অঙ্গে অভাবের চিহ্ন। আমরা ভাতের অভাবে খেয়েছি ঢ্যাপের খই, ফ্যান ত্যালানী, নোঠানী। এগুলো খেয়েই আমরা স্বাস্থ্যহীন—শক্তিহীন। এই বৃষ্টি আমাদের জল। জল পড়ে—পাতা নড়ে। শব্দ শোনা যায়—টুপ টাপ। বুঝতে পারি আমাদের শুকিয়ে যাওয়া প্রাণ আবার জল ফিরে পাচ্ছে।
এই রকম অভাব, খরা আর শুকনো মানুষের গল্প লিখেছিলাম গেল বছর। গল্পটি আমার দুই জমজ মাসির। দুজনেই পরীর মত দেখতে। আমার আজা মশাইয়ের ইচ্ছে তিনি এক ঘরের দুই ভায়ের সঙ্গে তার জমজ মেয়েদের বিয়ে দেবেন। কিন্তু তার সঙ্গতি নেই। একজনের বিয়ে হয়। আরেকজনের বিয়ে হয় না। দুজনে ঠিক করেন তারা আত্মহত্যা করবেন। এই আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তারা বুড়ো হয়ে যান। মানুষের অভাব বুড়ো হয় না। মানুষ বৃষ্টি চিহ্নিত জলের জন্য অপেক্ষা করেন। এই অ-বিয়েতো মাসি মানুষের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসবেন। জল নিয়ে আসবেন। এই জলের কথাটি লিখতে লিখতেই আমার মনে হল বৃষ্টি চিহ্নিত জল ছাড়া এই জলের গল্পটি হতে পারে না। এভাবে নামটি এসে গেল। কবিতা যেমন করে আসে ঠিক সেইভাবে।
আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর বাড়ির পাশের বাড়িটিতে আমি দীর্ঘকাল ভাড়া থেকে থেকেছি। তিনি জলকে জানতেন। আমি জলের স্বভাব জানি। বৃষ্টির ভঙ্গিমা বুঝতে পারি।
এমদাদ রহমান :
‘বৃষ্টি চিহ্নিত জল’ তো কোলকাতাতেও বের হচ্ছে।
কুলদা রায় :
কোলকাতার প্রকাশক সোপান প্রকাশনী। প্রখ্যাত গল্পকার-ঔপন্যাসিক অমর মিত্র গল্পগুলোকে বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে করেছিলেন। তিনিই কোলকাতার সোপান প্রকাশনী থেকে বইটি বের করছেন। খুঁটে খুঁটে বানানাদি সংশোধন করেছেন। প্রচ্ছদ করিয়েছেন। যেন বইটি আমার লেখা নয়—অমর মিত্রের নিজের বই। নিজের প্রথম বই।
এমদাদ রহমান :
পাঠককে আপনার গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলুন।
কুলদা রায় :
যখন লিখতে শুরু করি তখন ঠিক করে নিয়েছিলাম গল্পগুলো হবে পরীর গল্প। একটা ফাইলও খুলে ছিলামপরী সিরিজ নামে। সবগুলোর মধ্যেই পরীর ব্যাপারটি আছে। আমাদের বাড়ির পাশে শ্যামলদাবাঁশি বাজাতেন খুব সুন্দর করে। তিনি বাঁশি বাজালেই পরী নেমে আসত আকাশ থেকে। সেটাএকটা মায়ার জগৎ। তিনি আমাকে বহুদিন শ্মশান ক্ষেত্রে নিয়ে গেছেন। সেখানে বাঁশি বাজিয়েছেন। শিশিরে আমাদের গা ভিজে গেছে। গন্ধ গোকুল দূর থেকে ঘুরে গেছে। মানিকহারেরশেষ স্টিমার মিলিয়ে গেছে। তার মধ্যেই শাদা ডানা মেলে পরী এসেছে। সেই পরীটি যখন দেখেছি তখন মনে পড়েছে এই পরীতে আমাকে শিশুকালে মায়ের কোলের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের পণ্ডিত স্যার সেকারণে আমার নাম দিয়েছিলেন পরীমানব।
আমাদের পাশের বাড়ির মাহমুদাদের ঘরে পরী আসত। আমি যখন নিউ ইয়র্কে চলে আসি তখন আমার বাসার পাশেই একটা পার্ক দেখতে পাই। গোলাকার পার্কটি। তার মাঝখানে ডানা মেলা এইটি পরী দাঁড়িয়ে আছে। এই পরীটিই আমার শিশুকালের পরী। আমি নিউ ইয়র্কে আসছি জেনে আমার আগেই এসে পড়েছে। আমার ছোটো মেয়ে বলত—রাত্রিকালে পরীটি উড়ে যায়। পার্কে থাকে না। ভোরবেলায় ফিরে আসে।
পরী সিরিজের প্রথম গল্পটি ছিল আমার কৈশোরের একটি ঘটনা। আমার বন্ধু আলমগীর ছবি আঁকতো। সে যা আঁকতো তা কোনো না কোনো ভাবে সত্যি হয়ে যেতো। এই আলমগীর, আমাদের ক্লাশমেট এ্যানি, স্কুলের টিচার হুজুর স্যার, তার অদেখা স্ত্রী টগর, কলেজের তরুণ প্রভাষক আনিস স্যার, তার স্ত্রী গুলবদন বানু, আর তাদের মেয়ে শবনম অথবা হিমিকাকে নিয়ে গল্প। এই গল্পটি শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের আগে—দেশবিভাগের কালে। মাঝখানে পাকিস্তান হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। বহুমানুষ ভিটে-মাটি ছেড়ে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে। গল্পে দুটি সময়কাল আছে। দেশভাগের আগে-পরে। এ সময়ে ছিলেন সুনামগঞ্জের দিরাই শালনা এলাকার সালামোতুল্লাহ ওরফে হুজুর স্যার আর ১৯৭১ পরে বাংলার শিক্ষক আনিস স্যার। এ দুজনের আখ্যানের মধ্যে একটি পরীর গল্প। পরীর গল্প বলেই টাইমলাইনকে ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়াস আছে।
এই রকম করে আমি ইতিহাসের সূত্র ধরে ১৫টি গল্প লিখেছি। নির্মাণ করেছি ইতিহাসের বিকল্পপাঠ।
শেষ গল্পটি জ্যোতিদিদিকে নিয়ে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে। তিনি বহুদিন পরে দেশে ফিরে গেছেন। তিনি যখন প্লেনের দিকে চলে যান তখন বুঝতে পারি তিনি আসলে জ্যোতিদিদি নন—পরী। কোহেকাফে বাড়ি। এই কোহেকাফের পরীদিদিকে নিয়ে লিখেছি।
এমদাদ রহমান :
গল্পগুলো লেখার গল্প বলুন।
কুলদা রায় :
শবনম অথবা হিমিকালিপি গল্পটি লিখেছিলাম একটা নোটবুকে। লেখার আগে করেছিলাম ছোট একটি প্লটের ড্রাফট। তারপর চরিত্রগুলো লিখেছিলাম পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায়। সেই চরিত্রগুলো এই গল্পটিতে কি কি করেছিল বা করবে সেটা বিস্তারিতভাবে লিখে নিয়েছিলাম। পরে সাজিয়ে নিয়েছিলাম আখ্যানের সিকোয়েন্স বা পর্বগুলো। ঠিক সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখার মতো করে।
তারপর এই গল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলি লিখেছিলাম। কিভাবে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলিকে একটা ক্লাইমেক্সে পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্য টেনশনগুলিও ড্রাফট করেছিলাম।
গল্পের এই ক্রাফট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে সে সময়ে আমার অগ্রজ আনোয়ার শাহাদাতের সঙ্গে দিনের পর দিন নিউ ইয়র্কের স্টার বাকস রেস্তোরা, বার্নস এন্ড নোবলস বুক স্টোর, পার্ক, বে সাইড এবং ম্যানহাটনের সবচেয়ে পুরনো মদের দোকানে আড্ডা দিয়েছি। সামনে গ্লাশ থেকে উপচে পড়েছে টাকিলা অথবা কোনিয়াকের বুদবুদ। কখনো বৃষ্টির মধ্যে। কখনো বরফের মধ্যে। কখনো গরমের মধ্যে। কিন্তু লিখেছি বাংলাদেশের গল্প। আমার নিজের মানুষের গল্প। নমশুদ্রদের গল্প।
গল্পটি যেহেতু ইতিহাসকে অনুসরণ করে লিখছি ফলে এই জন্য দেশভাগের আগের মানুষের জীবনযাত্রা—পথঘাটের হিসেব, খরচ পাতি, নীলকর সাহেবদের কিছু আত্মচরিত এইসব বিষয়ে পড়ে নিতে হয়েছিল।
গল্পে একটি গান রয়েছে। ছেলেবেলা থেকে শোনা থাকলেও লেখার প্রস্তুতিকালে বারবার গানটি শুনেছি। গানে বৈঁচি ফলের কথা আছে, যে ফল গাছটি আমার এলাকায় খুব বেশি হয়না, কিন্তু আছে একটি শ্মশান ক্ষেত্রে—এই বৈঁচি ফল গাছটির শারীরবিদ্যা বা মরফোলজি জেনে নিতে হয়েছে। বারবার গানের কথা, তার সুর, গায়কীতে বারবার চোখ রেখেছি—মন রেখেছি। এভাবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করি গানটি আমি পূর্ণরূপেই গাইতে পারি। এক মাস ধরে গল্পটি লিখেছি। এই একমাস ধরেই আমি গানটি গেয়েছি। এভাবেই গল্পটি যেন এই গানটির মতোই সুরেলা হয়ে ওঠে সে চেষ্টাই অবচেতনে করেছি।
গল্পটি শুধু ইতিহাসের নয়। গল্পটি কিংবদন্তির। গল্পটি পরীদের। গল্পটি জলের নিচে থেকে ভেসে ওঠা আমার ছোটো মফস্বল শহরের। আর তার ক্রমশ ধূসর হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর। স্বপ্নের। দুঃস্বপ্নের। গল্পটি আমার নিজের। আমার নিজের গল্প বলেই এই গল্পটি সত্যি। সত্যি কখনো গল্প হয় না। সত্যিকে যখন ম্যাজিকের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয় তখন তা গল্প হয়ে ওঠে। আমি ঠিক এই কাজটিই করার চেষ্টা করেছি শবনম অথবা হিমিকালিপি নামের এই গল্পটিতে। এটা একটি যাদু-বাস্তব গল্প। আমার এ বইয়ের সব-গল্পই তাই।
এই গল্পটির পরপরই আমি আরেকটি গল্প লিখি। নাম সুবোলসখার বিয়ে বৃত্তান্ত। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে রূপোহাটি নামের একটি গ্রামে সুবোল কাকার বিয়েতে গিয়েছিলাম। সেই বিয়েতে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সেটাই লিখেছিলাম। গল্পটি মহা দূর্ভিক্ষের। কিন্তু দূর্ভিক্ষের কথা বলছি না। বলছি একটা রগড়ের কথা। রূপভান আর রহিম বাদশার কথা। বলছি জলের ভেতরে ছড়য়ে পড়া এক মাথা চুলের কথা। জলপরীর কথা। আলো ও অন্ধকারের কথা।
এবং এই গল্পটিরও প্রয়োজনীয় ছক করে নিয়েছিলাম। ফলে এই দুটো বড় গল্প লিখতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। কখনো বাসে, কখনো ট্রেনে বা পার্কে বসেও লিখেছি। এমন কি আমার কর্মস্থলেও ফাঁকে ফাঁকে লিখেছি।
প্রতিটি গল্পই ইতিহাসের নানা সময়কে কেন্দ্র করে। কোনোটাতে বৃটিশ আমলের সুসমাচার প্রচারকারী খ্রিস্টান মিশনারীদের কেন্দ্র করে এসেছে আমার ঠাকুরদার কৃষ্ণপালা আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সফরসঙ্গী প্রখ্যাত বাইজী মতিবিবি, তার মেয়ে গন্নিবিবির আখ্যান, কোনোটি ১৯৬৫ সালে শত্রু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কালে ভূমিচ্যুত মানুষের দীর্ঘশ্বাসের আখ্যান। কোনোটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কালপর্ব, এসেছে ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ, ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পীড়িত মানুষ। এর মধ্যে দিয়েই আমার শৈশবের পরীমানবগুলো নানাভাবে উড়ে আসে। কখনো তাদের ডানা থাকে। কখনো তাদের ডানা কেটে ফেলে গওহরডাঙার সদরুদ্দিন পীর সাহেব। কখনো আমেনা বুবুর ভাই বাছেদ ভুল করে সিন্দুক থেকে ডানা দুটো নিতে ভুলে যায়। ডানা ছাড়াই উড়াল দিতে চাই। ডানা ছাড়া ওড়া যায় না। তবু ওড়ার বাসনাটি ভেসে আসে। বাছেদের বদলে তার ছায়াটিকে নিয়ে যায়। আমি এই সব ছায়া মানুষের মধ্যে জীবনের একটা দীর্ঘ সময়ে থেকেছি বলে ছায়ার গল্পটিই লিখতে বসেছি।
এমদাদ রহমান :
আপনার গল্পের অনুষঙ্গে দেশভাগ ব্যাপারটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের আরও অনেক লেখকের গল্পেও দেশভাগ গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে। এ সম্পর্কে বলুন।
কুলদা রায় :
দেশভাগ আমাদের প্রাণকে ভাগ করেছে। আমাদেরকে ভূমি থেকে উন্মূল করেছে। ঘৃণা আর হাহাকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সমষ্টিগত বিষাদকে মনে গেঁথে দিয়েছে। ট্রমাগ্রস্থ করেছে।
উনিশ শতকের আগে দেশভাগের ব্যাপারটি মানুষের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের মধ্যেও ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত–সাম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব ছিল—সংঘাতও ছিল। সেটা সব দেশেই আছে। তার চেয়েও বেশি ছিল মানুষের মানুষে মিলন—সম্প্রীতি। বহুর মধ্যে ঐক্যবোধ। এভাবেই আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র আমাদের ছিল না।
বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শাসক ইংরেজরাই বুঝতে পেরেছিল তাদের এই ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। বিদেশী শাসনের নিগড়ে তারা থাকবে না। এটা ইতিহাস নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা তাদের ক্ষমতায় থাকার জন্যই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তোলে। তাকে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-ফ্যাসাদের মধ্যে ঠেলে দেয়। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ছিল না। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যখন হল তখন মানুষ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তাদের কাঁধের উপরে অস্ত্রের আঘাত এসে পড়ছে। কোলকাতায় দাঙ্গা বেঁধেছে। নোয়াখালিতে মানুষকে মারা হচ্ছে। আতঙ্কে মানুষকে পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যারা ১৯৪৭ সালে যেতে পারেননি, তারা ১৯৫০ সালে গেছেন। ১৯৫৪ সালে, ১৯৬৪ সালে, ১৯৭১ সালে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। এখনো করতে হচ্ছে নীরবে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসে লিখেছেন, যেদিন দেশভাগ হল, সেদিন তার বাবা, কাকা সারারাত পিতৃপুরুষের শ্মশানক্ষেত্রে শুয়ে থাকলেন। এই মাটিকে আকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন। পারলেন না। পরদিন। ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে হল।
হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখি উপন্যাসে সবাই যখন পশ্চিম বঙ্গ ছেড়ে পূর্ব বঙ্গে চলে আসছেন, গরুর গাড়িতে মাল-সামান রাখা হয়েছে, চাকা ঘুরতে শুরু করেছে—ঠিক তখনি পরিবারের গিন্নি গাড়িতে উঠলেন না। নিজে গিয়ে আকড়ে ধরলেন তার প্রথম সন্তানের কবরের মাটিকে। তিনি দেশ ছাড়বেন না। এই দেশ ছাড়ার বেদনাটি এখনো হাসানে বহমান। তিনি যখন লেখেন তখন দেশভাগের বেদনাটি টের পাওয়া যায়। এই বেদনাটি আরো বহুকাল আমাদেরকে টের পেতে হবে। দেশছাড়া হতে হবে।
১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয়েছিল—সে দেশভাগের কারণটি যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সেটা কিন্তু দেশভাগের কারণে থামেনি। সেটা বেড়েছে। এখনো প্রবলভাবেই টের পাওয়া যায়। এটা অসভ্যতা। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এটা নিশ্চিহ্ন করার জন্যই দেশভাগের বেদনাকে নিয়ে না লেখায় উপায় নেই।
এমদাদ রহমান :
গল্পগুলো কখন লিখেছেন?
কুলদা রায় :
গল্পগুলো গেল দুছর ধরে লিখেছি। এর আগে আমি মেমোয়ার ধর্মী ছোটো ছোটো লেখা করতাম। এই গল্প লেখার বয়সও বলা দু বছর। এর আগে আমি শব্দ নিয়ে কাজ করতাম। শব্দকে নানা ভঙ্গিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতাম। শব্দ দিয়ে ছবি আকঁতে চেষ্টা করতাম। ছবির মধ্যে প্রাণ দেওয়ার নানা চেষ্টা তব্দির করতাম।
এই শব্দ-ছবি আর প্রাণকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে করে।
এর মধ্যে আমার পুরণো দিনের অসুখটি আমাকে একদিন তুষার ঝড়ের মধ্যে জেগে ওঠে। আমি ঘুমোতে ভুলে যাই। হাঁটতে ভুলে যাই। বাঁচতে ভুলে যাই। এই অসুখটি নিদান হিসেবে আমার ডাক্তার আমাকে লিখতে বলেন। আমি লিখতে জানি না। ফ্যাল ফ্যাল করে বসে থাকি। তা দেখে আমার দুটো মেয়ে আমার পাশে কাগজ কলম নিয়ে বসেতো। ওরাও লিখতে লিখতে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।। বলে, বাবা লেখো। তারপর আমার মেয়েদের সঙ্গে আমি লিখতে শুরু করি। সেগুলোকে আমি নাম দেই—ছাতামাতা লেখা। এ সময় আমার পুরনো দিনের ছবির কথা মনে পড়ে যায়।
একটি সময়ে অমর মিত্রের সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি গল্পকার-ঔপন্যাসিক। আলাপটি ঘটে ইন্টারনেটে। তিনি গল্প লিখতে বলেন। আমি কখনো গল্প লিখিনি। গল্প কী করে লেখা হয় জানিই না। কিন্তু অমর মিত্রের বলাটা ছিল এতো মাধুর্য্যপূর্ণ যে তাকে হেলা করা কঠিন।
ফলে আমি নতুন করে আমার মুছে যাওয়া ছবির মানুষগুলোকে দেখতে শুরু করি। স্মৃতির মধ্যে ঢুকে পড়ি।
এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করি—এই স্মৃতির গুলো আসলে আমি নিজেই। আমার বাবা-মা ভাই বোনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে একাত্তরে দেশত্যাগ করছি। আমার আজামশাই ট্রেনে যেতে যেতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলছেন। তাঁর পাশ থেকে উঁকি ঝুকি মেরে আকাশ দেখার চেষ্টা করছে আমার জমজ দুমাসি—অঞ্জলি আর বিজুলি। রাস্তার পাশে কাঠপাতার ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেছি খয়রামারি কলেজের সামনে একটু গুঁড়ো দুধ অথবা দুটো পাওরুটি আনতে। অথবা চুয়াত্তরে দীঘারকূলের বিলের মধ্যে দিয়ে চলেছি বাচাড়ি নৌকায় রূপাহাটি গ্রামে। সেখানে বহুদিন পরে খাওয়া যাবে লক্ষ্মীদীঘা ধানের ভাত। এরপরে আলমগীরের সঙ্গে বৈঁচি ফল খুঁজতে যাবো নীলারমাঠে।
অমর মিত্র যেন জানেন—এইসব মানুষগুলো আসলে ছবির মানুষ নয়—সত্যি মানুষ। সত্যি মানুষের কারো কারো ডানা থাকে। পরী হয়ে উড়তে পারে। ডানা না থাকলে মানুষ হয় না। উড়তে উড়তে ডানা ভেঙ্গেও যায়। এই ডানার গল্পটিই আমার গল্প। অমর মিত্র বলেন—আর আমি লিখি। আমি লিখি অনেক দূরে বসে। তখন নিউ ইয়র্কে রাত্রি নামে। বৃষ্টি পড়ে। পাতা নড়ে। বরফ পড়ে। ঝড়ের শব্দ শোনা যায়।
নিউ ইয়র্কের বার্নস এন্ড নোবলসের বুক স্টোরে, স্টারস বাকস কফি শপে, ডানকিন ডোনাটে অথবা ফ্রেশমিডো পার্কের ঘাসের মধ্যে বসে বসে অগ্রজ গল্পকার-ঔপন্যাসিক আনোয়ার শাহাদাত দিনের পর দিন গল্পগুলো নেড়ে চেড়ে দেখেন। তিনি গল্পের ভেতর-বাইরেটা শার্লক হোমসের মতো আলো ফেলে খুটে খুটে দেখেন। যেন এই গল্পগুলো আমার নয়, তাঁর নিজেরই গল্প। তিনিই লিখছেন। লিখতে লিখতে বার বার সতর্ক করে বলেছেন, না, পরীর গল্প নয়—ডানাহীন মানুষের গল্প লেখেন। পরীদের গল্প কোনো গল্প হয় না। আর আমি মানুষের ছবির বদলে পরীর গল্পই লিখি।
এমদাদ রহমান :
কমলকুমার মজুমদার বলেছেন গল্পে একটি কাহিনী থাকে, ঘটনা থাকে, কিন্তু সেটাই গল্প নয়। আপনার কাছে এই কথাটি ব্যাখ্যা কী?
কুলদা রায় :
গল্প আসলে গল্পই। জীবনের আনন্দের গল্প। বেদনার গল্প। বেঁচে যাওয়ার গল্প। মরে যাওয়ার গল্প। জন্মান্তরের গল্প। একই আখ্যানের চক্রের মত পুনর্বিভাব মাত্র। ঘটনার পুনর্বয়ান মাত্র।
তাহলে একজন লেখকের পুরনো বিষয় নিয়ে লেখার কী দরকার? দরকার হল– নতুন করে পুরনোকে দেখা। ভিউ পয়েন্টটা পালটে দেখা। গল্পের আগে/পরে যে গল্পটি কখনোই বলা হয়নি—কিন্তু তার মধ্যেই গল্পের রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই রহস্যভেদ ছাড়া আমাদের রাত্রি শেষ হয় না, নিদ্রা আসে না, আহার রোচে না, শ্বাস নিতে পারি না—সেই গল্পের শুলুক সন্ধানের জন্যই কাহিনীর মধ্যে থেকে আরেকটি কাহিনীকে বের করে দেখানো যাতে করে আরেকটি গুপ্ত গল্প তৈরি হয়ে যায়। সেটা ধরে আরেকটি গল্প লিখবেন অন্য কেউ। গল্প থেকে বহু গল্পের নির্মাণের চক্রান্ত থেকেই গল্প লেখা মাত্র।
এমদাদ রহমান :
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলা ছোটগল্প মরে যাচ্ছে। তিনি গল্পে জীবনের সঙ্কটকে দেখেছিলেন। গল্পগুলোকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখেছিলেন। আপনার কি ধারণা?
কুলদা রায় :
জীবন অমৃত। সেটা মরে না। যখন সেই অমৃতের জীবনকে লেখা হয় তখন তা ব্যর্থ হয় না। তাহলে অমৃতকে জানতে হয়। জীবনকে বুঝতে হয়। এই দুইয়ের মর্মকে বেঁধে ফেলার কায়দাকে আত্মস্থ করতে হয়। এটার জন্য লেখককে নিজের ভেতরে ডুব দিতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতার কাছেই হাত পাততে হবে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কুবেবের বিষয়-আশয় উপন্যাসটিতে যে গল্প বলেছেন সেটা তাঁর নিজের গল্প। কুবেরের জীবনটা তিনি এককালে যাপন করেছেন।
আমি বহুদিন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসের সোনা আসলে তিনি। অলৌকিক জাহাজের ছোটোবাবু তিনি।
হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখির কথক আসলে হাসানের বাল্যকাল। জীবনের যে যে সঙ্কট দেখেছেন সেটা তার নিজেরই সঙ্কট। একে লিখলে সঙ্কটগুলো তার অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংশ প্রাণ সমেত উঠে আসে। এটাই তো একজন সেরা লেখকের কাজ।
বানিয়ে গল্প লেখা যায় না। এখন লেখকদের মধ্যে বানিয়ে গল্প লেখার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে তাদের গল্পের চরিত্রগুলোর প্রাণ নেই। তারা মৃত মানুষ। মৃত লেখা। তবে এর মধ্যেও আনোয়ার শাহাদাত, শিমুল মাহমুদ, মোজাফফর হোসেন লিখছেন। লিখছেন মেহেদীউল্লাহ। এদের লেখার মধ্যে জীবিত মানুষের গল্প আছে। নিজের গল্প। নিজের গল্প বলেই সে গল্পগুলো ব্যর্থ হতে পারে না।
এমদাদ রহমান :
ফর্ম এবং কাঠামো– গল্প লিখতে গিয়ে কোনটিকে গুরুত্ব দেন?
কুলদা রায় :
গল্পের ক্রাফটের কোনোটিকে অগুরুত্ব দিলে গল্প হেলে পড়ে। হেলে পড়া গল্প দিয়ে আমরা কী করবো!
আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে গল্প লিখি না। ফলে গল্পের আখ্যানবস্তুটি আমার ভেতরেই আছে। বাইরে যাওয়া লাগে না। কিন্তু গল্পের মর্মের জন্য গল্পটির ফর্ম ও কাঠামো নিয়ে ভাবতে থাকি লেখার আগেই। আগে কাঠামোটি করে ফেলি। তারপর ফর্মটি ঠিক করি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তৃপ্ত না হই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেই কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম অনুসারের গল্পের রক্ত, মাংশ, মজ্জা, প্রাণ, লাবণ্য যোগ করতে থাকি। ফলে একটি গল্প আমি সুতার মিস্ত্রীর (carpenter) মতো করে বহুদিন ধরে লিখি। হয়তো সে গল্পটি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লিখে যাবো।
এমদাদ রহমান :
এখানে আপনার গল্পও লেখার রসায়ন অর্থাৎ গল্প কি আগে থেকে ভেবে নিয়ে লেখেন, নাকি লিখতে শুরু করে শেষের দিকে এগিয়ে যান?
কুলদা রায় :
সাধারণত আমি দুধরনের গল্প লিখি। এক। মেমোয়ার ধরনের ছোটো লেখা। সেগুলো লিখে ফেলি এক বসাতেই। লিখতে লিখতেই ভাবনাগুলো এসে পড়ে। আলাদা করে ভাবার দরকার হয় না। এগুলোকে ঠিক গল্প বলিনা। এ ধরনের লেখা নিয়ে আমার একটা বই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছর আগে। নাম কাঠপাতার ঘর।
আর যে লেখাগুলোকে গল্প হিসেবে লিখি সেগুলো আগে ভেবে নিয়ে-কাঠামো করে নিয়ে—লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক করে নিয়ে লিখি। এসব প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হলে আমার অটোমেটিক রাইটিংটা এসে যায়।
এমদাদ রহমান :
প্রতিটি লেখাই তো লেখকের জীবনের খণ্ড। তো, আমাকে বলুন, আপনার লেখালেখিতে ব্যক্তিজীবন কীভাবে এসেছে, কতটা এসেছে?
কুলদা রায় :
আমি সব সময়ে আমার নিজেকেই লিখি। ফলে লেখার মধ্যে আমার ব্যক্তি-জীবনটা প্রবলভাবেই আসে। তবে এই ব্যক্তি-জীবনটাকে একটা উত্তরাধীকার হিসেবে দেখি।
আমাদের বাড়িতে একটি পুরনো ছবি ছিল। সাদা কালো। সাদা বর্ডারের চারপাশে লতাপাতার নকশা আঁকা। তার উপরে কাঁচ। আর কাঠের কালো ফ্রেমে বাঁধানো।
ছবিটির মাঝখানে একজন বুড়ো লোক মুখ উঁচু করে বসে আছেন। চোখে গোল চশমা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বাঁহাতে একটি লাঠি শক্ত করে ধরা। লোকটির সামনে তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ। মুখে চন্দন লেপা। আর গলায় ফুলের মালা পরানো। কপালে সিদুঁরের টিপ। শ্মশান-যাত্রার আগে ছবিটি তোলা হয়েছিল। অনুমান করি সেটা ১৯৩৬ সাল বা ৩৭ সালের দিকে তোলা।
এ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধী প্রদান করা হচ্ছে। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিতার বিয়ে হচ্ছে। ভারত বিনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। আন্দালুসিয়ার কবি ফেদোরিকা গার্সিয়া লোরকা মারা যাচ্ছেন। জার্মানিতে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় করছে।
এই বুড়ো লোকটির নাম সৃষ্টিধর রায়। তার স্ত্রীর নাম জানি না। তাঁর কাছে বসে আছেন তিন ছেলে। সঙ্গে তাঁদের সাত বউ। বড় ছেলের নাম বিরাজমোহন রায়। পেশায় কৃষক। দুই স্ত্রী। একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি দণ্ডকারণ্যে হারিয়ে গেছে। মেজো ছেলের নাম সতীশচন্দ্র রায়। তাঁর তিন স্ত্রী। দুটি মেয়ে।
ছোটো ছেলের নাম বিধুভূষণ রায়। কৃষ্ণপালায় গান করেন। তাঁর দুই বউ। দুটি মেয়ে। একটি ছেলে। বড় মেয়ের নাম খেপি। হাত জোড় করে আছেন। চোখ বন্ধ। ছোট মেয়েটির নাম পচি। হাতে চুরি। আর ছেলেটি দেখতে ঠিক আমার ছেলেবেলার ছবির মতো। চুলে বাঁদিকে সিঁথি করা। ইনি আমার বাবা—বিনয়শঙ্কর রায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামের শুরু থেকে বিনয় ঝরে গেছে। শুদ্র মানুষের বিনয় থাকার দরকার নেই।
এই তিন ভাইয়ের পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলের মধ্যে এখন বেঁচে আছেন একটি মেয়ে। তার নাম চুনু। নিবাস—মিরুখালি।
ছবিতে আরো কিছু লোকজন আছেন। এরা কেউ এ বাড়ির—কেউ ও বাড়ির। নানা বয়েসী পুরষ ও মহিলা। এটাই হয়তো এ এলাকার প্রথম দিকের তোলা ছবি। ফলে মৃতের বাড়িতেও এরা সবাই সেজেগুঁজেই এসেছেন। কয়েকজনের গলার দুপাশ থেকে গামছা নেমে গেছে। বউ-ঝিরা কপালের ওপর ঘোমটা টেনে দিয়েছেন।
এই ছবিটি বিরাজ মোহনের ছোটো বউয়ের জিম্মায় ছিল। তাঁকে যখন বাড়ি থেকে অপরাহ্নকালে বের করে দেওয়া হয়েছিল তিনি তখন কী মনে করে ছবিটি রেখে দেশত্যাগ করেন। তিনি আমার বড় ঠাকুর্মা– বড়রদি ছিলেন। রাতে তাঁর কাছেই ঘুমাতাম ছেলেবেলায়। তিনি ছবির মানুষগুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের গল্পগুলো বলে যেতেন। এভাবে এইসব মানুষ আমার ভেতর জীবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতেন।
ছবিটি এখন ঢাকায়। জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছবির মানুষগুলো কখনো ঢাকায়ই যায়নি। ছবিটি নিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি বহুবার ছবিটি চেয়েছি। শেষদিকে অনুরোধ করেছি মূল ছবিটির বদলে স্ক্যান করা ছবি দিলেও চলবে।
আমি ছবিটি পাইনি। ছবির ভেতরের মানুষগুলো তাই ধীর ধীরে মুছে যাচ্ছে। আর আমি বহুদূরে বসে হাহাকার করছি। তীব্র শীতের মধ্যে আমার অক্ষর দিয়ে তাদের মুছে যাওয়া রেখাগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।
ছবির এই লোকগুলোও আমার নিজের অংশ হয়ে উঠেছে। আমার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীরারাও আমার ব্যক্তিজীবনের অংশ। ফলে এই সব মিলেই আমি লিখি। কিন্তু যখন লিখি গল্প হিসেবে তখন আমি গল্প থেকে বের বের হয়ে আসি। নিজেকে দর্শক হিসেবে রাখি মাত্র–রাখি একটু দূরে। কোনোভাবেই গল্পের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাই না। কোনো মতামত দিতে চাই না। নিটোল গল্পই বলতে চাই। আমি শুধু ঘটনার বিবরণদানকারী হতে চাই মাত্র। অথচ লেখার সময় প্রতিটি চরিত্রকেই আমি চিনি। তাদের অংশ হয়ে উঠি। তাদের হয়েই লিখি। প্রতিটি চরিত্রে আমাকেই অভিনয় করতে হয়। ফলে কোনো চরিত্রের প্রতিই আমার পক্ষপাত থাকে না।
অথচ লেখার সময়ে প্রতিটি চরিত্রের অংশ হয়ে উঠি। চরিত্রটি যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—সেটা যেন আমার নিজেরই দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু আবার আমার নয়। আরেকটি ভীন্ন মানুষের দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠতে দেই। চরিত্রটির চোখে পড়ে—সেটা আমার নিজেরই পলক। অথচ লেখার কালে আমি সযতনে আমার এই চোখটি আমার চোখ থেকে বিযুক্ত করে ফেলি। লিখতে লিখতে এইভাবে সকল চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার সকলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ি। এটা একটা খেলার মত। কারো প্রতিই আমার কোনো মোহ থাকে না। ঈশ্বর পক্ষপাতহীন—নির্মোহ।
এমদাদ রহমান :
গল্প দিয়ে কি কোনও বিশেষ বক্তব্য বা মেসেজ দিতে চান পাঠককে?
কুলদা রায় :
আমি মেসেঞ্জার হতে আগ্রহ বোধ করি না। কোনো ধর্মবোধ আমার নেই। ফলে মেসেজ দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই। নিজের জন্য লিখি। ফলে পত্র-পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশ করা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। বই হল কি হল না সেটা নিয়েও আলাদা ভাবনা রাখি না। । কে কি এই লেখা থেকে পেলেন কি পেলেন না—কি শিখলেন কি শিখলেন না, কি হারালেন কি হারালেন না, এসব নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। আমি শিক্ষক নই। নেতা নই। লেখক– গল্পকার। আমার লিখতে ইচ্ছে করেছে, আমি লিখেছি। এইটুকু।
এমদাদ রহমান :
কখনও একটি গল্প পাঠকের মনে আজীবন গেঁথে থাকে। আমরা হাসান আজিজুল হকের আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পটির কথা এখানে মনে করতে পারি। এমন কেন হয়? মানে, একটি গল্পে এমন কী থাকে, যে মানুষ তাকে ভুলতে পারে না?
কুলদা রায় :
একটি গল্পে গল্পই থাকে। গল্পটি মানুষের বেঁচে থাকার গল্প থাকে। মৃত্যুর গল্প থাকে। আবার অমৃত্যুর গল্পও থাকে। এই অমৃত্যু ব্যাপারট থাকে বলেই গল্পটি মানুষের কাছে অমৃত বোধ হয়। মানুষ গল্পটি নিজের করে নেয়। তারা ভুলতে পারে না।
হাসানের আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পের সেই বুড়োটার উঠোনে একটি করবী গাছ আছে। সেটাতে ফুল ফোটে। সে ফুল সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ এই ফুলটিকে নিয়েই তাঁর বিখ্যাত রক্ত করবী নাটকটি লিখেছেন। নাটকটির নন্দিনীর গলায় থাকে এই করবী ফুলের মালা। আমরা নন্দীনীকেও ভালোবেসে ফেলি। রক্তকরবীকেও ভালোবেসে ফেলা ছাড়া আর কোনো নিয়তি থাকে না। কিন্তু হাসানের বুড়োটা, যার মেয়েটি টাকার বিনিময়ে ঘরের মধ্যে যুবকদের সঙ্গ দিচ্ছে—তার শাড়ির খস খস শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেটা চাপা দিতে গিয়ে বুড়ো বাবা বলছেন করবী গাছটির কথা। নন্দিনীর ফুলটির কথা বলছেন না। ফুলের ধারণাটিকে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চেষ্টা করছেন। ফুলটির লাবণ্যের বদলে বলছেন করবী ফলটির কথা। বলছেন ফলটির মধ্যে মারাত্মক বিষ আছে। এই বিষ খেলে মানুষ মরে যায়। ইচ্ছা মৃত্যু নিতে পারে মানুষ। এই যে সুন্দরের ভেতর থেকে অসুন্দরকে বের করে দেখালেন—আমাদের স্মৃতির মধ্যে বুনে দিলেন, জীবনের অংশ করে দিলেন– এটা তো আমাদের কাছে একেবারে নতুন। একে ভুলে যাই কি করে! ভোলা অসম্ভব।
এমদাদ রহমান :
কেন লিখেন? বা, যদি জানতে চাওয়া হয়, গল্প কেন লেখেন? কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন নিজের লেখালেখির জায়গাটাকে?
কুলদা রায় :
লেখাটা হল একটা লড়াই। বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির লড়াই। এই স্মৃতি আমার পূর্ব পুরুষের। আমার নিজের স্মৃতি। এই স্মৃতির মধ্যে থেকেই আমার পরের মানুষগুলো জন্ম নিচ্ছে। এগুলো আমার পূর্ব পুরুষরা লিখেছেন। এখন আমি লিখছি। এর পরে উত্তর পুরুষ লিখবে।
এমদাদ রহমান :
শুধু আধুনিককালেই নয়, সব সময়ই লেখকজীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থাকে নিঃসঙ্গতা। সলিচিউড। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচিউড! অতীতেও ব্যাপারটা ছিল। এখনও আছে। আগামীর লেখকজীবনেও থাকবে। জানতে চাই, একজন লেখক কি নিঃসঙ্গ?
কুলদা রায় :
প্রতিটি মানুষই একা ও নিঃসঙ্গ। এই মানুষেরই অন্য নাম লেখক। ফলে লেখক মাত্রই একা ও নিঃসঙ্গ।
এমদাদ রহমান :
প্রিয় লেখক নিয়ে বলেন। কেন তাঁকে পড়েন। কী তাঁর ভাল লাগে। কোন ব্যাপারটা আপনাকে টেনেছে? নিজের লেখা গল্পে আপনার সবচে প্রিয় লেখকের প্রভাব কি পড়েছে?
কুলদা রায় :
আমার প্রিয় গল্পকার হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তিনি মহাভারত লিখেছেন। তবে এই ব্যাস বলতে একটি গল্পকার বংশকেই বোঝানো হয়। ফলে একটু সংশয় থেকে যায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সম্পর্কে। মহাভারত অসংখ্য আখ্যানের সমষ্টি। বাস্তব, পরাবাস্তব, যাদুবাস্তব, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শনের অসামান্য ব্যবহার রয়েছে এই মহাগ্রন্থে। রয়েছে মানুষ ও অমানুষের বহুমাত্রিক গল্প। তিনি জীবনকে রূপকথার মধ্যে নিয়ে যান—আবার রূপকথাকে যাদুকরের মত জীবনের অংশ করে তোলেন। এই দিকটিই আমাকে আকর্ষণ করে।
এর সঙ্গে আবিষ্কার করি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, অমর মিত্র, ও স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে। তাঁদের গল্পগুলো নিবিড়ভাবে পাঠ করি। গল্পগুলোর কলকব্জা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখি। তাদের কাছ থেকে গল্পলেখার ক্রাফটগুলো লিখি। এদেরকে গুরু বলে মান্য করি। এদের হাত ধরেই নিজের গল্পের ভুবনটি নির্মাণের চেষ্টা করছি।
এমদাদ রহমান :
সমকালীন বাংলাসাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের মূল প্রবণতাটিকে লক্ষ্য করলে, সেখানে ঠিক কোন পার্থক্যটি আপনার কাছে বিশেষভাবে ধরা পড়ছে?
কুলদা রায় :
লেখালেখি লেখকের নিজের জীবনের একটি শিল্পকর্ম। লেখক কিভাবে নিজেকে গড়ে তুলছেন সেভাবেই লেখাটি হয়ে উঠবে। লেখাটি হয়ে ওঠার পরে সেটি আর লেখকের থাকে না। লেখা নিজেই একটি জীবন হয়ে ওঠে—আলাদা শিল্পকর্ম হয়ে পড়ে। এটাই লেখালেখির আদি ও অকৃত্রিম সূত্র।
এ সময়ের বিশ্বসাহিত্যের প্রবণতা হল চূড়ান্ত কোনো সত্যকে বাতিল করে দেওয়া। যে কোনো কিছুকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা—প্রচলিত অর্থের গণ্ডি থেকে শব্দকে বের করে আনা। অতীতের কর্তৃত্বপরায়ণ লেখন ভঙ্গিমাকে বাদাম পাহাড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মুক্ত লেখন ভঙ্গিমাকে পথ করে দেওয়া। নতুন করে এই পথের সর্বত্র নানা কোণ থেকে আলো ফেলে নতুন নতুন সম্ভাবনা ও আশঙ্কাকে উন্মোচন করা। এখন ফিকশনের প্রবণতা হল—অরৈখিক আখ্যান, সচেতন ভাবের মূর্ত প্রকাশের স্রোতধারা, বিনির্মাণবাদী সমালোচনা, ব্যাকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, সংলাপের প্রচলিত ধরনটাকে বদলে ফেলা—আখ্যানের অংশ করে ফেলা যাতে গল্পবস্তু আর সংলাপের মধ্যে কোনো পার্থক্যরেখা না থাকে। পরিসমাপ্তিহীন আখ্যান লেখা। টাইমফ্রেমকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়াও এ সময়ের অন্যতম কাজ। লেখালেখিকে কোনো নির্দিষ্ট শাখায় আটকে না রেখে বহুমাত্রিক শাখার মধ্যে মিলিয়ে-মিশিয়ে লেখাটাও এ সময়ের লেখালেখির অন্যতম প্রবণতা। যেমন বাংলা ভাষায় দেবেশ রায় লেখেন। ব্যক্তিগত জার্নাল, ঐতিহাসিক তথ্য, সংবাদপত্রের ভাষ্য বা খবর, কিংবদন্তী বা রূপকথা, পুরাণকথা, প্রতিবেদন আখ্যানের সঙ্গে এসে বসে পড়ছে। কখনো মনে হবে আখ্যান পড়ছি। আবার কখনো মনে হবে প্রতিবেদন পড়ছি। কখনো মনে হবে রূপকথা শুনছি। কখনো মনে হবে কোর্টে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে চলছে সওয়াল জবাব। এক ধরনের কনফিউশন তৈরি করে দেওয়াটাই এ সময়ের লেখালেখির নতুন ধরন। ফলে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসছে লেখক ও পাঠকদের মধ্যে।
এ সময়ের আরেকটি প্রবণতা হল কথকের একমাত্র স্বত্ত্ব বাতিল করে দেওয়া। বহু কথকের সমাবেশ ঘটানো। এই কথক হবেন তৃতীয় পুরুষ বা নাম পুরুষ। যেমন রশোমন চলিচিত্রে একটি খুনের ঘটনার দর্শক তিনজন। এই তিনজনই আলাদা আলাদাভাবে দেখেছেন খুনটি। তারা আলাদা আলাদাভাবে খুনের ঘটনাটির বর্ণনা দিচ্ছেন। একটি খুনের বদলে চারটি আলাদা খুনের ঘটনা ঘটেছে যেন। একটি খুনের মধ্য থেকে চারটি খুনের ঘটনা বের করে আনা। সবকটিই যেন সত্যি। ম্যাজিকের মতো ঘটনা ঘটে এটা দেখে। এটা তো কিছুই নয়—ভিউ পয়েন্টের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ম্যাজিকটি তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনটাও এ সময়ের অন্যতম কাজ।
আরেকটি বড় প্রবণতা হল—নানা দৃশ্যের অবতারণা ঘটানো। এই ধরনটা টিভি বা সিনেমাতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত আমরা একটি দৃশ্যের র মধ্যে থাকি। সেই দৃশ্যের স্থান ও সময় আমাদেরকে অভ্যস্থ করানোর জন্য নানা রকম ডিটেইল ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে আখ্যানের কোনো একটি পর্ব ঘটে। সেখান থেকে পরের পর্বে যাওয়ার জন্য লেখক আবার নতুন কার্যকারণ তৈরি করেন—নতুন ডিটেইল বসান। আমাদেরকে নতুন দৃশ্য ও সময়ে অভ্যস্থ করাতে লেখককে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। লজিক্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক করতে হয়। কিন্তু ক্যামারার মধ্যে দিয়ে এসব কিছুই লাগে না। দ্রুত সুইচ টিপে টিপে দিলে আরেকটি স্থান ও সময়ের মধ্যে পরিচালক অতি সহজেই নিয়ে যেতে পারেন। এর জন্য আলাদা কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন না করলেও চলে। আখ্যানের শুরু থেকেই এরকম একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে। ঠিক এইভাবেই আখ্যানেও দ্রুত দৃশ্যান্তর ঘটানোর কাজটি করেন কেউ কেউ। এতে পাঠক কখনো কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পান না বা সুযোগ গ্রহণ করেন—হুট করে এই নতুন দৃশ্যে তিনি এলেন বা তাকে নিয়ে আসা হল। এটা ফ্যান্টাসীর একটা ধরন। এ ধারার অন্যতম লেখক অমর মিত্র।
লেখক কোনোভাবে কর্তৃত্ব পরায়ণতা পোষণ করেন না। তিনি কর্তা হয়ে ওঠেন না তার লেখালেখিতে। তিনি থাকেন আখ্যান থেকে দূরে। তিনি হয়ে ওঠেন বর্ণনাকারী মাত্র। ভূমিকাহীন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে চরিত্রদের সঙ্গে তিনি কেঁদে ওঠেন না—হেসেও ওঠেন না। থাকেন নির্বিকার। ভাবলেশহীন। নির্মোহ। এই ঘটনার কোনো কিছুতেই তার সম্পৃক্তি নেই। তার দ্বায়িত্ব ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা। সত্যনিষ্ঠ থাকা। সে সত্যও চুড়ান্ত সত্য নয়। পাঠক সেখান থেকে আরেকটি সত্য পেতে পারেন। চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। ন্যায় দর্শনের মত—সেই মায়ার খেলা। অন্ধকারে সাপ দেখে লাঠি মনে হতে পারে। আবার লাঠিকেও সাপ মনে হতে পারে। দুটোই দুরকম করে সত্য। যিনি লাঠিকে সাপ হিসেবে দেখেছেন—তিনি বলবেন—তিনি একটি সাপ দেখেন। সাপের বদলে তার কাছে সাপই সত্যি। আরেকজন হয়তো লাঠিকে লাঠি হিসেবেই দেখেছেন। তিনি বলবেন–তিনি লাঠি দেখেছেন। কোনো ভুল নেই। শুধু তার দেখাটাকে সত্যি করে বলাটাই তার দ্বায়িত্ব। এটা একটা ম্যাজিক।
এই স্টাইলটা মহাভারতে আছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা করছেন সঞ্জয় নামে একজন লোক। পেশায় তিনি বর্ণানাকারী বা কথক।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ লেগেছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে নিয়োগ করেছেন যুদ্ধের বর্ণনা করতে। ধৃতরাষ্ট্র আবার জন্মান্ধ। জগতের কিছুই তিনি চর্মচক্ষে দেখেননি। আবার তিনি যুদ্ধের একপক্ষের পিতা। আরেকপক্ষের পিতৃব্য। দুপক্ষই তার কাছে সমান স্নেহে লালিত পালিত হয়েছে। দুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতিই তার গভীরতর দুঃখের কারণ। তিনি রাজপ্রাসাদে বসে দূরের যুদ্ধটার বিবরণ এমনভাবে শুনবেন যেন তিনি নিজ চোখেই সব কিছু দেখতে পারেন। বুঝতে পারেন। ভাবতে পারেন। অসত্য বর্ণনা হলে রাজা কথককে ছেড়ে দেবেন না। তার মাথা কাটা পড়বে। ফলে কথক সঞ্জয়ের কাজটি খুবই কঠিন– অন্ধকে প্রকৃত যুদ্ধটি চক্ষুষ্মানের মত দেখাতে হবে।
কথক সঞ্জয় বর্ণনা করার আগে শর্ত দিয়ে রাখছেন—এই যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে তাঁর কোনো অভিমত থাকবে না। কোথাও তিনি নিজে অংশ নেবেন না। যেরকম ঘটছে ঠিক সেরকম করেই রাজাকে শোনাবেন। কিভাবে শোনাবেন? দেখে শোনাবেন। কিন্তু সঞ্জয় নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রেও নেই। আছেন রাজার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে। তাহলে তিনি কিভাবে দেখবেন? কিভাবে ঘটার কালেই ঘটনাটির বস্তুনিষ্ট বিবরণ বলবেন? তিনি কি বানিয়ে বলবেন? না। সেটা সম্ভব নয়। মহাভারতের কবি তাঁর চোখে একটি যাদু পুরে দিয়েছেন। দূর থেকেও তিনি যুদ্ধের সকল কিছুই ক্যামেরার মত দেখতে পারবেন। সেটা দেখেই রাজাকে টেলিকাস্ট করতে পারবেন। তার বলাটা এমন বাস্তব হয়ে উঠবে যে অন্ধরাজাও যুদ্ধকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন, কোথাও তার কনফিউশন থাকবেন না। এটাই ম্যাজিক রিয়ালিজম।
এ সময়ের লেখক একজন কথক সঞ্জয়। আর পাঠক হলের অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র।
পাঠক একজন গল্পকারের কাছ থেকে এমনভাবে কোনো আখ্যান জানতে চান যে-আখ্যানটি তার ধারণার মধ্যেই নেই–কিন্তু তিনি পড়তে পড়তে সেই কাহিনীর অন্তর্গত হয়ে পড়বেন। মনে হবে যেন গল্পকারের কাছ থেকে শুনছেন না। গল্পটি তার চোখের সামনে ঘটছে। প্রতিটি চরিত্রকে চেনেন। পরিবেশটাও জানা। এবং যা ঘটছে সে বিষয়ে লেখকের কাছ থেকে অভিমত নেওয়ার দরকার নেই–তিনি নিজেই ঘটনাটির বিষয়ে অভিমত নিতে পারবেন।
এই যে লেখালেখির নতুন প্রবণতাগুলো আমরা বিশ্বসাহিত্যে দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কি আমরা ধরে নেবো লেখালেখির প্রচলিত পদ্ধতিটি বাতিল করে দিতে হবে? লেখালেখির জন্য লেখালেখির কোনো পদ্ধতিই অধ্যায়নের দরকার নেই। না। এ সময়ের একজন লেখক ২৪ ঘণ্টাই লেখক। তিনি ১০০% পেশাদারি লেখক। পেশাদারিত্ব অর্জন করার জন্য লেখালেখির সকল ক্রাফটগুলো তিনি শিখবেন। সেগুলো সহজে আয়ত্ব করবেন। তাতে দক্ষতা অর্জন করবেন। চর্চা থাকবে। শিল্পের সকল মাধ্যমেই তার অবাধ যাতায়াত থাকবে। তিনি হয়ে উঠবেন লেখালেখির মাস্টার আর্টিস্ট। তিনি সেই লেখালেখির চরিত্র সৃষ্টি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি করবেন। টেনশনে ফেলে দেবেন পাঠককে, সাসপেন্স সৃষ্টি করবেন। পাঠককে নিয়ে যাবেন চূড়ান্ত ক্লাইমেক্সে। এগুলো তিনি ব্যবহার করবেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। কিন্তু এর সঙ্গে নতুন কিছু টুলস তিনি যোগ করবেন। বদলে দেবেন ভিউ পয়েন্ট। এভাবে পুরনো পুরনো ফ্রেম ভেঙে তিনি নতুন উদ্ভাবনে যেতে পারবেন। নতুন কিছু করা ছাড়া লেখকের লেখার কোনো অর্থ নেই।
ঠিক এই জায়গাটিতেই বাংলা সাহিত্য স্থবির হয়ে পড়েছে। তারা পুরনোকেও জানেন না। বর্তমানকেও জানতে চেষ্টা করেন না। ভবিষ্যতকে জানার কোনো উদ্যোগ নেই। কোনো নিউ লুক তাদের মধ্যে নেই। নেই যৌক্তিক কল্পনার সৃজনমেধা। নেই কল্পনাকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেবার ক্ষমতা। ফলে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কল্পগল্পের ধারাটি গড়ে ওঠেনি। হরর স্টোরী নেই। রম্যগল্প নেই। রূপকথা লেখা হচ্ছে না। থ্রিলার গল্প হচ্ছে না।
যেটা হচ্ছে সেটা খিস্তি খেউড়। ভাড়ামো অথবা অলেখা। অথবা সাবেক পাকিস্তানী মডেলে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুৎপাদন। তারা লেখালেখি করার চেয়ে নাম ফলানোতেই ব্যস্ত। আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আছেন, হাসান আজিজুল হক আছেন, হূমায়ূন আহমেদ আছেন। আমরা কেউ খুঁজেও এদেরকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করি না। তাদের লেখাকে পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে দেখি না। গল্পের মধ্যে থেকে গল্পের কলকব্জাগুলো খুলে খুলে দেখি না। গল্প-নির্মাণের পথে যাই না। অথচ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ভরেই রয়েছে অসামান্য সব মহত্তম গল্প। লেখার কায়দাটা জানতে পারলেই লেখা সম্ভব সেই মহৎ কাহিনীগুলো।
সাহিত্যের জন্য এর চেয়ে মর্মান্তিক দুদর্শা আর নেই। ফলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বাংলা সাহিত্য হয়েই টিকে থাকতে চাইছে। বিশ্বসাহিত্য হয়ে উঠছে না। ওঠার লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না।
এমদাদ রহমান :
‘আমি স্পেনের জন্য গান গাই আর আমি তাকে অনুভব করি আমার মজ্জার ভিতর। তবে, এই সবকিছুর আগে আমি এই পৃথিবীর লোক, সকলের ভাই। না, আমি কোনও রাজনৈতিক সীমানায় বিশ্বাসী লোক নই’। এই কথাগুলি কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা’র। কবি এখানে বিশ্ববোধের কথাই তো বলছেন। আপনার প্রবাসজীবন অর্থাৎ ডায়াস্ফরিক অবস্থান, আপনার লেখালেখি, ভাবনা, সাহিত্যপাঠ, মূল্যায়ন ও পাঠকৃতিতে কী ধরণের প্রভাব ফেলছে?
কুলদা রায় :
দেশে থাকতে আমি কখনোই বড় শহরে বাস করিনি। ঢাকা শহরে পেশাগত কাজে গেছি মাত্র। কাজ সেরেই আবার ফিরে গেছি মফস্বলে—গ্রামে। এবং কোনো সাহিত্য কর্মও করিনি। শুধু দেশ ও মানুষকে সমগ্ররূপে নিজের মধ্যে ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। কোনো খণ্ডবোধ আমার মধ্যে ছিল না। আবার প্রবাসে এসে আমার চিন্তাজগতের মধ্যে বিপুলভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা হল বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধের মধ্যে দিয়ে আমার স্বদেশের অভিজ্ঞতাগুলো চালান করছি। তার দুর্বলতাকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করছি। ফলে আমি নিজেকে দেখি বিশ্বমানবের অন্তর্গত হিসেবে। আমার ভেতর থেকে ধর্মবোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রদায়-বোধটি কেটে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রমন্যতা মুছে যাচ্ছে। বহুর মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে পাচ্ছি। এই ঐক্যই আমাদের আদি পরিচয়। এই পরিচয়টিকেই ক্ষমতার কাঠামো ভুলিয়ে দিতে চায়। আমি এই ভুলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকে মানি না। আমার লেখালেখি তাই বিস্মৃতির বিরুদ্ধের স্মৃতির লড়াই। এটাই আমার ডায়াস্ফরিক অবস্থানগত লাভ। এটাই আমার লেখালেখির কাঠামো।
এমদাদ রহমান :
এই প্রশ্নটি বেশ আগে হাসান আজিজুল হককেও করা হয়েছিল। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, মানুষ আপনার লেখা কেন পড়বে? আসলে জানতে চাইছি, মানুষ সাহিত্য পড়বে কেন? কী সেই প্রয়োজন?
কুলদা রায় :
মানুষ আমার লেখা পড়বে না। তার নিজের লেখাটিই পড়বে। নিজেকে পড়বে। আমি যে মানুষটি সে মানুষটি তো একক কোনো মানুষ নয়। সকল মানুষকে নিয়েই আমি মানুষটি। ওই গাছটিও আমি। ওই মাছটি অথবা পাখিটিও আমি। যে নদীতে আমি স্নান করেছি—সে নদী আমিই। আকাশটি আমি। যে হাওয়ায় আমি শ্বাস নেই সেও আমি। উপনিষদে এই আমাকে বলা হয়েছে—অহম বয়ম। আমিই সে-ই। সে-ই আমি। আমি ভুবন ভরা। আমি এক অখণ্ড সত্ত্বা। এই অখণ্ডকে জানার আগ্রহের কারণেই মানুষ পড়বে অখণ্ড মানুষের লেখালেখি।
এমদাদ রহমান :
মানুষ কি খুব দ্রুত বই বিষয়টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?
কুলদা রায় :
আমার কাছে সে রকম এক সময় মনে হত। কিন্তু আমি ভালো করে দেখেছি বই পড়াটা মানুষের রক্তের মধ্যে আছে। তাকে ছেড়ে দূরে থাকা অসমভব।
এমদাদ রহমান :
একটি চিরকালীন প্রসঙ্গে আসছি। উম্বের্তো একো’কে বইয়ের ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, দ্য বুক উইল নেভার ডাই।
কুলদা রায় :
বই হল মানুষের স্মৃতি। এ স্মৃতি মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে বহন করে। নিজের মধ্যে রাখে। পরের জন্য বাঁচিয়ে রাখে।
মানুষ অমৃতের সন্তান। সে কেনো মরবে? মানুষ মৃত্যুহীন। লেখার মধ্যে দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকবে চিরকাল।



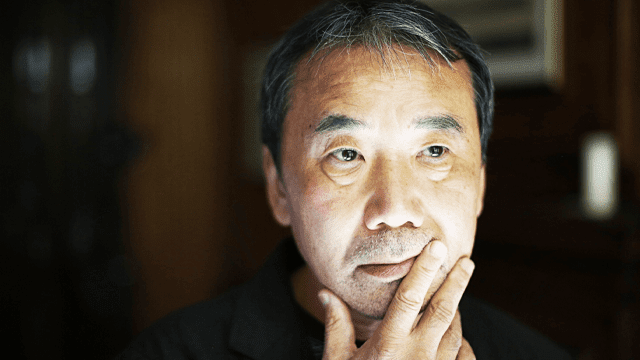






0 Comments