আমার অনেক কিছু বলার আছে, বেদনা আছে
পুরুষোত্তম সিংহ
কুলদা রায় আমার অত্যন্ত প্রিয় গল্পকার। কুলদা রায়ের গল্প আমি মুগ্ধ চিত্তে পড়ি। তাঁর গল্প পড়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। অথচ তিনি লেখেন কম। একটি গল্পের জন্য অনেক সময় নেন। বহু ভেবে চিন্তে বোধহয় একটি একটি করে অক্ষর সৃষ্টি করেন। তাঁর কোন তাড়াহুড়ো নেই, লেখক হওয়ার বাসনা নিয়েই, আপন খেয়ালেই লেখেন।
গল্প প্রকাশের তেমন কোন তাগিদ নেই। গল্প শেষ করে বুঝি উপলব্ধি করেন –‘হা কৃষ্ণ’ – সব শেষ। আর ভাবার কোন জায়গা নেই। আবার নতুন করে ভাবতে হবে। আমার কুলদা রায় পাঠ শুরু হয়েছিল ‘কাঠপাতার ঘর’ দিয়ে। তিনি যে গল্প লেখেন জানতাম না। সাহিত্যিক অমর মিত্র পড়তে বলেছিলেন ‘বৃষ্টি চিহ্নিত জল’ গ্রন্থ। পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। এমন গল্পকারকে না পড়া যেন নিজের পাঠক সত্তার অপূরণীয় ক্ষতি। তারপর কতজনকে যে সে বই পড়তে বলেছি তার ইয়াত্তা নেই। এবার শুরু ‘মার্কজের পুতুল ও অন্যান্য গল্প’ নিয়ে। তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন, দেশত্যাগের বেদনা উপলব্ধি করেছেন, স্বজন হারানোর বেদনা মর্মে মর্মে বহন করে বেড়ান। নিজের দেশের ক্রমগ্রাসমান অবস্থা মেনে নিতে পারেননি। সাধারণ মানুষের ওপর রাষ্ট্রের নিপীড়ন দেখে তিনি ক্রূদ্ধ হন। সেই অভিমান, বেদনা যেন চোখের জল দিয়ে ছোট ছোট বাক্যে সাজান। এ যেন স্বজন হারানো বেদনার বহিঃপ্রকাশ। এই অক্ষর সৃষ্টি কোন অভিপ্রায় থেকে উঠে আসে তা আমরা জানি না। গ্রন্থের ‘ভূমিকথা’ অংশ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরি –
‘’জুম্মাবারের নামাজ সেরে মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান গ্রোসারিতে যাচ্ছেন। তার দাড়ি বৃষ্টিচিহ্নিত।
আমার ভাগ্নি তুতুন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করে, মামা তুমি কি পুজো করো।
উত্তর দেই হেসে হেসে, না। কখনো পুজো দেইনি।
--তাহলে তুমি কী করে হিন্দু ?
--আমি ঈশ্বরের মানুষ। কোনো ধর্মের দানব নই।
শুনে ঈশ্বর আবার এক পশলা জল ঝরিয়ে বলছেন, আনন্দ। আনন্দ।
তিনি আনন্দে আছেন। আনন্দে থাকেন। সেই আনন্দের অক্ষর দিয়েই এই বইটি মুদ্রিত।‘’
বাস্তব-অবাস্তব, পরাবাস্তব, মায়াবাস্তব, জাদুবাস্তব, ফ্যান্টাসি নিয়ে পাঠককের চেতনাকে দুলিয়েছেন ‘ঘোড়া রত্তনের অশ্ব’ গল্পে। তিনি পাঠককে গল্পের এক গভীর রহস্য নিকেতনে ডুবিয়ে দিয়েছেন। আজকের গল্প পুরোপুরি বাস্তবকে সামনে রেখে গড়ে উঠবে না। আঁকড়া বাস্তব বা বাস্তবের হুবাহু বর্ণনা করে গল্প লেখার দিন আজ সমাগত। তবে লেখক বাস্তবকে ছেড়েও যাবেন না। ফলে লেখককে গল্প কৌশলে পরিবর্তন আনতে হয়, আখ্যান, টেকনিক, বিন্যাস সজ্জায় বড় পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এ গল্পের পুরো প্লটটাই দাঁড়িয়ে আছে একটি রহস্য নিকেতনের ওপর। আবার একে পুরোপুরি অবাস্তব বলেও বাতিল করে দিতে পারি না। তিন প্রজন্মের লোককথা, লোকশ্রুতি যেন শুনিয়ে গেলেন রত্তন। সেই লোককথা, লোকশ্রুতির কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা আমরা জানি না। জানার দরকারও নেই। সেই লোকশ্রুতির সবটা যে সত্য বা মিথ্যা তেমন নয়। আসলে এভাবেই আদিম মানুষ কাহিনি রচনা করেছিল, গল্প গড়ে তুলেছিল। সেই কাহিনিই যেন আবার তিনি পরিবেশন করতে চাইলেন, কিন্তু নিজের সময়ে বসে। রত্তন মোল্লা ঘোড়া খুঁজতে বেরিয়েছে। বলা ভালো ঘোড়া কিনতে বেরিয়েছে। কেননা ঘোড়া ছাড়া বিক্রমপুরের রওশোনেরা আসবে না। ঘোড়ার চড়ে তাঁর দাদি শ্বশুর বাড়ি যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দাদুর টাকা ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সেই ঐতিহ্য পিতা ফটিক মোল্লা হয়ে রত্তন মোল্লা ঘোড়া কিনতে বেরিয়েছে। আর ঘোড়া কিনতে গিয়ে বারবার প্রতারিত হয়েছে আব্দুল আলি মুন্সির কাছে। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি অমর মিত্রের ‘অশ্বচরিত’ উপন্যাসের কথা। সেখানে শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াটি হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতেই ভানুদাস সারাজীবন ঘুরে চলছিল। ভানুর ঘোড়া খোঁজার নামে লেখক আবহমান ভারতবর্ষের এক কাহিনি লিপিবদ্ধ কর চলেছেন। এ গল্পে ঘোড়া কিনতে তিন প্রজন্ম চলে গেছে। গল্পের শেষে রত্তনের থলে থেকে তিন ধরণের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল –রানী ভিক্টোরিয়ার মাথাওয়ালা কাঁচা টাকা, জিন্না সাহেবের টুপিওয়ালা নোট ও শেখ মুজিবের হাসি মুখের ছবিওয়ালা টাকা। এ থেকে বোঝা যায় মোল্লা বংশ তিন প্রজন্ম ধরে ঘোড়া কেনার চেষ্টা করে চলেছে। তবে এ সত্য বিশ্বাসের কোন পটভূমি নেই। রত্তন মোল্লা কোনভাবে টাকা সংগ্রহ করতেও পারে। যেমন ভাবে কারও কারও কাছে পূর্বের টাকা থাকে। তবে গল্পের জন্য সে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি যে অবস্থান তাঁকে সামনে রেখেই এ গল্প আবর্তিত হয়েছে। আসলে আবহমান কাল ধরে রূপকথা, লোককথা যেভাবে মানুষ বহন করে এসেছে, ঠাকুমা-ঠাকুরদা যেভাবে অতীতের কাহিনি নতুন প্রজন্মের কাছে সত্য-মিথ্যার বন্ধনে চেতনায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে সেই রীতিতেই তিনি গল্প গড়ে তুলেছেন –
‘’মহিম দত্ত স্মৃতিশাস্ত্রী মশাই কী একটু হিসেব কষলেন চক্ষু বুজে। তারপর রত্তন মোল্লারে কইলেন , বাপা, তুমি যে কাহিনীটি আমারে কইলে সেই সেলিমাবাদ পরগনার জমিদার মসলেম উদ্দিন চৌধুরী দেড়শ বছর আগে ছিলেন। তখন তোমার দাদাজান ইনসান মোল্লার জন্ম হয় নাই।
-তাইলে মনে হয় আমার পরদাদার গল্প এইটা। অথবা তারও পরদাদার ঘটনা। ঘটনাটি কিন্তু সত্যি। আমার আব্বাজান কখনো মিছা কথা কন নাই।“ ( ঘোড়া রত্তনের অশ্ব, মার্কেজের পুতুল ও অন্যান্য গল্প, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, সোপান, পৃ. ২৭, ২৮ )
এক ভিত্তিহীন বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এ গল্পের আখ্যান। তবে লেখক তাঁকে বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে নিয়ে গেছেন। রত্তন মোল্লাকে আপাত দৃষ্টিতে পাগল মনে হতে পারে। এই অবাস্তবের মধ্যেও আঁকড়া বাস্তব যে নেই তা নয়। আছে সময় বিবর্তনের চিত্র। ডাক্তার রমজান আলির সখের ঘোড়া থাকলেও মোটরসাইকেল কেনার সঙ্গে সঙ্গে তা বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেও তিনি উড়ান দিয়েছেন। ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে রত্তন মোল্লা আজ বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ঘোড়া খোঁজার জন্য চুরির অপবাদে প্রহার সহ্য করতে হয়েছে। গল্পের শেষ হয়েছে পরাবাস্তবে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সে উড়ে গেছে। এই আপাত অবাস্তবতার ভিতরেও বাস্তবতার পাঠ আছে। বাংলাদেশের জনজীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও মানুষকে সামনে রেখেই তিনি গল্পের ফর্ম গড়ে তুলেছেন।
নাম গল্প ‘মার্কেজের পুতুল’। এ গল্প কুলদার পক্ষেই লেখা সম্ভব। পাঠকের মনে হতে পারে একটা ছেঁদা কথা বললাম। একটি গল্পের যে পাঠ একজন লেখক নির্মাণ করেন সে পাঠ অন্য লেখকের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তার থেকে ভালো বা মন্দগল্প লেখা সম্ভব। এমনকি সেই লেখকই দ্বিতীয় বার তেমন গল্প আর নির্মাণ করতে পারবেন না। আসলে কিছু গল্প লেখকের ভিতর থেকে উঠে আসে। ভাবনা বলয়ের গভীর চেতনা লিখিয়ে নেয়, সেই সঙ্গে আছে দেশ সমাজ সময় সম্পর্কে লেখকের গভীর বেদনাবোধ। কুলদাই এ গল্প লিখতে পারেন কেননা তিনটি দেশের অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে আছে। তেমনি দেশভাগের খণ্ড সত্য কীভাবে অলীক বাস্তবতায় মিশে যাচ্ছে তা আবিষ্কার করেন। তবে এ বাস্তবতাকে অস্বীকারের কোন পরিসর নেই। এক বহুমুখী পাঠের দাবি করে এ গল্প। এ গল্প একবারে লেখা সম্ভব নয়, তিনি ধীরে ধীরে গল্পের রহস্য আবিষ্কার করেছেন। লেখক খুব সচেতনভাবে এ গল্পের প্লট গড়ে তুলেছেন। কলাম্বিয়ান কার্নিভালে শাকিরা আসার কথা। কিন্তু লেখক জানান শাকিয়া আসবে না। এরপরেই গল্পে এসেছে মার্কেজ ও নেরুদার প্রসঙ্গ। নেরুদা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিল। বিষ্ণু দে’র সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছিল। গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ের বিসর্জনের চিত্র দেখে সে খুব ব্যথিত হয়। এরপরেই লেখক গল্পে প্রবেশ করিয়েছেন ভারতীয় জাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ। একজন জাদুকর যেভাবে পর্যায় ভেঙে ভেঙে শেষ সত্যে পৌঁছান গল্পও তেমন ভাবে এগিয়ে গেছে। এক সাধু নেরুদার সব শুনে একটি পুতুল দিয়েছিল নেরুদাকে। সাধুর বক্তব্য এই পুতুল থাকলে সে দৃশ্য আর মনে আসবে না। গল্পের চরিত্র যেভাবে গড়ে ওঠে, লেখক যেভাবে কল্পনার ভিতর থেকে চরিত্রকে নামিয়ে আনেন, রূপকথায় যেভাবে নায়ক প্রবেশ করে, জাদুকর যেভাবে শেষ পর্যায়ে এসে নিজের অনন্ত শক্তি প্রয়োগ করে দর্শককে ভেলকি দেখান এ গল্পেও শেষ পর্যায়ে এসে লেখক বাস্তবতার মুখোশ খুলে দেন। এক ভয়ংকর বাস্তবতার মুখোমুখি পাঠককে দাঁড় করাতেই লেখকের এই কৌশল। বরিশালের দাঙ্গায় ওপার থেকে এপারে চলে এসেছিল মুসলিম জ্যোৎস্না বেগম। সে ওপারে কৃষ্ণযাত্রায় রাধারানী সেজেছিল। তাঁর চেতনায় রাধার বেদনা, মনন মিশে আছে। লেখক এক অসাম্প্রদায়িক মনন নিয়ে এ গল্পের ক্যানভাস গড়ে তুলেছেন। দেশভাগের আগে হিন্দু-মুসলিমের তেমন বিভেদ ছিল না। জাতি ভিন্ন হলেও সংস্কৃতিকে তেমন ভিন্ন ভাবে দেখেনি বাঙালি। তানভীর মোকাম্মেলের ‘চিত্রা নদীর পারে’ চলচিত্র দেখলে স্পষ্ট হবে। কৃষ্ণ হিন্দু শ্যামদাসের প্রতি ছিল তাঁর ভালোবাসা। এপারে এসে সে ধর্ষিত হয়েছিল। শ্যামদাস চলে গেছে কলাম্বিয়ায়। মার্কেজ গল্প উপন্যাসে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর ঠাকুমার কাছে যে কাহিনিগুলি শুনেছিলেন সেই রীতিতেই অবাস্তবতার আড়ালে জীবনের গভীর বাস্তবতার পাঠ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সে জাদুবিদ্যা তাঁর দেশের। ফলে তাঁর হাতে পুতুল আর রাধারানী হয়ে ওঠে না। অথচ সেই ফেলে দেওয়া পুতুলই কলাম্বিয়ার রাস্তায় ঘুরে বেরানো শ্যামদাসের হাতের জাদুতে হয়ে ওঠে রাধারানী। আপাত কার্নিভালের আড়ালে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম জীবনের এক গভীর জীবনচেতনার পাঠ কুলদা রায় এ গল্পে দিয়ে যান। তেমনি ভারতীয় জাদুবাস্তবতা ও লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতা যে সম্পূর্ণ পৃথক তা সচেতন ভাবেই দেখিয়ে দেন। মার্কেজ শাকিরাকে আনতে পেরছে, শ্যামদাস রাধারাণীকে। বাঙালি সংস্কৃতির এক ভিন্ন রূপ তিনি এ গল্পে দেখান। মানুষগুলি একই ছিল, জাতি আলাদা হলেও সংস্কৃতিকে তাঁরা পৃথকভাবে দেখেনি। সেই সংস্কৃতিকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের সঙ্গে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অচল, তেমনি কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নিজের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করতে পারেনা। দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষকে তিনি প্রেমের বীণায় এক সরলরেখায় মিলিয়ে দিয়েছেন। শ্যামদাসের রাঁশিতে আজও রাখির সঙ্গে সোনার টিকলি ঝোলে।
তিনি গল্পে গাছ বোনেন। গাছকে বড় করে তোলেন, ফুল ফোঁটান, পাঠক সে ফুলের গন্ধ পায়, তারপর বিদায় নেন। আসলে তিনি জীবনের কথা বলেন। এ যেন ‘আমার গল্পটি ফুরালো নটে গাছটি মুড়োলো’। ফোঁটা ফুল তিনি মানুষের হাতে পৌঁছে দেন, দেবতার পায়ে নয়। ধর্ম অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠতায় তিনি বিশ্বাস করেন। পুস্প কাননের স্বপ্ন নিয়ে যে কুড়িটি বড় হয়ে উঠেছিল, যার জন্ম মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের, সেখানে কত মানুষের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু মুক্তির স্বপ্নের বদলে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠতে শুরু করেছিল নবগঠিত দেশেই, সেই স্বপ্নভঙ্গ তিনি ভুলবেন কী করে ? হুমায়ুন আজাদ গভীর বেদনা থেকে লিখেছিলেন ‘আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম’ গ্রন্থ। কী চেয়েছিল মানুষ, আর কী পেল। বাংলাদেশের ইতিহাসের সংস্কৃতির ধ্বংস, অত্যাচারকে সামনে রেখে তিনি লিখেছেন ‘রজনীগন্ধা ফুলটি যেদিন ফুটেছিল’ গল্প। ফুল ফোঁটা অবধি তাঁর অপেক্ষা বা বলা ভালো যাবতীয় বক্তব্য পরিস্ফুটনের পরেই ফুল ফোঁটা, তা সুন্দরের হাতে তুলে দিয়েই বিদায়। এই ক্যানভ্যাস আঁকতে তাঁকে পরাবাস্তবের আশ্রয় নিতে হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মুসলিমদের হাতে নারী কীভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে তা দেখান। জাগিগান, ভাটিয়ালি গান, কবিগান যাঁরা মুগ্ধ চিত্তে উপলব্ধি করত, সময়ের বিবর্তনে হিন্দি সংগীত কীভাবে জনচিত্তকে গ্রাস করছে তা দেখান। মহীতোষ বাবুর কন্যা শেফালিকা যে সুন্দর গান করত, সে অপহৃত হয়েছিল মেজর আতিকের দ্বারা। শেফালিকার হারিয়ে যাওয়া নিয়ে লেখক কতগুলি কারণ অনুমান করেছেন। এর মধ্যে ষষ্ট কারণটি হল –‘’দুঃসাহসী কয়েকজন সন্দেহ করল, মেজর আতিক তাকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছেন। তাকে বিয়ে করেছেন। ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে কেউই একথাটি মুখ বলতে পারল না। মেজর আতিক কিছুদিন এ শহরেই ছিলেন। তারপর শোনা যায়, পাকিস্তানের কাকুলে উচ্চতর ট্রেনিং নিতে চলে গেছেন।‘’ ( তদেব, পৃ. ৪৫ ) শেফালিকা মৃত হয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি থেকে অনুমান করেই নিতে হবে সে ধর্ষিত হয়েছে। লেখক বাস্তব-অবাস্তব, সত্য-অর্ধসত্যের মধ্যে কাহিনিকে দুলিয়েছেন। এই শেফালিকারাই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি বেলি ড্যান্সের শেলি খানকে। জনরুচি কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা লেখক দেখান। কিন্তু লেখক গল্পের উড়ান দেন পরাবাস্তবতায়। শেফালিদের টবে বোনা রজনীগন্ধা গাছটি নিয়ে গিয়েছিল আব্দুস সামাদ। আজ ফুল ফুটেছে, তাঁরা এসেছে শেফালিকার খোঁজে। পরাবাস্তবতায় পানসিতে পেয়ে যান শেফালিকাকে, ফুলটি দিয়ে দেন –‘’পানসিটা তরতর বেগে দূরে মিলিয়ে যায়। শরিফুন্নেসা জলের দিকে পা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যায়। রজনীগন্ধা ফুল জলে ভাসিয়ে দেয়। ভাসিয়ে দিয়ে দেখতে পেলো চাঁদের আলোতে জলের নিচে কী একটা চকচক করছে। নিচু হয়ে তুলল। সেটা একটা লকেট। শাদা শঙ্খের এই লকেটটিতে লেখা, শেফালিকা।‘’ (তদেব, পৃ. ৫৪) এক অদ্ভুত মায়াবাস্তবতায় তিনি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যান। কুলদার হাতে একটা সোনার কলম আছে। সেই কলমের ভেতর বাংলাদেশের যাবতীয় ধ্যান ধারণা আছে। বিদেশে বসে সেই কলমে তিনি বারবার রঙ লাগান। নিব থেকে যেন সোনার পাতে রুপোর অক্ষর সাজিয়ে দেন। এক অদ্ভুত ভাবে তিনি গল্পের পরিণতি ঘটান। যেন সবটা যেনেই তিনি এই পরিণতিতে পৌঁছেছেন। কাহিনির মালা গাথা নয়, শক্ত হাতে তিনি কাহিনি ধরে থাকেন, চরিত্রের বিকাশ নয়, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা, সেই যাত্রাপথের দুদিকের চিত্র, একাধিক ঘটনা ও চরিত্র এনে বিনিসুতোর মালা গেথে পরিণতিতে পৌঁছে যান। যেখানে পাঠক পৌঁছে পান মুক্তির স্বাদ। এমনকি অন্য গল্পকার থেকে কুলদার গোত্র পৃথক করে নিতে বাধ্য হন।
কুলদার গল্পে একটা রূপকথা আছে। ঝোলার বিড়াল আছে। সে বিড়াল গল্পের অন্তিম মুহূর্তে বার হয়ে আসে। সে জন্য গল্পের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি একটা পরিসর গড়ে তোলেন। একটা মোড় ভাঙার দিকে বিন্দু বিন্দু করে এগিয়ে যান। সেই এগিয়ে যেতে যেতেই তিনি জনজীবনের ইতিহাস লিখে চলেন। দেশ রাষ্ট্র সমাজকে এক সরলরেখায় রেখে তিনি কথক ঠাকুরের মতো বা চরিত্রের মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে বাস্তব থেকে ক্রূর বাস্তবের দিকে কাহিনকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু গল্পের মোড় ভেঙে দেন না। ‘পরেশ মাস্টারের পরিবার’ গল্পে মতুয়া সম্প্রদায়, নমঃশূদ্রদের লড়াই, বরিশালের যোগেন মণ্ডলের লড়াই, মন্ত্রী হওয়া ও দেশত্যাগ, হাজৎ বিদ্রোহ সহ দেশভাগ পরবর্তী এক চিত্র এঁকেছেন। সে সময় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের। সেদিন যুবকরা কমিউনিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নতুন চেতনার ডাক দিয়েছিল। যুবক পরেশ সেদিন ছিল কমিউনিষ্ট। অন্নপূর্ণা ও রামনাথ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সমস্ত মতুয়ারা ওপারে চলে গেছে, রামনাথও যেতে চেয়েছে কিন্তু দিদি অন্নপূর্ণা যেতে চায়না। এই না যেতে চাওয়ার মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে আছে। কালশিয়া গ্রামে ছিল অন্নপূর্ণার মামার বাড়ি। সে গ্রামেই ছিল কমিউনিষ্টদের গোপন আশ্রয়। কিন্তু পুলিশ অভিযান চালালে অন্নপূর্ণার মামা মিথ্যা বিবাহ দিয়ে পরেশকে রক্ষা করেছিল। পরের দিন পরেশকে মামা পার করে দেয়। এরপর অন্নপূর্ণা আর বিবাহ করেনি। এই নকল স্বামীকেই আসল স্বামী ভেবে প্রতিক্ষায় বসে আছে। এ প্রতিক্ষায় ছাব্বিশ বছর কেটেছে। প্রমাণ হিসেবে রয়েছে পরেশের একটি ডায়েরির পাতা। কালশিয়া গ্রাম থেকে বিদায় নেবার কালে পরেশ ডায়েরি ফেলে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে আবার ডায়েরি নিতে এলে অন্নপূর্ণা ডায়েরি দিয়ে দেয় কিন্তু মামা একটি পৃষ্টা ছিঁড়ে রেখেছিল। এই পৃষ্ঠার সূত্র ধরেই অন্নপূর্ণা আজ ছাব্বিশ বছর পর স্বামী খুঁজতে বেরিয়েছে। প্রথমে কেউ বিশ্বাস না করলেও পরেশ হাতের লেখা দেখে বুঝেছে এটা তাঁরই ডায়েরি, এমনকি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ডায়েরির ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা নেই। ডায়েরিতে লেখা ছিল কার্ল মার্ক্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি –
‘’Communists must be ready at all times to stand up for the truth-be-cause truth is in the interrests of the people-communist must be ready at all time to correct their mistakes – because mistakes are against the interests of the people
Karl Marx –selected works-vol iv-p.315
নিচে তারিখ লেখা 2nd December 1949 f kalshira f mollahat – Bagerhat f PB পি অক্ষরের মধ্যে একটা ফোটা।‘’ ( তদেব, পৃ. ৭১ )
গল্পের শেষে প্রাকৃতিক ঝড় উঠে এল। লেখকও শব্দ ঝরে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে গেলেন। রঙ্গমঞ্চের প্লট যেন এলোমেলো হয়ে গেল। লেখকও অকৃত্তিম সত্য কথাটি বের করে নিয়ে এলেন। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে ব্যক্তি বিপর্যয়ের যে সূচনা হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তা যেন সমাধান হতে চলেছে। এরমধ্যেই কেটে গেছে ছাব্বিশ বছর। অন্নপূর্ণার মতো এ গল্পও অপেক্ষার গল্প। অপেক্ষার শেষে আছে অমৃতের স্বাদ। একটি বিষয় মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তো ছোটোগল্পের এই সংজ্ঞাই দিয়েছিলেন। তাহলে কুলদা রায় কোথায় দূরে সরে গেলেন। কুলদা সময় ও পরিসরের চিত্র আঁকেন। তিনি হুট করে থেমে গিয়ে বিদায় নেন না। গল্পের একটা নির্দিষ্ট ছক অঙ্কন করেই সেই ছকে ভেসে বেড়ান। পরিসমাপ্তিটা তিনি জানেন কিন্তু পাঠক জানেন না। সে জন্যই তিনি গল্প শোনাতে চান। দুরূহ ও জটিল শব্দ প্রয়োগ তাঁর গল্পে নেই। গল্পকে তিনি অযথা জটিল করে তোলেন না। বাংলাদেশের জনজীবনের হৃদয় আত্মার কথা তিনি আবিষ্কার করেন। হারানো দেশের জন্য মমতা নয়, জীবনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা গভীর সত্য তিনি এঁকে চলেন।
তিনি শিল্পী। চিত্রশিল্পী। তিনি রঙের খেলায় নামেন। রং তুলি নিয়ে গল্প গড়ে তোলেন। নিজের দেশ সম্পর্কে তাঁর ঝুলিতে অজস্র অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাগুলি তিনি আশ্চর্য সুর তালে ছন্দের বিন্যাসে গল্প সজান। সুর-তাল-ছন্দের বিন্যাস শুনে আপনার মনে হতে পারে হয়ত অতিরঞ্জন কিন্তু পাঠকের যাবতীয় ধারণা ভেঙে যাবে কুলদা রায়ের গল্পপাঠে। গল্পের নাম ‘চাঁপাকথা’। এক অবরুদ্ধ বেদনার বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের জনজীবনে কত ফুল। সেসব ফুল নিয়ে তিনি এ গল্পে খেলেছেন। শৈশবের ফুল নিয়ে খেলার দিনগুলি ফিরিয়ে এনেছেন। ‘চাঁপাকথা’ শব্দটির ‘চাপা’ অর্থে লুকিয়ে রাখা বা চলতি ভাষায় যদি ‘ধামাচাপা’ অর্থ ধরি তবে সে সত্য আরও বৃহৎ ব্যাপ্তি পায়। উইলিয়ামস ট্রেমর আঁকা রোজ ট্রেমেইন ছবির কথা কন্যাকে বলতে গিয়ে পিতা ফিরে গেছে নিজের শৈশবে। সেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কন্যার নাম রাখা হোত ফুলের নাম দিয়ে। সব ফুল কি দেবতার অর্ঘ্য পায় ? সব ফুলই তো ফোঁটার পর ঝরে যায়। এরসঙ্গে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন দেশভাগের সত্যকে। দেশভাগে হিন্দুদের এপারে চলে আসার বৃত্তান্ত। তেমনি মুসলিম গুলমোহররা এপার থেকে ওপারে গিয়ে আশ্রয় গড়ে তুলেছিল। গুলমোহর বানু আজ আশ্রয় নিয়েছে মালতীদের বাড়িতে। হিন্দুর বাড়ি দখল করে নিয়েছিল ওপারের মানুষ, ওপারের মুসলিমরা ভেবেছিল বাংলাদেশ তাঁদের, সেখানে হিন্দু মানুষের কোন অধিকার নেই। বাংলাদেশের জনজীবনের একটা সামগ্রিক চিত্র এ গল্পে লেখক পরিবেশন করেছেন। অজস্র চরিত্রের টুকরো টুকরো প্রসঙ্গ এনে একটা সামগ্রিক ইতিবৃত্তে পৌঁছতে চেয়েছেন। যে দেশ ছাড়ার জন্য বেদনা রয়েছে। কন্যাকে গল্প বলতে গিয়ে পিতা নিজেই কেঁদে ফেলেছেন। যে চাপাকথা গুলি এতদিন মনে আত্মগোপন করে রেখেছিলেন তা প্রকাশ হতেই চোখ ছলছল হয়ে উঠেছে –
‘’কোন সাড়া এলো না। আমাদের ভয় করতে লাগল। একটা বদ হাওয়া ঘুরে এলো। আর ঘরেই দরজাটিও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল। বাড়িটি ফাঁকা। রান্নাঘরে কয়েকটি কাটা সবজি গামলায় পড়ে আছে মাত্র। মালতীও নেই-চাঁপাও নেই। দুটি চুল বাঁধা ফিতে বিছানার উপর গড়াচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। হাওয়ায় উবে গেছে। সেটা দেখে আমাদের কান্না পেলো। সেই প্রথম আমরা সবাই সত্যিকারের কান্না করতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম কান্না ছাড়া আমাদের কিছুই নেই। সেটা ভেবে আজ আবার এই মধ্য বয়সে কান্না এলো।
দেখে আমার মেয়ে অবাক হয়ে বলল, কাঁদছ কেন ?
বললাম, কাঁদছি না তো। বলতে বলতে আবার চোখ বেয়ে জল ঝড়তে লাগল।
মেয়ে কী বুঝল কে জানে। বলল, দেশ থেকে ঘুরে এসো। নিশ্চয়ই চাঁপার সন্ধান পাবে।
হয়তো পেতে পারি। নাও পেতে পারি। তবে চাঁপার জন্য যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
বহু বছর পরে দেশে ফিরছি রিপভ্যান উইংক্যালের মতো। চেনা শহরটি আর নেই। গাছপালা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর আর মানুষও সব পালটে গেছে।‘’ ( তদেব, পৃ. ৯৮ )
শৈশবের সে চিত্র দ্রুত পাল্টে গেছে। সবাই যে উদ্বাস্তু হয়েছে তা নয়, কেউ কেউ সুখে আছে, কেউ কেউ বেদনায়। অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না ! সরকার লিপিবদ্ধ করে রাখেনি কত মানুষ দেশত্যাগ করল। এই যে হিন্দু সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ এর পিছনে কি সরকারেও ভূমিকা ছিল ? কিছু চাপাকথাকে উস্কে দেন লেখক। যে ইতিহাসেরও ওপর ধুলো পড়তে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে তা যেন তুলে ধরেন। নানাফুলের নানা গন্ধ থাকে । কিন্তু দেশত্যাগের গন্ধ কী ? বেদনার গন্ধ কী ?
তিনি গল্পে পরী নামিয়ে আনেন। মানুষের আখ্যানকেই তিনি পরীমানবে রূপান্তর করেন। বাস্তব থেকে তিনি আড়াল খুঁজে নেন। সেই আড়ালেই তিনি মানুষের গল্প বলে যান। বাংলাদেশের শেকড়ের গভীর থেকে তিনি গল্প তুলে আনেন। কুলদা বুঝি সমষ্টি চরিত্রে বিশ্বাস করেন। গল্পে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা বহু চরিত্রের ভিড় এসে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকটি চরিত্র সম্পর্কেই তিনি সামান্য করে বলেই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সেখানে কেউ কেউ কাহিনি ধরে থাকে। ‘’সত্য জানা ছাড়া এ জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।‘’ (তদেব, পৃ. ৭৩ ) – সেই সত্য সন্ধানে তিনি অগ্রসর হয়েছে। শ্যামল সত্যবদ্ধ জীবনের সন্ধান পেতে চেয়েছে। জীবনে বেঁচে থাকতে সত্যের সন্ধান করতে হয়। মিথ্যা বা মেকির ওপর জীবনের কোনো আদর্শ স্থাপিত হতে পারে না। আর স্থাপিত হলেও তা ক্ষণিক। তাই শ্যামল কবিরাজ মশাইকে শেষ সত্য জানিয়ে দিয়েছিল। মানুষকে বাঁচাতেই পরীর ছলনা করা হয়েছিল। ‘’সত্যের মুখ উজ্জ্বল সোনার পাত্রের দ্বারা আবৃত। সোনার ঢাকনা দেখে লোকে মজে থাকে। ঢাকনাটি সরিয়ে দেখতে চায় না তার ভেতর কী আছে।‘’ ( তদেব, পৃ. ৭৫ ) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-‘সত্য যে কঠিন’। কিন্তু এই কঠিনকে কেউ ভালোবাসতে চায় না। সবাই মেকিকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চায়। সত্যকে ভালোবাসার জন্য অনেক ত্যাগ, বিসর্জন প্রয়োজন। এই পরী জীবনের চিত্রের মধ্যেও তিনি বাংলাদেশের মৌলবাদী ধারণা স্পষ্ট করে দেন। সে দেশে রবীন্দ্রনাথ নিসিদ্ধ, তবে কাজী নজরুল ইসলামের গান চলবে। তেমনি মুসলিম নারীদের নাচ গান করা নিষেধ মৌলবাদী ধারণা অনুসারে। তবুও নরুদ্দিন মাস্টারের কন্যা নূরজাহান ওরফে রেখা মঞ্চে গান গেয়েছিল। মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই তাঁকে বিবাহ দিয়ে ভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবাই জানতো মেয়েটিকে পরী নিয়ে গেছে। এ শহরের সব হিন্দু আগেই চলে গেছে, কিন্তু কবিরাজ মশাই ছিলেন। কেননা কবিরাজ মশাইকে বড় প্রয়োজন। কিন্তু লেখক শেষে অধিবাস্তবতার স্তর ভেঙে দিয়েছেন। পরীজীবনকে অতিক্রম করে মানুষের চিত্র বড় করে তুলেছেন। রেখা , জামানদের প্রায় নির্বাসন ঘটে গিয়েছিল। বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে যে জামান বড় হয়ে উঠেছিল সে আজ স্ত্রী রেখার রক্ষায় আত্মমগ্ন। কেননা সে দেশের সমাজ পরিস্থির প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল নারীদের রক্ষা করা ভীষণ কঠিন। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ গর্জে ওঠে না। সেই মুখ যে প্রকৃতপক্ষে ‘মুখোশ’ এর আশ্রয় তা লেখক জানেন। সেই চরম বাস্তবের দরজা খুলে দিতেই তিনি পরীমানবের গল্প লেখেন। পরীকে সামনে রেখে তিনি মানুষের গল্প লেখেন, যে মানুষ অর্ধেক আকাশের নারী। বাংলাদেশের সমাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরাই সবচেয়ে বিপন্ন। সেই বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলতেই লেখক পরাবাস্তবতার জগতে ভেসে যান। আকাশের বুক থেকে মেঘ নামিয়ে এনে মাটির রুক্ষতাকে ভিজিয়ে দেন বটে কিন্তু রুক্ষ মাটির যন্ত্রণার চিত্রও পাঠককে দিয়ে যান।
তিনি সংস্কৃতির খোঁজে অগ্রসর হন। যে সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতি বেঁচেছিল। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদ ছিল না। অথচ সময় পরিবর্তনে সে সংস্কৃতির বিভেদ ঘটে গেল। আর এই বিভেদ ঘটাতে ওপারে মুসলিমরা বেশি সচেষ্ট ছিল। তবে সব মুসলিমই যে বিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। তবুও সময়ের পরিবর্তনে মিলনের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গেল, সেই হারানো সংস্কৃতি, বিপন্ন সংস্কৃতি খুঁজে বেরিয়েছেন ‘মধুশ্রীর খোঁজে’ গল্পে। ‘সখী, ওই বুঝি বাঁশি ডাকে’ গানটি কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করেছিল মুসলিম হাবিলের। ছোটবেলা থেকেই এ গান শুনে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রে এ গান গাওয়া নিষেধ। বন্ধ হয়ে গেছে সে যাত্রা পালাও। গল্প বর্ণিত হয়েছে গল্পকথক ও সোহরাব চাচার মধ্য দিয়ে। হবিব মিঞা আন্ধারমানিক গ্রামের সাবিকুন নাহারকে বিবাহ করেছিল। এ গ্রামের মধুশ্রী বড় ভালো এই গানটি গাইত। কৃষ্ণ যাত্রাপালা দেখে সেদিন মুগ্ধ হত হিন্দু মুসলিম সাধারণ মানুষ। পালাকারের পালা রচনার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু সময় বিবর্তনে ধীরেন বাগচী আর কারবালা পালা করতে পারেনি। হাবিব মিঞা সাহস সঞ্চার করলেও সম্ভব হয়নি। হাবিব মিঞার সুখী সংসার হলেও সে পাগল হয়ে গেছে। তবে মধুশ্রীর কণ্ঠে ‘সখী, ওই বুঝি বাঁশি ডাকে’ গানটি শুনলে চেতনা ফিরে পান। এতদিন স্ত্রী সন্দেহ না করলেও শেষে সন্দেহ করেছে হাবিব বুঝি ভালোবাসে মধুশ্রীকে। কিন্তু তা নয়, সে ভালোবাসত গানটি। মধুশ্রীকে ভালোবাসত সোহারাব। নিম্নবিত্ত হওয়ায় সে সত্য আর প্রকাশ করেনি, আজ তা গল্পকথককে জানিয়ে গেছেন। স্বামী সম্পর্কে সাবিকুন নাহারের যে ধারণা ছিল তা যেন ভেঙে যায় –
‘’তারপর আমার কানের কাছে মুখটি এনে সোহরাব চাচা বললেন, মধুশ্রীকে হাবিল মিয়া নয় আমি ভালোবাইসাছিলাম। তারে বিয়া করা আমার মতন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জীবনে অন্য কাউরে বিয়াই করি নাই।
সোহরাব চাচা আমার হাত ধরলেন। তখন আবার তার হাত আবার কাঁপতে শুরু করেছে। থামাতে পারছেন না। তার কথাও বেশ জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি এই কথাটা জীবনে অন্য কাউকে বলেননি। আমার কাছেই শুধু স্বীকার করলেন। এই গভীর গোপন কথাটা বলার জন্যই তিনি এতদিন অপেক্ষা করছেন। বলে তাঁর মুখটা সলজ্জ হয়ে উঠেছে। আবার চাপা পড়া ভারও নেমে গেছে। অনন্ত প্রশান্তি নিয়ে বললেন, সাবিকুন নাহার ভাবীর লগে তুমি দেখা কইরো। তারে কইয়ো, তিনি যেন হাবিল মিয়াকে ক্ষমা কইরা দ্যান।“ ( তদেব, পৃ. ১৮৪,১৮৫ )
গানের কোন শ্রেণি হয় না, জাতি হয় না। তা সুরের মুর্ছনায় মানুষকে মুগ্ধ করে। একটি জাতি যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল, যেখানে বিভেদের কোন বাতাবরণ ছিল না তা কালের গ্রাসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শুধু এ গল্পেই নয় কুলদা রায় এ গল্প সংকলনের বেশ কিছু গল্পে বাঙালি সংস্কৃতি কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তা যেমন দেখান তেমনি জীবনের আনন্দের জন্য ভারত থেকেও গান আমদানির প্রসঙ্গ দেখান। কুলদা রায়ের গল্প তৃতীয় বিশ্বের কাছে এক নতুন ভাষ্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের শেকড়কে সামনে রেখেই তিনি গল্প গড়ে তোলেন, কিন্তু গল্পের উত্তরণ ঘটে আমেরিকা মহাদেশে। বিপরীত ঘটনাও ঘটে। সেখান থেকে শুরু করে তিনি বাংলাদেশের জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করেন। চোখের সামনে নিজের জন্মভূমির কীভাবে পরিবর্তন ঘটে গেল তা আশ্চর্যভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরীরা যেমন স্বপ্নরাজ্যে বিচারণ করে বেড়ায়, এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে এক নিমিষে যেতে পারে তেমনি তিনিও পরীর মতো পাখা নিয়েই ওই সুদূর থেকেই জন্মভূমিতে প্রবেশ করে যান। সামান্য পরিসরে জীবনের এক বৃত্ততম সত্যের আভাস দিয়ে বিদায় নেন। এ গল্পগুলি যেন তাঁর জন্মভূমি দর্শন। সে দর্শনে আবেগ রইলেও বক্তব্য সচেতন। সে বক্তব্যই গল্পের ভিন্ন পরিমণ্ডল গড়ে তোলে।
‘দি র্যালে সাইকেল’ দীর্ঘ জার্নির গল্প। সাইকেলকে সামনে রেখে দেশের ইতিহাস সন্ধান। যে ইতিহাস তথাকথিত নিম্নবিত্তের ইতিহাস। এ ইতিহাস মানুষই বহন করে চলেছে। ইতিহাস যেভাবে গড়ে ওঠে, ভিন্নধর্মী মতবাদে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইতিহাস কীভাবে পাল্টে যায়, কালের ইতিহাসে যেভাবে চাপা পড়ে যায় তা বড় হয়ে ওঠে। আসলে মানুষই তো ইতিহাস রচনা করে, জনজীবনের গভীর থেকে উঠে আসে ইতিহাস। একটি সাইকেল সন্ধানকে সামনে রেখে লেখক পৌঁছে গেছেন দেশভাগের কালে। দেশভাগ, দাঙ্গা, ক্ষমতা হস্তান্তর, মুসলিমদের এপার থেকে ওপারে যাওয়া, নমঃশূদ্রদের ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় , মুসলিম লীগ, সঙ্গে ব্যক্তির সাতকাহন। গল্পের সূচনা বিন্দু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ রা এপ্রিল। এরপরই লেখক পৌঁছে গেছেন ১৯৪৬ এর দিনগুলিতে। একাধিক চরিত্র, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কখনও রিপোর্টিং ঢঙে, ব্যক্তির প্রেম ভালোবাসাকে সামনে রেখে তিনি এ আখ্যান নির্মাণ করেছেন। বিনোদিনীর সন্তান নীল একটি সাইকেল পেয়েছে মাটির গর্ত থেকে। ঝরে নারকেল গাছ উপড়ে যাওয়ায় সে সাইকেলটি পায়। এ সাইকলে সে প্রদর্শনীতে নিয়ে গেছে। আয়েনুদ্দিন মুন্সিরা ছিল এপারের মুসলিম, দেশভাগে ওপারে চলে যান। তাঁর একটি সাইকেল ছিল। সে সাইকেল সে বন্ধক দিয়েছিল বিধুবাবুর কাছে। পরে আয়েনুদ্দিনের সাইকেল নিতে এসেছে খবিরুদ্দিন। আয়েনুদ্দিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর কবরে যেন সাইকেলটা দেওয়া হয়। শহরের প্রবীণ সাংবাদিক মোজাম্মেল হক মুন্না। তিনি সাহিত্য লিখে তেমন খ্যাতি আর্জন করতে পারেননি। তাই আবার সাংবাদিকতা করছেন, তবে ভালো সংবাদও সংগ্রহ করতে পারেন না। তিনিই এই সাইকেল রহস্যের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। বলা ভালো মোজাম্মেল হক মুন্নার মধ্য দিয়ে লেখক একটা বিস্তৃর্ণ সময়ের ইতিহাস লিখেছেন। সে সাইকেলের গায়ে লেখা ছিল ‘POSTAL SERVICE OF INDIA-946’ এই সূত্র ধরেই একটা ইতিহাস উঠে এসেছে। তিনি রিপোর্টিং করেছেন দুইবার, কিন্তু রিপোর্ট যেহেতু তথ্যসমৃদ্ধ হয়নি তাই অনুসন্ধানে গিয়েছেন। সে অনুসন্ধানে এসেছে মতুয়া প্রসঙ্গ, নমঃশূদ্রদের অভিপ্রায় কার সঙ্গে যোগ দেবেন, যোগেন মণ্ডলের বৃত্তান্ত ও সিডিউলকাস্ট সম্মেলনের কথা। সিডিউলকাস্ট সম্মেলনে আম্বেদকরের আসার কথা থাকলেও আসেনি। সম্মেলনে সভাপতি কাকে করা হবে এ নিয়ে মত পার্থক্য হয়। শেষে ঠিক হয় সভাপতি করা হবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছেলে পিয়ার ঠাকুরকে। এজন্য সাইকেল প্রয়োজন। কিন্তু বিধুবাবু ছাড়া কেউ সাইকেল চালাতে পারেনা। কিন্তু বিধুবাবু সাইকেল নিয়ে ওড়াকান্দীতে পিয়ার ঠাকুরকে না আনতে গিয়ে চিতলমারি থেকে এক কন্যাকে বিবাহ করে এনেছেন। এ ঘটনায় সতীশবাবু ক্রূদ্ধ হয়ে ভাই বিধুকে তাড়িয়ে দিলেও বধূকে রেখে দেন, আর সাইকেলটি নদীতে ফেলে দেন, যদিও সে সাইকেলের নাম ছিল ফোনিক্স। এ বৃত্তান্ত মোজাম্মেলকে শুনিয়েছে অমৃত মুচি।
তবে লাল মিয়া সাইকেল নিয়ে ভিন্ন বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। যে আখ্যানে আছে ব্রিটিশ সরকারের ডাক বিভাগের কার্যকলাপ। হ্যামিলটন সাহেব রানার রতন মোল্লার কাজে খুশি হয়ে একটি সাইকেল পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। সে সাইকেল ছিল –‘’ব্রিটেনের র্যালে কোম্পানীর সাইকেল। খোদাই করে লেখা – পোস্টাল সর্ভিস অফ ইন্ডিয়া’’। বিধুবাবু চিঠি লিখত স্ত্রী স্বর্ণময়ীকে। সে চিঠি পৌঁছে দিন রতন গোপনে সরলাবালার কাছে। সরলাবালা মেজো বউ লীলাবতির দিদি। কিন্তু এ তথ্য ধরা পড়ে যায় সতীশবাবুর কাছে। তিনি ডাকবিভাগে নোটিশ করে রতনের বদলির ব্যবস্থা করেন গৌরনদীর তীরে। বিদায় কালে রতন সরলাবালাকে নিজের ভালোবাসার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু সরলাবলা যায়নি, এমনকি রতন মুসলিম বলেই বোধহয় যায়নি। মনে ভয় তো ছিলই। ছিল নারী সুলভ লজ্জা। তবে সে রতনের কাছে সাইকেলের বেলটি চেয়েছিল। বেলটি সে যন্ত্র করে নিজের পুটলির মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুকালে এই বেলটিকেও যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে রতন গৌরনদীর তীরে পোস্ট অফিসে কেন যোগদান করেনি তা জানে না লাল মিঞা। এমনকি সাইকেলটি নদীতে ফেলে দিয়েছিল কিনা তাও জানে না। রতনের কোন খবর ডাক বিভাগ দিতে পারেনি। তবে অনেকগুলি অনুমান মূলক কারণ আছে। সে অনুমানগুলিকে সামনে রেখে তদন্ত করেও কোন সাফল্য মেলেনি –
‘’এ সন্দেহগুলোকে উদ্দেশ্য করে আরো তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশভাগ হয়ে যায়। ইংরেজরা চলে যায়। হিন্দু অফিসারদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে বদলি নিয়ে দেশত্যাগ করে। তাদের স্থলে মুসলমান অফিসাররা অন্যান্য বিভাগের মতো ডাকবিভাগেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারা ছিলেন অনভিজ্ঞ। তাই অফিসকে গোছগাছ করার কাজে দীর্ঘমেয়াদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে বৃটিশ আমলের কোনো এক পোস্টম্যানের বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।“ (তদেব, পৃ. ১৪২ )
তবে সরলাবালার সাইকেল বেলটি পুটলিতে রাখা, ও মৃত্যুকালে তা পুড়িয়ে দেওয়ার বৃত্তান্ত লাল মিঞা মোজ্জামেলকে শোনায়নি, তা লেখক পাঠককে শুনিয়েছেন। এ গল্প এক হারানো সময়ের গল্প। হারানো ঐতিহ্যের গল্প। সাইকেলকে সামনে রেখে তিনি নিরুদ্দেশ অভিযানে বেরিয়েছেন। যেখানে রয়েছে সময়ের এক বৃহৎ পরিসর। কুলদার গল্পে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি অবস্থন করে। বিভেদের সংস্কৃতি এঁদের মধ্যে বিরাজ করেনা। কিন্তু যেটা বড় হয়ে ওঠে তা হল দেশভাগকে কেন্দ্র করে কীভাবে দুটি জাতি পৃথক হয়ে গেল। শুধু ধর্মের দিক থেকে পৃথক নয় সংস্কৃতির দিক থেকে দূরে চলে গেল। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ক্ষমতা লোভের বিভাজন বড় হয়ে উঠল। কুলদা শুধু গল্প লেখেন না তিনি সমাজিক ইতিহাস রচনা করেন। সে ইতিহাস বরিশালের বৃহত্তম ইতিহাস। বাংলাদেশের গভীর থেকে জনজীবনের ইতিহাস সহ মনোগত অভিপ্রায় ফুটিয়ে তোলেন। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেন মায়াবি ভাষা দিয়ে। গল্পের আখ্যানকে তিনি বড় কাঁটাছেড়া করেন। তবে তা টেকনিকে বিশেষ নয়, কাহিনিকে তিনি বারবার ভেঙে দেন। এক সমান্তরাল পাঠ কুলদার গল্পে পাওয়া যাবে না।
‘আয়ূব খানের ঘোড়া’ অনবদ্য গল্প। সীমিত পরিসরে তিনি গভীর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে আছে রাষ্ট্রীয় শোষণের ইতিবৃত্ত। পাকিস্তান পর্বে সাধরাণ মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিকথা। কলুদা তাঁর গল্পে যেটা বড় করে দেখান তা হল সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। ধর্মগত দিক থেকে মানুষগুলি পৃথক হলেও সংস্কৃতিগত দিক থেকে ছিল এক। হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে পৃথক কোন বস্তু ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান পর্বে বা তার পরে সেই বিভাজন বড় হয়ে উঠল। রাষ্ট্র নির্ধারিত করে দিল মানুষের সংস্কৃতি। মুসলিম গওহর আলী ছিলেন কবিগানের শিল্পী। তিনি কবিগান গাইতেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনগাথা বা বেদনাগাথা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। কিন্তু পাকিস্তান পর্বে তাঁর বড় চুল কেটে দেওয়া হল –‘’আয়ুব খানের আম্রি চুল কাইডা দিচ্ছে। কৈছে নয়া জামানায় এইসব চলবে না।‘’ ( তদেব, পৃ. ১৮৬ ) সে আজ হয়েছে ছাগল পালক। কিছুদিন পর শুরু হল ঘোড়া দৌড়। সেখানে বলি দেওয়া হল ছাগলদুটিকে। মুন্সী সাহেব গওহর কাছে গান শুনতে চায়। সে গান গায় –‘’প্রাণ সখীগো / আই শোন কদম্বডালে বংশী বাজায় কে ?’’। এ গানের ব্যাখ্যা শুনে মুন্সী সাহেবের মনে হয় ‘মালাউনগো গান। নির্দেশ দেওয়া হয় কান কেটে দেওয়ার। এখন সে কৃমির ঔষুধ বিক্রি করে। মাথায় জিন্না টুপি, কাটা কানে ছাগলের পরিত্যক্ত কান, আর গান গায় –‘’পিয়ারা দোসতা গো / আই শোন খাজুর তলায় শিঙ্গা ফুকায় কে ?’’ এখানেই তিনি গল্পকে নিয়ে যান জীবনের গভীর তলদেশে। ভাষা পাল্টেছে, ভাব কি পাল্টেছে ? একই কথা সে ভিন্ন ভাষায় গেয়ে চলেছে। খান সেনারা ও আয়ূব খানরা যে কত মূর্খ তা তিনি এ গল্পে প্রতিপন্ন করেছেন। সেই সঙ্গে আছে মানুষকে পশুতে পরিণত করা। ছাগলের কান নিজের কানে লাগিয়ে গওহর আলী কী এক ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিল না ? তেমনি ‘শুডকি ইনদুর’ এর চিত্রে বৃহৎ ক্যানভাস আঁকেন। সে পর্বে মানুষ তো ভয়ে ইঁদুরই হয়ে গিয়েছিল তেমনি ইঁদুরের মতোই তো দেশত্যাগ করেছিল। এক বহুস্বরিক ভাষ্য রচনা করে যান লেখক এ গল্পে।
( ২ )
এ গ্রন্থের ‘ভূমিকথা’ অংশ থেকে লেখকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরি –‘’এগুলো আমি লিখছি না। লেখার তো কিছু নেই। এই গল্পগুলো আমাদের দেশ গাঁয়ে ছিল এবং আছে। তার উপরে পলি পড়ে যাচ্ছে। জীবাশ্মের আকার ধারণ করছে। চাপা পড়ে যাচ্ছে। স্মরণপ্রদেশ থেকে মুছে যাচ্ছে। আমার কাজটি হলো, খুঁড়ে খুঁড়ে ধুলোমাটি সরিয়ে সরিয়ে সেই গল্পগুলো বের করে আনা। আবার মানুষের মর্মে ফিরিয়ে দেওয়া। এটা হলো একটা লড়াই। ঘৃণার বিরুদ্ধে সমষ্টিগত লড়াই। এই লড়াইটাই করছি আমি, আমরা সবাই।‘’ সে লড়াইয়ের গল্প হল ‘বিদ্যেসুন্দর’। জন্মভূমি তো মনোরম সুন্দর ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছিল বর্বর, হিংস্র। আর এই হিংসা সৃষ্টি করেছিল রাষ্ট্র। সবসময় যে প্রতিরোধ ছিল তা নয়। ভয়ে মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে কেউ কেউ যে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ করেনি তা নয়। সেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সম্প্রীতির গল্প লিখেছেন তিনি। এ গল্পের গদাধর ও বিদ্যেধর ছিল কিনা তা আমরা জানি না। জানতেই চাই না। র্যাডক্লিফ কমিশন হয়ত সে গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। শুধু র্যাডক্লিফ কমিশন নয়, এই উপমহাদেশ থেকে কত নদী, গ্রাম হারিয়ে গেছে ইতিহাসের স্রোতে। একজন প্রকৃত লেখকের কাজ তো সেই হারানো ইতিহাস অনুসন্ধান। এই গদাধর ও বিদ্যেধরকে সামনে রেখে লেখক হারানো ঐতিহ্য সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। এক উত্তর আধুনিক গল্পবলয় গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘদিন পরে সে গ্রাম , মানুষের সন্ধান পাবে কি করে ! ফলে লোককথা, কথকথা, লোকশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যায়। কুলদার গল্পে বৃদ্ধ গল্পবুড়ি বা গল্পবুড়ো থাকেন। যাঁরা জনজীবনের ইতিহাস জানেন। সেই সত্য-অর্ধসত্যের কাহিনিই তাঁরা উত্তর প্রজন্মের কাছে জানিয়ে যায়। বিনোদিনী ছোট সন্তানের মঙ্গলকামনায় সন্ধানে গিয়েছিলেন বিদ্যেধর ও গদাধরের। আজ বিনোদিনী বৃদ্ধ, নাতি নাতিনী সহ পরিবার। সে কাহিনিই হয়ত তিনি নাতি-নাতিনীদের মধ্যে সঞ্চার করে যাবেন। হয়ত কিছুটা কল্পনা মিশবে, কিছুটা বাদ যাবে, তবে এভাবেই কাহিনি সময় থেকে সময়ান্তরে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ আব্দুল হক আজ মৃত হয়েছেন, তাঁর শোনানো কাহিনিই হয়ত উত্তর প্রজন্ম বহন করে যাবে। সময় থেকে সময়ান্তরে যেতে কাহিনি গুলি হারিয়ে যায়, পরে অনুমানকে সামনে রেখেই আবার নতুন গল্পকথা গড়ে তুলতে হয়। এভাবেই দেশের জনজীবনের ইতিহাস বেঁচে থাকে। খোল-কর্তাল নিয়ে এক নবজীবনের ডাক দিয়েছিল চৈতন্য। এ গল্পে আছে গদাধর। প্রকৃত নাম গফুররুদ্দিন বা গদাধর। তবে কাহিনির সূত্র ধরে বিবিধ গদাধরকে আমরা পাব। আসলে এভাবেই লোকশ্রুতি গড়ে ওঠে, এভাবেই মিথ গড়ে ওঠে। স্মরণীয় ব্যক্তিকে সামনে রেখে বিবিধ গল্পগাথা রচিত হয়। তবে যা সত্য তা হল সে ব্যক্তির কার্যকলাপ। এই গদাধরকে সামনে রেখে গ্রামের দাঙ্গা রোধ করে দিয়েছিল হিন্দু মুসলিম মানুষ। শ্রেণি নয় একই অঞ্চলে টিকে থাকাই ছিল তাঁদের একমাত্র অধিকার। হিন্দু মুসলিমের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন মানুষ জয়ী হয়েছিল –
‘’দাঙ্গাকারীরা গান গাওয়া রত লোকজনের মুখোমুখি হয়েছিল। কারো কিছু হয়নি। গানের শব্দ এতো তীব্র ছিল যে তারা সহ্য করতে না পেরে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় তারা কোনো একজন লোকের মাথায় লাঠি মেরে গেছে। কারো কারো মতে সেই লোকটিই করতাল বাজিয়ে পথ দিয়ে গান গাইছিল। তার বাম হাত ছিল বাঁকা। এবং লোকটিকে আর কখনো দেখা যায়নি। কারো কারো মুখে শোনা গেল – লোকটির নাম ছিল গদাধর। লোকটি বিদ্যেধর চলে গেছে।‘’ ( তদেব, পৃ. ১৬১ )
এই নিরুদ্দেশ বৃত্তান্তের মধ্যেই আছে মিলনগাথা। কুলদা গল্পে সামাজিক শ্রেণির ওপর ভীষণ জোড় দেন। মানুষের অন্তর মননের রহস্য তুলে আনেন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি নয় তিনি বাঙালি মানুষের সংস্কৃতির কথা বলেন। এই মানুষগুলির মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। কিন্তু নিপীড়িত শাসক সেই বিভেদ গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তান শাসন পূর্ববর্তী সময়টিকে তিনি গল্পে ধরতে চেষ্টা করেন। মানুষকে দেখিয়ে দেন কী ছিল আমার দেশ, গ্রাম। অথচ সেই গ্রামের সংস্কৃতি কীভাবে পাল্টে গেল তাও দেখান। তিনি সংস্কৃতির ভিতর থেকে মানুষকে তুলে আনেন। তবে কাউকেই আঘাত বা ব্যঙ্গ করেন না। তিনি প্রকৃত সত্যটা দেখিয়ে দেন। সেখানেই তাঁর গল্পের যাবতীয় মুন্সিয়ানা। যেহেতু দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে তিনি গল্পগুলি লিখছেন তাই অনেক সময় অনুমান নির্ভর বাক্য রচনা করেন। এটা তাঁর গল্পরচনার টেকনিক বা কৌশল। সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। যাঁরা স্মৃতিতে জাতি, জনজীবনের ইতিহাস সঞ্চার করে চলেছেন। কিন্তু স্মৃতিতে মাঝে মাঝেই ধুলো পরে যায়। ফলে লেখক একটি ঘটনাকে সামনে রেখে অনেকগুলি কাহিনি গড়ে তোলেন। সেই ভিন্নধর্মী কাহিনি থেকেই তিনি গল্পের সত্যে উপনীত হন।
‘প্রস্তর জালাল’ গল্পে গোটা বাংলাদেশের শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। শুধু বাংলাদেশে নয় এই ভারতবর্ষেও শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের বদলে তৈরি করা হয় গোরু। নবগঠিত বাংলাদেশের কাছে সাধারণ মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সে দেশ ক্রমেই ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র ক্রমে অত্যাচার করেছে, নানা শাসন চাপিয়ে দিয়েছে, সব মেনে নিলেও যখন ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল তখন আর মেনে নিতে পারেনি –‘’লুল পুরুষ রাষ্ট্রে একটা ধর্ম দিল তখন থেইকা আর মানুষ থাকবার মঞ্চাইল না। সত্যি সত্যি গাইগরু হৈয়া গেছি। নাম দিছি গাভি-হল-জালালুদ্দিন।‘’ ( তদেব, পৃ. ১৭৪ ) জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে করে তোলা হয়েছে ধর্মনির্ভর। চারিত্রিক দিক থেকে লম্পট লোকরাই রয়েছে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে। যেখানে জীবনের পাঠ নেই, জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পাঠ নেই, পৃথক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই সে শিক্ষা ভিত্তিহীন। সেখানে থিসিসের কোন মূল্য নেই। যে ছাত্র শাসন ব্যবস্থা, ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বে মুক্তমনা মানুষের কথা বলতে পারে না, যা চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না সে শিক্ষা ভিত্তিহীন। বংলাদেশের রাষ্ট্রয় পরিকাঠামো এই পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে, সেখানে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই, ফলে মানুষ ক্রমেই গোরুতে পরিণত হয়েছে –‘’আমরা লোকজনরে গরুই বানাইতে চাই। মানুষ দিয়া কাম নাই।‘’ ( তদেব, পৃ. ১৭৩ )
তিনি গল্পে গাছ লাগান। গাছে ফুল ধরে, ফুল ধরে। গল্পের সত্য প্রতিষ্ঠা করতে আবার গাছ উপড়েও ফেলতে হয়। ‘দি জায়েন্ট গ্রেফ’ গল্পে তিন দেশের তিন মানুষের চেতনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। লাউ গাছকে সামনে রেখে তিনি জীবনের সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। গাছই যেন জীবনের প্রতীক, ভালোবাসার প্রতীক। বরিশালের কথক ও স্ত্রী, স্প্যানিস বেনী ও ক্যালিফোর্নিয়ার এলা বার্টন। কথকের স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল লাউ পাতা দিয়ে কই মাছ খাওয়ার বাসনা। এ উদ্দেশ্যেই লাগানো হয়েছিল লাউ গাছ, তা পরিচর্চা করত সিকিউরিটি বেনী, আর লাউ গাছকে মনে হয়েছে আঙুর গাছ এলা বার্টনের। এ গাছকে সামনে রেখে এলা ফিরে গেছে নিজের স্বামীর কথা, নিজের যৌবনের প্রেমে, গল্পকথকের স্ত্রীর মনে বাসনা লাউ গাছ বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু গাছের প্রতি অনন্ত মায়া বেনীর। আসলে একজন মানুষ সন্তানসম স্নেহে গাছ বড় করে তোলে। এক অপার ভালোবাসা গাছের প্রতি। তাই যেদিন লাউ দিয়ে উৎসব হবে তার আগেই বেনী লাউ গাছ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এ গল্পে আছে হারানো সংগীতের কথা, বাইবেলের প্রসঙ্গ। বাংলা গল্পে ভিন্ন ভূগোল এনে উপস্থিত করেন লেখক। তবে দেশের শেকড়কে সামনে রেখেই তা বিবর্তিত হয়। পরবাসে থেকে লাউ শাক খাবার বাসনা থেকে ভিন্ন শ্রেণির মানুষকে তিনি যেভাবে মিলিয়ে দিলেন তা বড় বিস্ময়কর। পৃথক দেশের, গোত্রের মানুষ হলেও জীবনের সত্য যে একই ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত তা লেখক দেখিয়ে দেন। ‘পাতা ঝরার গান’ গল্পে ছবি আঁকেন। সে ছবি নৈঃশব্দের বর্ণমালা। মৃদুমন্দ বাতাসে সে ছবি যেন ভেসে যায়। সেখানেও এক গভীর সত্য থাকে। চেলসির জীবন যন্ত্রণার কথা। যে জীবনে ভালোবাসা পায়নি। পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে নিজের আক্ষেপ শুনিয়ে গেছে। ‘’পাতা ঝরার শব্দ। মাটির শব্দ। জলের শব্দ। নৈঃশব্দের শব্দ।‘’ সে চিত্র তিনি এঁকে যান। কলুদার গল্প ভীষণ ভাবে কাব্যময়। বাক্যের জাদুতে তিনি পাঠককে মুগ্ধ করেন। তিনি কখনোই বড় বা জটিল বাক্য রচনা করেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যময় বাক্যে তিনি জীবনের গভীর সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।
‘ফ্লাই উইদাউট উইং’ গল্পে পরাবাস্তব, জাদুবাস্তব, মায়াবাস্তব মিলে মিশে আছে। একধিক চরিত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের সত্য আবিষ্কার করেছেন। আর তা মিলিয়ে দিয়েছেন পরী, ছায়া দ্বারা। বিভিন্ন পেশার একাধিক চরিত্র মিলিত হয়েছে পার্কে। কেউ ছবি আঁকে, কেউ গান গায়, কেউ সময় কাটাতে, কেউ প্রেম করতে এসেছে। প্রত্যেকেই সৃষ্টিশীল মানুষ। এঁদের নীরবতা ভেঙে দিয়েছে পুলিশ এসে। আর অলক্ষ থেকে তিনি পরীর গল্প লিখে চলেন। বাস্তব-অবাস্তবে মিলিয়ে তিনি জীবনের গভীর তলদেশে পৌঁছে যান। পুলিশ সর্বদা মানুষকে লক্ষ রাখে, সর্বত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। এমনকি বৃদ্ধের দাড়ি দেখে সন্দেহ হয়েছে, খুঁজে পাননি কোন পরিচয় পত্র। কানা পুলিশ, ধলা পুলিশকে সামনে রেখে তিনি বাস্তব জীবনের গভীরে প্রবেশ করে যান। পুলিশও উষ্ণতা খোঁজে, অথচ পার্কে তাঁরা এসেছিল প্রেমিকাদের ধরতেই। একাধিক চরিত্রকে সামনে রেখে দৃশ্যের গতিতে গল্প এগিয়ে যায় –
‘’পরীটিকে ঘিরে গোলাকার পাকা চত্বর। বারোটি কাঠের বেঞ্চ। কাঠের পিঠ ঠেকনা। ল্যাংরি থাবার উপরে ঘুমিয়ে আছে। তার মাথার উপরে ঝুঁকে আছে জেনিফার। জোসেফ গীটার বাজিয়ে গান গাইছে। লোপেজ কাগজের উপর খসখস করে একটা পাতার ডিজাইন আঁকছে। জারমিনা ঘাসের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। লাইটারটা তাকে খুঁজে পাতেই হবে। আর একজন বুড়ো লোক বেঞ্চির পিঠ-ঠেকনায় মাথা হেলিয়ে বসে আছে।‘’ ( তদেব, পৃ. ২১২ )
কুলদা রায় বাংলা গল্পে নিজেই একটি ধারা আবিষ্কার করে নিয়েছেন। ‘বৃষ্টি চিহ্নিত জল’ গল্পগ্রন্থের পর এ গ্রন্থ পড়লে পাঠকের সে ধারণা স্পষ্ট হবে। সুদূর বিদেশে বসেও তিনি নিজের শেকড়ের গভীরে যেমন প্রবেশ করেছেন তেমনি বিদেশের পটভূমিকায় লেখা গল্পেও পরী, ছায়া, গান প্রবেশ করিয়ে তা জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর ভাষাটা স্বচ্ছ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মতো তাঁর ভাষা যেন প্রবাহমান। বড় মায়াবি ভাষায় তিনি কথা বুনে চলেন। এ ভাষা যেন হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা না থাকলে এমন আশ্চর্য ভাষা বুঝি সম্ভব নয়। তাঁর গল্পের একটা আশ্চর্য বাতাবরণ আছে। যা তিনি পরী দ্বারা বৃত্ত করে রাখেন। তাঁর গল্পে মানুষ পরী হয়ে যায়। তিনি পরী মানুষের গল্প লেখেন। তাঁর চরিত্র বলে ওঠে ‘হা কৃষ্ণ’। দেশের জন্য মানুষের যে বেদনা তা তিনি বড় করে দেখান, বাঙালির অখণ্ড সংস্কৃতির কীভাবে বিভাজন ঘটে গেল তার রহস্য উন্মোচন করে দেন। তাঁর গল্প বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আমেরিকায় উড়ান দেয়। তৃতীয় বিশ্বের ভূগোলকে তিনি নতুন করে দেখিয়ে দেন। বাঙালি পাঠকের কাছে তা নতুনত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়।
বইটি পাওয়ার ঠিকানা
মার্কেজের পুতুল
কুলদা রায়ের তৃতীয় গল্পের বই
প্রকাশক :
সোপান
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (033)2257-3738/ 9433343616/9836321521
নালন্দা প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৯৫৯০৬১৭
বাতিঘর।। ঢাকা।
এছাড়া পাওয়া যাবে ঃ রকমারী অনলাইন অর্ডার লিংক
https://www.rokomari.com/book/195935/marquezer-putul-o-onnanya-golpa





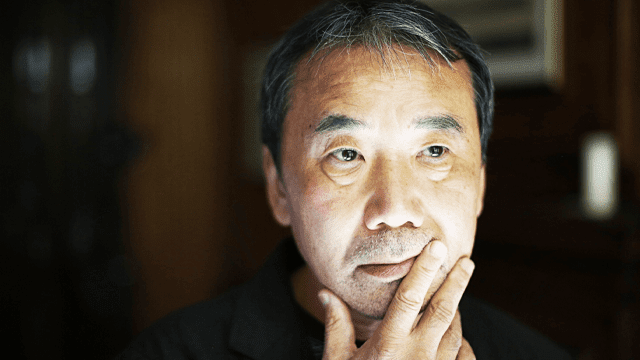







0 Comments