কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো আলাপ-পরিচয় ছিল না। ২০১৪ সালে আমার এক বন্ধু তাঁর ফোন নম্বর দিলেন। একদিন সাহস করে ফোন করলাম। তিনি ধরলেন। আমাকে তিনি চেনেন না। কোনোদিন নামও শোনেননি আমার। আমার সঙ্গে চেনা মানুষের মতোই ঘণ্টা দেড়েক কথা বললেন। অচেনা-অজানার গণ্ডিটা তিনি ঘুঁচিয়ে দিলেন।
সে সময়ে গল্পপাঠে দেশভাগের কথাসাহিত্য নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বেশ কিছু প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের ভাবনাগুলো সাক্ষাতকার আকারে নিচ্ছিলাম। দেশভাগ নিয়ে হাসান আজিজুল হকই লিখেছেন সবচেয়ে বেশী। লিখেছেন প্রথম উপন্যাস আগুনপাখি। এটা দেশভাগেরই মহাআখ্যান।
পরিকল্পনা ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ এই আলাপচারিতা হবে। প্রতি রবিবারে--তাঁর সময় হবে বেলা এগারোটায়। আর আমার রাত একটায়। প্রথম সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরে তিনি বাথরুমে পড়ে যান। পা ভেঙ্গে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকেন। সুস্থ হওয়ার পরে আবার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর টাইমটেবিল কিছুটা পালটে গেছে ততদিনে। আর দীর্ঘ সময় ধরে ফোনে তাঁকে পাওয়া সম্ভব হয়নি। আমি চেষ্টা করেছিলাম অন্যদের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ করার। কিন্তু নানা কারণে সেটাও সম্ভব হয়নি। ফলে আমার কাজটি সম্পূর্ণই রয়ে গেল। এটা আমার একটা জীবনব্যাপী দুঃখের বিষয়ও হয়ে থাকল।
ফোনে হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে এই আলাপচারিতা রেকর্ড করে নিয়েছিলাম। পরে সেটা টাইপ করে ফেলি। এটা এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।
সাক্ষাতকারের শুরুতে তাঁর আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পটি নিয়ে কিছু ভাবনা এক্সযুক্ত করেছি। তারপরে মূল সাক্ষাৎকার বা আলাপচারিতা পত্রস্থ হলো।
১.
আমার সবচেয়ে প্রিয় গল্পটির নাম আত্মজা ও একটি করবী গাছ। প্রিয় গল্পকার হাসান আজিজুল হক। এই রকম গল্প একদিনে লেখা যায় না। একা লেখা যায় না। বংশপরম্পরায় লিখতে হয়। একটি জনপদের সবাই মিলেই লেখেন।
এই গল্পটি যখন আমার মুদিদোকানী বাবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়তেন--স্পষ্টভাবে দেখতে পেতাম, বাবার শ্বাস ঘন হয়ে পড়ছে। নাকের ডগা লাল হয়ে উঠেছে। পড়া শেষ হলে দপদপিয়ে মুদিখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। কোন কথা বলতে পারছেন না। পারলে রাস্তাটিকে ধরে আকাশের ওপারে ছুড়ে মারতেন।
সে সময় আমাদের পাড়ায় কয়েকটা করবী ফুলের গাছ ছিল। ফুলগুলো লাল হত না—হলুদ হয়ে ফুটত। ফুলটির নাম যে করবী এটা কেউ জানত না। সবাই বলত কলকি ফুল। এই কলকি ফুল তুলতে নেই।
একদিন আমার মেজোদিদি একটি কলকি ফুলের গাছ এনে আমাদের মন্দিরের সামনে লাগিয়েছিল। গাছটি তুলে ফেলেছিল আমার মা। রেগেমেগে বলেছিল, সংসারে কি অ্যালফ্যাল আনতি চাও নাকিরে মাইয়া?
এরপর গাছটি বহুদিন পড়েছিল নিমতলার পাশে। সেখান থেকে বেলতলার নিচে। শুকিয়ে ঠ্যানঠ্যানে হয়ে পড়েছিল। তারপর পুকুরপাড়ে ছুড়ে ফেলেছিল।
এই পুকুরপাড়ে আমাদের পাড়ার জেঠীকাকীরা প্রতিদিন সকালে থালাবাসন মাজতেন। মাজতে মাজতে তাদের মাজা ধরে আসত। জল দিয়ে চোখ থেকে জল মুছে দিতেন। মুখে জল নিয়ে কুলকুচা করে উঠে পড়তেন। মাঝে মাঝে সেই কুলকুচা এসে পড়ত পাড়ের দিকে। আর সেই থেকেই আমাদের কলকি গাছটি নড়ে চড়ে উঠেছিল। আমাদের অবাক করে দিয়ে তার শুকনো ডালে পাতা এসেছিল। শেকড় জেগেছিল।
আমার সেজো বোনটি সেই মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া কলকি গাছটি মন্দিরের পাশটিতে আবার লাগিয়ে দিয়েছিল। মা যখন গাছটিকে তুলে ফেলবে বলে ডাল ধরেছে, সেই সময়ে উঠোনে ঢুকছেন কুসুমদিয়ার ফকির। তিনি ডেকে বলছেন, গাছটির নাম করবীগাছ। সেই থেকে আমাদের কলকি ফুল করবী হয়ে আমাদের উঠোনে ফুটেছিল।
২.
সে সময়কালে হাসান আজিজুল হকের বুড়োটির মত বেশ কয়েকজন বুড়ো খুব ভোরে হাঁটতে বের হতেন রাস্তা দিয়ে। এর মধ্যে একজন ছিলেন কাশেম রেজা। চোখের ডাক্তার। তিনিই আমাদের জলের তলা থেকে ভেসে ওঠা খুদে শহরের কবিকাকা। তিনি পূজোর সময়ে দুর্গামণ্ডপে কবিতা পড়তেন। শহীদ মিনারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে কাগজে কবিতা লিখে বিলি করতেন। তাঁর মুখ ছিল প্রাচীন ঋষিদের মত সৌম্য। আর শিশিরের মত মায়াময়। তিনি একদিন ভোরবেলা সবাইকে ডেকে তুললেন। বললেন, এই করবী গাছটি নিয়ে আমি একটি কবিতা লিখব। তোমাদের শুনিয়ে যাব।
তিনি কবিতা শোনাবেন এই আশায় আমরা তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। পাশে কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়। ছবি তুলে কেউ বেরিয়েছে ছবিঘর থেকে। তার চুলে তখনো টেরিকাটা। মকলু ভাই হৈ হৈ করে যাত্রাদলের কথা বলছেন। পথচারিরা আমাদের পাশ হেঁটে যেত। কেউ কেউ গান গাইত, অনেক সাধের ময়না আমার। ময়নাটি বাঁধন কেটে যেত। তারা কল্পনা সিনেমা হলে রাজ্জাক কবরীর ময়নামতি সিনেমাটি দেখে যাবে।
কবির ঘরটি ছিল কালিবাড়ির পুকুরের উপরে। মাচা থেকে মাছ ধরা যেত। আমাদের বন্ধু পল্টু পুকুর থেকে জল তুলে ঠিক পুকুরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল সারত। বলত, জানিস, পৃথিবীতে কেউ জলের উপরে হাঁটতে পারে না। আমরা পারি। কবি কাশেম রেজা আর তার ছেলে কবি রেজা পল্টু প্রতিরোজ জলের উপরে হেঁটে বেড়াত। আমরা দেখতে পেতাম—কবি তার টেবিলে ঝুঁকে কবিতা লিখছেন। চোখের উপর থেকে চশমাটি নাকের উপরে ঝুকে এসেছে। কাঁচাপাকা চুল। আর বাদশাহী দাড়ি। আমরা অপেক্ষা করতাম এই কবি বুড়ো হওয়ার আগে করবী গাছটি নিয়ে কবিতাটি লেখা শেষ করবেন। আমরা শুনতে পাব। পল্টু তখন বলেছিল, কষ্ট কবিতা থেকে জন্ম নেয়। কী কষ্ট জানিনা। তাহলে কি করবী কোনো কষ্টের নাম?
৩.
পান্নু স্যারের বাসার সামনেই বাজার বসে। শুক্রবারে আর মঙ্গলবারে দূরের হাটুরেরা এসে কবির হোটেলে ভাত খেয়ে যায়। খেতে খেতে লাউগাছের গল্প করে। রায়েন্দাধানের পুড়ে যাওয়ার জন্য হাহাকার শোনায়। মাঝিগাতির বিলে শালুকধরার খবরাদি জানিয়ে যায়। রাধুনে মহিলাটি এসে বলে—বাবা, আপনেও চাইট্টা খাইয়া লন। এ সময়ই পান্নু স্যার তার দ্বিতীয় বিবির জন্য ম্যাকবেথ পড়ছেন। আর বাজার ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে।
কবি আমাদের উঠোনে ভোর ফোটার আগেই ঘুরে যেতেন। তখন তার ঘরে মোজো মেয়েটির ছেলেমেয়েরা এসে পড়েছে। কেউ কেউ বারান্দায় ঘুমোয়। কেউ কেউ রোগীদেখার ঘরে। কোকো আপা মন খারাপ করে ইস্কুলে পড়াতে যান। সেকো আপার সঙ্গে দেখা হয় না। রেখা আপা একদিন বিপ্লব হবে বলে ছুটে বেড়ান এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। আর শোনা যায় কচি আপা কবিতা লিখছেন। ঢাকায় কবিতা ছাপা হচ্ছে। করবী ফুলকে নিয়ে কেউ কবিতা লেখেনি। আমরা জানি আমাদের শহরের সত্যিকারের কবি কাশেম রেজাই লিখবেন কবিতাটি। আমরা শুনব। শুনলে আমাদের মন ভালো হয়ে যাবে। এইহেতু আমাদের উঠোনে একটি গাছেই কখনো রক্তের মতো লাল ফুল ফুটত। কখনো শ্বেত পাথরের মত সাদা ফুল। কখনো আমার মায়ের চুলের মতো কালো কালো ফুল। আবার বাটা হলুদের মত হলুদ হলুদ। কবিতা এই লাল, সাদা, কালো আর হলুদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। চারিদিকে ফেটে পড়বে।
৪.
এইভাবে আমাদের কবি একদিন বুড়ো হতে হতে তার লেখার টেবিল হারিয়ে ফেললেন। সেখানে বসেছে ক্যারামবোর্ড। আর কবিতার খাতার বদলে মাসুদ রানা। অমিতাভ বচ্চন—আখেরি রাস্তা। ইয়াহ-ঢিসুম ঢুসুম।
কবি আমাদের বটতলায় আসেন। হাতে ময়ূরমুখী লাঠি। মাথায় সাদা টুপি। তার চোখের মধ্যে অনেকগুলো কাক কা কা করে ওড়ে। পাখা ঝটপটায়। মা দুটো মুড়ি খেতে দেয়। একখণ্ড নলেন গুড়। কাসার গ্লাসে জল। কবির হাতে জলের গ্লাস। তিনি বলেন, কবিতা লেখা হয়েছে।
তিনি ঢকঢক করে জল খেলেন। তারপর পড়লেন 'একটি বাবা, তার মেয়ে আর একটি একটি করবী গাছের' কবিতা। বাবা বারান্দার ঘরে বসে থাকে। তার ঘরে গ্রামের ছেলেরা আসে। দুটো একটা টাকা দেয়। ভেতর ঘরে তার মেয়েটির শাড়ির খসখসানি কানে আসে। বুড়ো খুক খুক করে কাশে। আর বাইরে সেই করবী গাছ বেড়ে ওঠে। বুড়ো শোনায় করবী ফলের মধ্যে মারাত্মক বিষ থাকে।
আমরা কবির কণ্ঠে শুনি সেই বিষের গল্পটি। আর কিছু নয়। এই বিষময় করবী গাছটি আমাদের মন্দিরে বেড়ে ওঠে। বাতাসে তারা চিকন চাকন পাতাগুলো দোলে। মা রান্না ঘর থেকে গরম ভাতের ফ্যান গাছটির গায়ে ফেলতে ফেলতে থেমে যায়। এ সময়ই কবি জলের গ্লাসটি আবার ঠোঁটে চেপে ধরেন। তার আবার জল পিপাসা জেগেছে। কিন্তু গ্লাসটি শূণ্য। আমাদের উঠোনে করবী ফুল ফেটে পড়েছে।
------------------------------------------------------------------------
১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
রাত ১০৩০, নিউ ইয়র্ক থেকে ফোন করি। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯.৩০। হাসান আজিজুল হক স্যার সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। বিছানায় বসেই ফোনে কথা বলতে শুরু করলেন।
------------------------------------------------------------------------
কুলদা রায় :
আপনি দীর্ঘদিন ধরে শুধু ছোটো গল্পই লিখেছেন। উপন্যাস লেখেননি। কেনো শুধু গল্পের মধ্যে থাকলেন?
হাসান আজিজুল হক :
এই প্রশ্নটা অনেকদিন ধরে মানুষ করে। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, আমি শুরু থেকে গল্প নয়—উপন্যাস লিখতেই চেয়েছি। ছোটগল্প লিখে যে আমার খ্যাতি হবে সেটা আমার অনুমানে ছিল। যেকোন লেখকেরই লেখার জায়গাটা ঠিক হতে একটু সময় লাগে। সেই জন্য তারা শুরু থেকে গল্প উপন্যাস কবিতা নানান কিছু লেখেন। আমি উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করেছিলাম ১৯৫৭ সাল থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ১৯৫৪ সাল থেকে ইচ্ছে ছিল লিখব। ১৯৬০ সালে এসে আমি লিখে ফেলেছি শকুন নামে একটি গল্প। সবাই দেখলেন। পড়লেন। কেউ কেউ খুশি হলেন। কেউ হলেন না। সবাই বললেন, সাহিত্যের নতুন লোক। তারপর আমি গল্পই লিখেছি। তবে আমি খুব বড় উপন্যাস লিখতে চেয়েছি সব সময়। এটা আমার মনের মধ্যে সব সময়ই ছিল।
এখন দুএকটা লম্বা লেখা বেরচ্ছে। সেটা উপন্যাস কিনা জানিনা।
কুলদা রায় :
আপনি আত্মজা ও একটি করবী গাছ নামে গল্প লিখলেন…
হাসান আজিজুল হক :
১৯৬৭ সালে লিখেছি এই গল্পটি।
কুলদা রায় :
সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। গণভ্যুত্থান ঘটার প্রস্তুতি পর্ব চলছে।
হাসান আজিজুল হক :
তখন আমার একটি বইও বেরিয়ে গেছে। আমার প্রথম বই বেরিয়ে ১৯৬৪ সালে।
কুলদা রায় :
এই সময়কালে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগেছে। পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি আইন করেছে। এই আইনের আওতায় রাষ্ট্রের মদতে হিন্দু সম্প্রদায় বিষয়-সম্পত্তি হারাতে শুরু করেছে। একটি করবী গাছের কাহিনীতে বুড়ো হিন্দু লোকটা দেশ ছাড়েনি। হয়তো ছাড়ার উপায় নেই। দিন দিন গরীব হয়ে পড়ছেন। এক ধরনের শ্বাসরোধী বেদনাবোধ টের পাচ্ছি তার মধ্যে। আপনি এই বেদনাটা কঠিনভাবে লিখেছেন। এমন কঠিনভাবে যে আজও সেটা শুনতে পাই। সেটা চলছে। থামেনি।
হাসান আজিজুল হক :
আমি কখনোই ১৯৪৭ সালের ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশভাগটিকে মেনে নেইনি। সেসময়ে বাংলাকে যে পশ্চিম বঙ্গ আর পূর্ব বঙ্গ নামে দ্বিখণ্ডিত করা হল—আরো একবার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৫ সালে—সেটা ১৯৪৭ সালে হয়ে গেল। এ ঘটনায় আমার কখনোই সমর্থন ছিল না। আমি সব সময়ই মনে করেছি—সাঁতার যদি দিতেই হয় তাহলে দীঘিতে সাঁতার দেওয়াই ভালো। পুকুরে নয়। আমরা স্বাধীনতা চাই—কিন্তু খণ্ডিত একটি জায়গার জন্য চাইতে হবে—তার জন্য সম্প্রদায়গত একটি বিভক্তিকে কারণ হিসেবে দেখানো হবে—আমি কোনো দিনই মেনে নিতে পারিনি। আমি আগাগোড়া এর বিরোধিতাই করেছি।
আমরা পশ্চিম বঙ্গ থেকে এসেছি। উব্দাস্তু। আমরা যে ভুখণ্ডে ছিলাম সেইখানে আমাদের বিকাশ হচ্ছে না। একটা আতঙ্কে আছি। আবার দেশ ছেড়ে যাব। যেতে ইচ্ছে করে না। একটা নিরাপত্তার অভাব বোধ আছে—আতঙ্ক আছে। যাই যাই করেও যাওয়া হচ্ছে না। একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এই কমিউনিটি এটা ভোগ করেছে ১৯৪৭ সাল থেকে। হিন্দু কমিউনিটি অপেক্ষাকৃত বেশি ভোগ করেছে। এটা জীবনের জন্য বড় কষ্টদায়ক ঘটনা হয়ে উঠেছে। এ জন্য আমি ঐ আত্মজা ও করবী গাছ গল্পটি লিখেছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা অংশের যে আতঙ্ক সেটা এসেছে এই গল্পে। ওখান থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যেও আতঙ্কটা ছিল। এখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে আরো বেশি ছিল।
কুলদা রায় :
সে সময়ে পাকিস্তানে তমুদ্দিনপন্থীরা মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণের একটা পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে নেমেছিল। কিছু কিছু লোকজনও এই পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে ভাষা সংস্কারের চেষ্টা হিসেবে শব্দের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন তারা। জোর করে অপ্রচলিত আরবী-উর্দু শব্দ বাংলা ভাষায় গায়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। কিন্তু আপনারা সে সময়েই খুব নিটোলভাবে জীবনের সাদামাটা আখ্যান লিখতে শুরু করলেন সাধারণ মানুষের ভাষায়। চেনা শব্দে লিখলেন। শুদ্ধু বাংলা ভাষায় লিখলেন। প্রমিত ভাষায় লিখলেন। কোনো চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা আপনারা আমলে নিলেন না। নিজের ভাষার দিকে, সংস্কৃতির দিকে, জীবনবোধের দিকে সবার চোখ ফেরালেন। এটা ছিলো এক ধরনের প্রতিবাদ।
আপনারা কি সে সময়ে এই কাজগুলো করতে কোনো সমস্যা বোধ করেছিলেন? কোনো চাপের মুখে পড়েছিলেন?
হাসান আজিজুল হক :
আদৌ নয়। আমরা কি লিখব না লিখব তা আমরাই ঠিক করেছি। ১৯৫৪ সালে আমরা পশ্চিম বঙ্গ ছেড়ে এদেশে এসেছি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছে। সে সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গে থাকাকালে কিছুই জানতাম না। এখানে এসে এরকম একটা অবস্থা দেখলাম। এ ধরনের চাপিয়ে দেওয়ার কাজের আমি সব সময়ই বিরোধী। আমি লিখতে চেয়েছি নিজের ইচ্ছাতে। কারো চাপিয়ে দেওয়া কাজ করব—এটা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভাষাটাকে সংস্কার করতে কোনো সম্প্রদায়ের আদলে করতে হবে –এইসব ব্যাপার মনের মধ্যে কখনোই ছিল না। ফলে আমি নিজের লেখার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি—এই ধরনের কোনো ব্যাপারেই আমি কর্ণপাত করিনি। বরং সে সময়ে হিন্দু সম্প্রদায় নিয়ে—যে কোনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে—যে কোনো সম্প্রদায়কে নিয়েই আমি সহজাতভাবে লিখেছি। আমি তাদের ভাষা নিয়ে—জীবন নিয়ে নানা রকম কাজ করেছি।
কুলদা রায় :
তমুদ্দুন পন্থীরা যেরকম পরিকল্পনা করে ভাষা-সংস্কৃতি পালটে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল—আপনারাও কি সে সময় পরিকল্পনা করে প্রচলিত বাংলা ভাষায়ই লিখতে শুরু করেছিলেন?
হাসান আজিজুল হক :
না। সে ধরনের পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। এ ধরনের পরিকল্পনা আমাদের থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশ শোষিত হচ্ছে—তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ভাষাকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে—এগুলো নিয়েই আন্দোলন ছিল। ১৯৬৭ সালে পর্যন্ত এরকমই ঘটেছিল। আমাদের লেখকদের এরকম করে লেখার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আররতলা নিয়ে যে ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল—সে রকম করে লেখকদের কোনো দৃশ্যমান পৃথক আন্দোলন ছিল না। দরকার হয়নি। আমরা তো সেদিন পাকিস্তানীদের কোনো তোয়াক্কাই করিনি। তোয়াক্কা করলে তো তাদেরকে প্রতিরোধের চেষ্টা করার দরকার হয়। আমারা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই লিখেছি। নিজেদেরকে লিখেছি বলেই পাকিস্তানীদের তৎপরতায় বিচলিত হইনি।
কুলদা রায় :
আপনি কি রাজশাহীতে সে সময় শিক্ষক হিসেবে ছিলেন?
হাসান আজিজুল হক :
আমি তখন রাজশাহীতে একটা সান্ধ্যকালীন কলেজে শিক্ষকতা করেছিলাম বছরখানেক। ১৯৬১ সাল থেকে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল খুলনার ফুলতলাতে। এভাবে এদেশের মানুষ হয়ে যাওয়াটা আমার রক্তের মধ্যেই ছিল। আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।
কুলদা রায় :
১৯৪৭ সালের আগে দুই বঙ্গ যখন এক্ত্রে ছিল তখন কি আপনি বা আপনারা মনে করতেন যে, পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের সংস্কৃতি আলাদা?
হাসান আজিজুল হক :
আমার মনে হয়েছে—সে রকম যে ছিল না তা নয়। তবে আমি এ সমস্তে বিশ্বাসী ছিলাম না—কোনোদিনই নয়। আমি দাবী করতে পারি আমি সম্পূর্ণভাবে একজন মুক্ত মানুষ। সেটা ধর্ম সংস্কারসম্প্রদায় –এর কোনোটাই আমি বিবেচনার মধ্যে রাখি না। কোনোটার প্রতিই আমার কোনো পক্ষপাত নেই।
কুলদা রায় :
কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন দেশটা ভাগ হয়ে গেল—যদিও আপনি ১৯৫৪ সালের দিকে এপারে চলে এলেন, তারমানে দেশভাগের আরো ৭ বছর পরে চলে এলেন। সেই ১৯৪৭ সালে অনেকেই চলে গেলেন বা পরেও অনেকে চলে গেলেন ঐ বঙ্গে। এই যে দেশভাগ—দেশভাগের যে বেদনাটাটা এটাতো প্রবলভাবে মানুষের বুকের মধ্যে বাজল, আপনি এপারে চলে এলেন। অমর মিত্ররা সাতক্ষীরা থেকে চলে গেলেন। নরসিংদি থেকে চলে গেলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাদের সাহিত্যে ব্যাপকভাবে এই চলে যাওয়ার বেদনাটা বাজে। সেই কষ্টের-বেদনার ভারটা এখনো তাদের মধ্যে দেখতে পাই।
হাসান আজিজুল হক : শুনুন। আমি শহরের কোনো লোক ছিলাম না। আমি পশ্চিম বঙ্গের একটি হিন্দু প্রধান গ্রামের লোক। এই গ্রামের ১০% মুসলিম। বাকীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। সেইখানে আমি বড় হয়েছি। আমরা সে সময়ে এদিককার কোনো খবর টবর পাইনি। বাল্যকালে এইসব বিষয়ে আমাকে স্পর্শ করেনি। আমার জন্ম ১৯৩৯ সালে। এ বঙ্গে যখন আসি তখন আমার বয়স মাত্র ১৪-১৫। আমার যখন বয়স ৪-৫ তখন তো আমার কিছুই মনে থাকার কথা নয়। তখন তো আমি বালকেরও কম বয়েসী। আমি ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। আমার কাছে তাই এইসব অন্যকিছু। কোনো পার্থক্য টার্থক্য আমার কাছে কখনো ধরা পড়ে নি। আমরা আগে যেমন ছিলাম—তেমনিই আছি। কোনো তফাত কখনো অনুভব করিনি। মাঝখান থেকে একটু হারিয়ে গিয়েছি। এদের খাওয়া দাওয়া একটু পরীক্ষা করে দেখেছি—কেমন হয় আর কি।
কুলদা রায় :
তার অর্থ দেশভাগের বিষয়টা আপনার মধ্যে তেমনভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। করার বয়সে আপনি ছিলেন না। আপনি কি মনে করেন আপনার বাবা-মা বা আপনার যারা সিনিয়র তাদের মধ্যে কি দেশভাগের কোনো বেদনা ছিল?
হাসান আজিজুল হক :
সেটা এতোই দূরত্বের যে আমাদের অঞ্চলে আর কি সে সব নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারিত হতে শুনিনি। আমি তো সেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ওইপারের গ্রামটি ছিলাম। সেখানে এধরনের কোনো কথা আমি শুনিনি। কখনো রায়ট ফায়ট হয়েছে। তা সামান্যই। সাধারণ বিষয় নিয়ে একটু রেশারেশি। সেটা নিয়ে দেশ ছাড়তে হবে এইভাবে কেউ রিয়াক্ট করেনি। কারো মনেই কখনো উঁকি দেয়নি যে আরে ওই দেশে চলে গেলে আমরা বোধ হয় আরো ভালো থাকতে পারব। ওই দেশ বলে একটা দেশ আছে সে রকম কোনো ধারনাই তো মানুষের মধ্যে ছিল না। মানুষ বড় বিচিত্র। প্রান্তিক মানুষ এভাবেই নিজেদের ভাবনাটি নিয়েই থাকে। তাদের ঘাড়ে যে বিষয়গুলো চেপে আছে সেগুলো নিয়েই তারা ভাবে। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। দেশ ভাগ হয়েছে। মুসলমানদেরর জন্য আলাদা দেশ হয়েছে। সেখানে মুসলমানরা কেবলমাত্র থাকবে—এই সব বিষয় তাদের মধ্যে ছিল না। হয়তো শহর এলাকায় ছিল বা থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামে এসব বালাই ছিল না। আমি এসব একেবারেই দেখিনি। হিন্দুদের মধ্যেও দেখিনি—মুসলমানের মধ্যেও দেখিনি।
কুলদা রায়:
সে সময়টা বা আপনি যে পরিবেশে ছিলেন বা পরিবারের মানুষ –তার মধ্যে এই ধরনের বিভাজন বা ভেদ চিন্তা আসেনি। কষ্ট বা বেদনাবোধ পাওয়ার মত ঘটনা ছিল না। এটা থেকে আপনারা অনেকটা মুক্ত ছিলেন।
হাসান আজিজুল হক :
বলা যায়। মুক্তই ছিলাম।
কুলদা রায় :
এই মুক্তবোধের কারণেই আপনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বোধ আপনার মধ্যে সহজাতভাবে এবং প্রবলভাবেই আছে। বিশেষ করে যে প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে আপনার অবস্থান ছিল তাদের মধ্যে যে সম্প্রীতি দেখেছেন তা আপনি লিখছেন। আবার কোলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এপারে চলেন তাদের সাহিত্যে কিন্তু এই চলে আসার বেদনা বা দেশভাগের বেদনাটি সেভাবে আসেনি।
হাসান আজিজুল হক :
আসলেই তাই। অনেকদিন ধরেই আমি এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। যেমন মাইনোরিটির কোনো মাইন্ড থাকে না তেমনি এদের সংখ্যাটি তো ওপারে তেমন বেশি ছিল না। বৃহদংশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমি দেখেছি-১৯৫৪ সালের আগে যখন মাঝে মাঝে আমি আসতাম এদেশে কলেজে লেখাপড়া করার জন্য, সে সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছি ট্রেন ধরার জন্য। সেই প্লাটফর্মে দেখেছি কতো পরিবার সেখানে রয়েছে। তাদের পরিবার পরিজনের নানান রকমের জৈবিকতা—সব কিছু খোলা আকাশের নিচে পড়েছিল। আমি ট্রেনে উঠতাম লোকের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে। মাটিতে পড়ে যাওয়া মানুষ। এমনভাবে হাঁটতাম যেন কোনো মানুষের গায়ে পা না পড়ে। এসব দৃশ্য আমি দেখেছি। কাজেই এটা তো মনের মধ্যেই কাজ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। আমার অভিজ্ঞতায় সে রকম তিক্ত বিষয় নেই। তবে লেখক, জানেন তো, সব কিছুকে নিজের মত গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে নেয়। ঘটনার অংশ হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলো তৈরি করে নেয়। কথাগুলো তৈরি করে নেয়। সেটা তার বিশেষ একটা লক্ষ্য। সেটা তিনি পারেন। সেটা তার ক্ষমতা। মানে সমব্যাথী হওয়াটা বা রাষ্ট্রিক দুর্যোগটাকে প্রায় ব্যক্তিগত করে তোলার ক্ষমতাটা সাহিত্যের লেখকদেরই থাকে। আমার ধারণা তাই।
কুলদা রায় :
পশ্চিম বঙ্গের তুলনার বাংলাদেশের মানুষদেরকে অনেক বেশি রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে বা হয়। প্রাকৃতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক নানা ধরনের বিচিত্র দুর্যোগ বাংলাদেশকে পীড়িত করে চলছে সেই বহুকাল ধরেই। সেই হিসেবে আমাদের জীবন অভিজ্ঞতাটা আরো বেশি সংকটপূর্ণ—আরো বেশি সংগ্রাম মুখর। কিন্তু যেভাবে এই ঘটনাগুলো আমাদের সাহিত্যে গল্প উপন্যাসে আসা দরকার ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের মধ্যে—এই সংগ্রামগুলো—জীবন আখ্যানগুলো, সেগুলো সেভাবে বিপুলভাবে মহৎভাবে আসেনি বা আসছে না।
হাসান আজিজুল হক :
আপনার কথা সত্যি। আসলে সব কিছু একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। কারণ বেশিরভাগ মানুষের কনসার্ন হওয়ার উপায় ছিল না। পশ্চিম বঙ্গ থেকে কিছু মানুষ পূর্ব বঙ্গে গিয়েছে। কেউ কেউ বলবেন আমরা বিতাড়িত হয়েছি। আমাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এরকম কিছু মানুষ বলে। আবার আমার মত মানুষজনও আছে যারা এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে যায়নি। তারা সেভাবে উদ্বাস্তু হয়ে আসেনি। তা না হলে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান--আন্দোলনটা গড়ে উঠল কেন?
এরকম কিছু একটা ছিল। আরও বাস্তব কিছু কারণও ছিল। এখানকার হিন্দু কমিউনিটির অনেক লোকজন ওইপারে চলে যায়। তখন একটা ফাঁক তৈরি হয়ে যায়। এটা পূরণ করার জন্য লোক দরকার। এখানে সেরকম গুণী লোক ছিল না। পশ্চিম বঙ্গ থেকে এসে অনেক পুরনো পরিবার সে দ্বায়িত্ব নেয়। এদের মধ্যে বিখ্যাত কিছু লোকজন ছিল। আবার সাধারণ লোকজনও ছিল। তারা শোষিত হয়েছে। তারা এই শোষণের কথা বলেছে। এই বঙ্গে এসে তারা বাড়তি কিছু দাবী করে বসে। তারা মনে করে তাদের এইসব প্রাপ্য। এক রকম হীনমন্যতা সব সময় তাদের মধ্যে কাজ করেছে। সে মনোভাব ভালো নয়। কিছু লোক প্রচণ্ড কষ্ট করেছে। দাঙ্গায় যারা উৎখাত হয়েছে তাদের কথা আলাদা। আদারওয়াইজ যারা এদেশে এসেছে যারা মনে করেছে—মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ হয়েছে, যাই সেখানে। তাদের কেউ তাড়ায়নি। তারা নিজের উদ্যোগেই চলে এসেছে। আর যারা এদেশেই সেই পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে দেশত্যাগ করতে হয়নি। কেউ পূর্ব বঙ্গ থেকে পশ্চিম বঙ্গে যায়নি।
কুলদা রায় :
কেউ যায়নি। সেটা তো যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।
হাসান আজিজুল হক :
তাদের মধ্যে এই দেশভাগের বেদনাবোধটা নেই। কষ্টটাও নেই। তারা কিছু হারায়নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে বেদনাবোধটা না থকলে তা পুরো সমাজের মধ্যে ব্যপ্ত হবে কিভাবে? তারা তো সুবিধাভোগী অংশ।
এর মানে দেশভাগের ব্যাপারটা পূর্ব বঙ্গে একটা ফাঁকে পড়ে গেল
আমি যেভাবে দেখেছি সেইভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। একটু ভেবে দেখুন , আমি যে দীর্ঘদিন যে এটেনশন পাইনি—কেনো পাইনি? এর কারণগুলো আমি লিখে দিতে পারি। এখান থেকে যারা চলে গিয়েছে সেই সব হিন্দুরা ছিল শিক্ষিত। তার সম্পদশালী। ভদ্রলোক। তারা বেশি এফেক্টেড হয়েছে। তারা পূর্ব বঙ্গে মার খেয়েছে। সরকারও তাদের পিটিয়েছে। আবার পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়ে এদের অনেকেই নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য দন্ডকারণ্য তৈরী করতে হয়েছে।
-----------------------------
গত ১৬ তারিখ রাতে ১১.৫৫ আবার ফোন করি। তিনি এদিন বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন। ব্যথা পেয়েছেন। কথা বলেননি। পরদিন খোঁজ নেই তাঁর মেয়ের কাছে। তিনি জানান সপ্তাহখানেক পরে ফোন করতে। এরপরে আর ফোনে তাঁকে পাওয়া যায়নি।



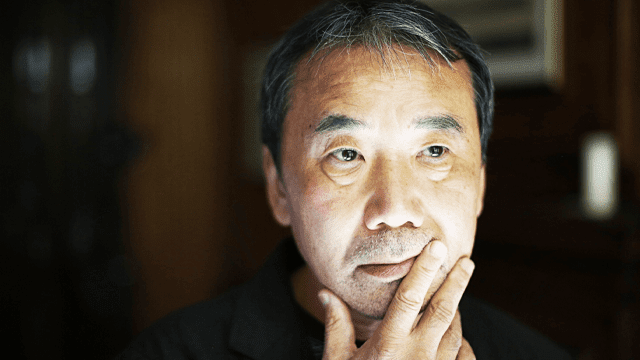






0 Comments